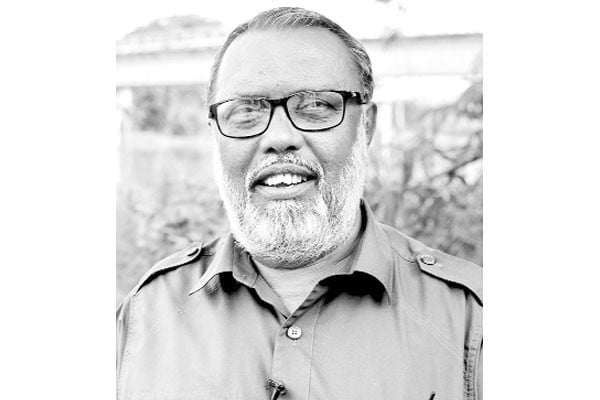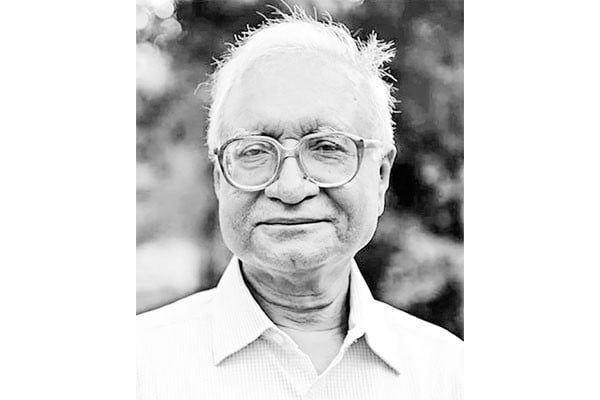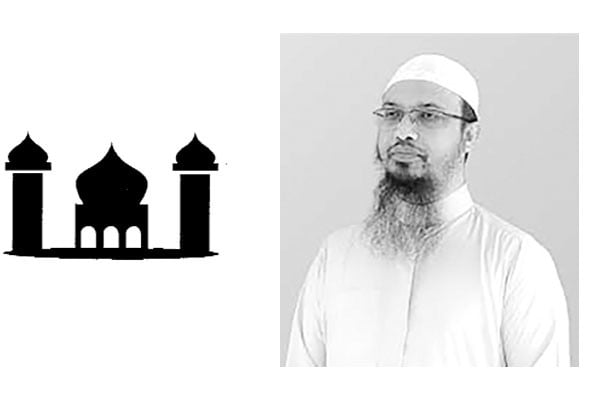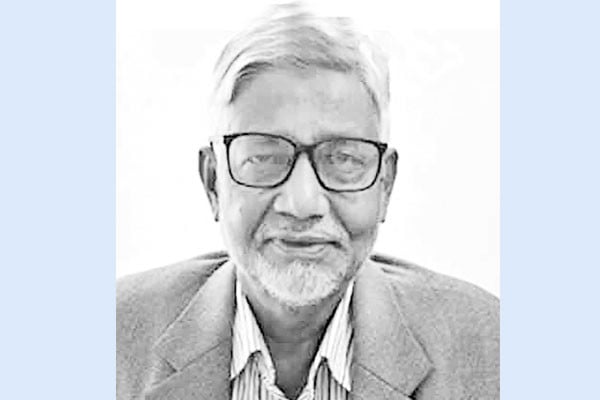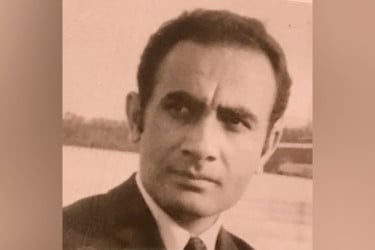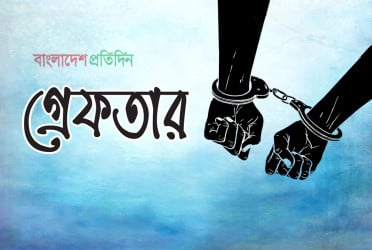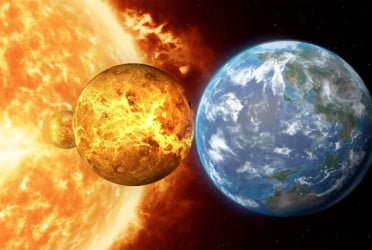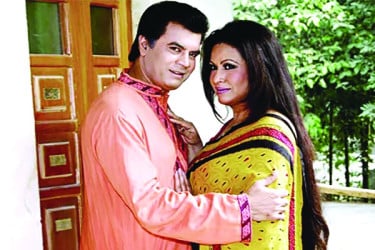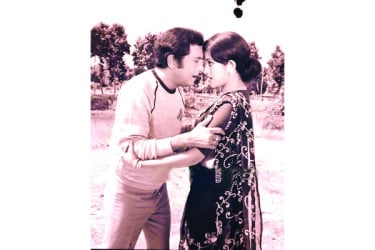আধুনিক সভ্যতা প্রযুক্তির গতিতে এগিয়ে চলেছে। কৃষি, চিকিৎসা, শিক্ষা থেকে শুরু করে অর্থনীতি কিংবা বিনোদন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি আজ অনিবার্য সঙ্গী। কিন্তু প্রযুক্তি যত সুযোগ সৃষ্টি করছে, তার সঙ্গে বাড়ছে ঝুঁকিও। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এই সময়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তবে প্রশ্ন একটাই, আমরা কি প্রযুক্তির ব্যবহারে যথেষ্ট দায়িত্বশীল? ২০২৫ সালের শুরুতে জি-৭ দেশগুলোর নেতারা জাপানের হিরোশিমায় এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্বশীলতার আওতায় আনতে হবে। তারা বলেছিলেন, ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন শুধু প্রযুক্তি নয়, এটি সামাজিক কাঠামো ও নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত।’
জি-৭ দেশগুলো ২০২৩ সালে ‘হিরোশিমা এআই প্রসেস’ নামে একটি উদ্যোগ নেয়, যেখানে কপিরাইট লঙ্ঘন, ভুয়া তথ্য ছড়ানো, এবং কনটেন্ট নির্মাতাদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টও ChatGPT-সহ বিভিন্ন এআই প্ল্যাটফর্মের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু করে।
যুক্তরাষ্ট্রে, ওপেনএআইয়ের সিইও স্যাম অল্টম্যান নিজেই মার্কিন সিনেটে সাক্ষ্য দিয়েছেন, এআই নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। অর্থাৎ প্রযুক্তির নির্মাতারাই এখন বলছেন, ‘অতিরিক্ত স্বাধীনতা নয়, প্রয়োজন দায়িত্বশীল সীমারেখা।’
এ যেন প্রযুক্তির এক নতুন যুগ, যেখানে বিশ্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করবে, কিন্তু সতর্কভাবে। ২০২৪ সালে প্রকাশিত ‘ন্যাশনাল এআই পলিসি’র খসড়ায় বলা হয়েছে দেশের উন্নয়ন কাঠামোতে এআই ব্যবহারের ক্ষেত্র বাড়াতে হবে, তবে তার সঙ্গে থাকতে হবে ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার রক্ষার দিকনির্দেশনা।
তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, নীতির ভাষা এখনো অনেকটাই তাত্ত্বিক। বাস্তবে এআই ব্যবহারের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা, এবং তথ্য সুরক্ষার আইন স্পষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশসহ অনেকে দেশেই এখনো ‘এআই দ্বারা তৈরি কনটেন্ট’-এর মালিকানা সংজ্ঞায়িত হয়নি। একজন শিল্পী যদি বলেন, ‘আমার ছবির ধরন ব্যবহার করে এআই ছবি তৈরি করেছে’ তার আইনি প্রতিকার কোথায়?
 এই জায়গায় আইন ও নীতিমালা দরকার। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন মানে শুধু যন্ত্রের সক্ষমতা নয়, নৈতিক সুরক্ষাও।
এই জায়গায় আইন ও নীতিমালা দরকার। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন মানে শুধু যন্ত্রের সক্ষমতা নয়, নৈতিক সুরক্ষাও।
এআইভিত্তিক অনলাইন লার্নিং ও পার্সোনালাইজড কোচিং প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশে ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে। ChatGPT ও Google Gemini-এর মতো টুল অনেক শিক্ষার্থী ব্যবহার করছে প্রবন্ধ লেখা, অনুবাদ বা গবেষণা সহায়তায়।
তবে এটি আবার এক নতুন ধরনের ‘নির্ভরতা’ তৈরি করছে। শিক্ষার্থীরা অনেক সময় নিজের চিন্তা বাদ দিয়ে এআই-এর চিন্তা গ্রহণ করছে। ফলে শেখার জায়গা সংকুচিত হচ্ছে।
অন্যদিকে এআইনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানোর নতুন সুযোগও তৈরি করেছে। উদাহরণস্বরূপ এআইচালিত ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট এখন গ্রামীণ স্কুলে ইংরেজি উচ্চারণ শেখানোর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।
কৃষি বাংলাদেশের প্রাণ। এখন সেই কৃষিও প্রযুক্তিনির্ভর হচ্ছে। এআইভিত্তিক ‘AgriTech’ সমাধান যেমন ‘KrishiBot’ ও ‘Smart Crop Advisory’ অ্যাপ, মাটির গুণমান বিশ্লেষণ ও ফলনের পূর্বাভাস দিতে পারে।
কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই তথ্য সংগ্রহের সময় কৃষকের ব্যক্তিগত বা অর্থনৈতিক তথ্য কতটা সুরক্ষিত? এই ডেটা যদি বিদেশি কোম্পানির হাতে যায়, তবে কৃষি নীতিনির্ধারণে তা কেমন প্রভাব ফেলবে?
এআই আমাদের জীবন সহজ করছে, কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের ওপর ‘নজরদারি’ও বাড়াচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমের অ্যালগরিদম এখন জানে আপনি কী পছন্দ করেন, কোথায় যান, এমনকি কী ভাবেন। ডেটা হলো নতুন ‘রসদ’, কিন্তু এই রসদ যদি অসৎভাবে ব্যবহার হয়, তবে তা হয়ে দাঁড়াবে অস্ত্র।
এআইভিত্তিক ‘ডিপফেক’ ভিডিও এখন রাজনীতি ও সমাজে ভয়াবহ বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। কারও মুখ বসিয়ে মিথ্যা ভিডিও বানানো বা ভুয়া সংবাদ ছড়ানোসহ অপরাধামূলক কাজে ব্যবহার হচ্ছে। এই ডিজিটাল প্রতারণা থামাতে এখনই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।
বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী পাঁচ বছরে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৮৩ মিলিয়ন চাকরি বিলুপ্ত হবে, যার বড় অংশটি অটোমেশন ও এআই দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।
বাংলাদেশেও ব্যাংক, বিমা, কল সেন্টার, ও প্রোডাকশন সেক্টরে এআই প্রয়োগের ফলে একই ধরনের ঝুঁকি তৈরি হবে। তবে এর বিকল্প পথও আছে। নতুন দক্ষতা শেখা, পুনঃপ্রশিক্ষণ, এবং মানবিক বুদ্ধিমত্তার (emotional intelligence) ওপর গুরুত্ব বাড়ানো।
প্রযুক্তি মানুষের জায়গা দখল করবে- এ ভয় বাস্তব নয়। বরং মানুষ যদি প্রযুক্তিকে বুঝতে না পারে, তখনই প্রযুক্তি তার বিপরীতে দাঁড়ায়।
দায়িত্বশীল প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য আমাদের কিছু মৌলিক দিক স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে। প্রথমত আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের বিষয়টি এখন সময়ের দাবি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের জন্য একটি আলাদা ও আধুনিক আইন তৈরি করতে হবে, যেখানে স্বচ্ছতা, নিরীক্ষণ এবং মানব তত্ত্বাবধানের বাধ্যবাধকতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই আইনগুলোকে সময়োপযোগী রাখতে হবে, যাতে ব্যবহারকারীর অধিকার ও নিরাপত্তা উভয়ই সুরক্ষিত থাকে।
দ্বিতীয়ত ডেটা সুরক্ষা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্পষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে, যাতে নাগরিকের গোপনীয়তা বিঘ্নিত না হয়। এ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিডিপিআর (GDPR)-এর মতো কাঠামো অনুসরণ করা যেতে পারে, যা তথ্য ব্যবহারের নৈতিক ও আইনি মানদণ্ড নির্ধারণে বিশ্বজুড়ে একটি আদর্শ মডেল হিসেবে স্বীকৃত।
তৃতীয়ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাক্রমে এআই-সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা ও নৈতিকতা শেখানো উচিত। পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি খাতের কর্মীদেরও নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ দিতে হবে, যাতে তারা প্রযুক্তির পরিবর্তনশীল পরিবেশে সক্ষমভাবে কাজ করতে পারেন।
চতুর্থত জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। এআইসংক্রান্ত নীতি ও কাঠামো তৈরিতে শুধু প্রযুক্তিবিদ বা প্রশাসক নয়, সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদেরও যুক্ত করতে হবে। এতে প্রযুক্তির সামাজিক ও মানবিক প্রভাব নিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হবে।
সবশেষে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। জি-৭, ইউনেস্কো বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার নীতিমালা ও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বৈশ্বিক মানদণ্ডে নিজেদের সংযুক্ত করা জরুরি। কারণ প্রযুক্তি এখন আর কোনো একক দেশের সম্পদ নয়, এটি এক বৈশ্বিক বাস্তবতা, যার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া বিকল্প নেই।
প্রযুক্তি নিজে ভালো বা মন্দ নয়। তার ব্যবহারই নির্ধারণ করে সে উন্নয়নের হাতিয়ার নাকি ধ্বংসের অস্ত্র। বাংলাদেশ এখন যে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের উন্নয়নের গতি বহু গুণ বাড়াতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে বাড়বে দায়িত্বের চাপ। আমরা যদি এখনই দায়িত্বশীল ব্যবহার, স্বচ্ছ নীতি এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করি, তবে প্রযুক্তি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করবে, আমরা নই।
অতএব প্রযুক্তিকে ভয় না পেয়ে, তাকে বুঝে, নিয়ন্ত্রণে এনে, দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করা শিখতে হবে।
লেখক : মিডিয়াব্যক্তিত্ব