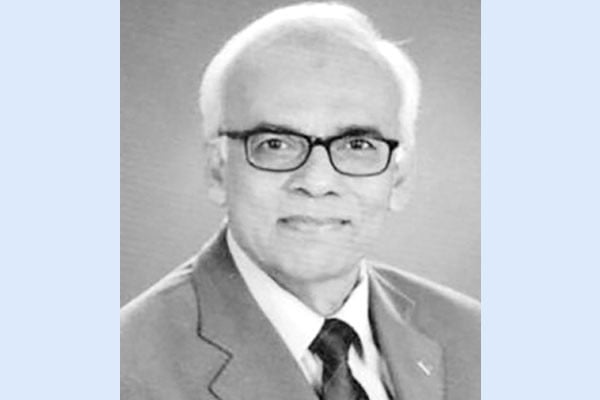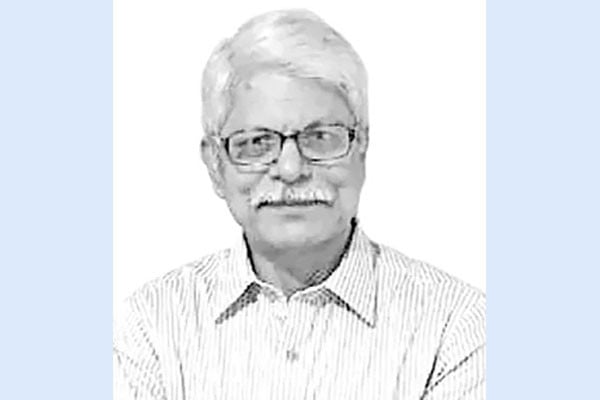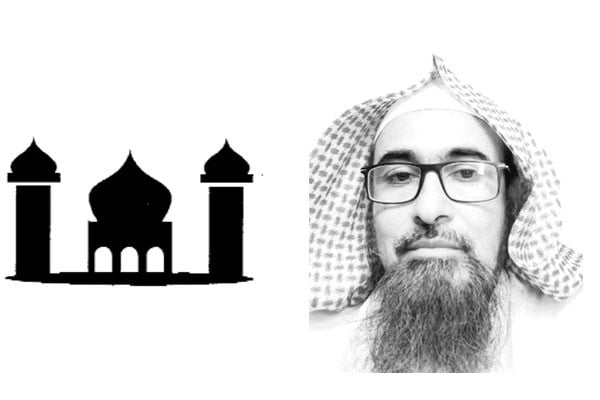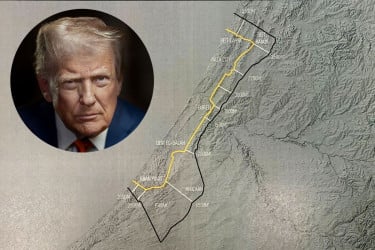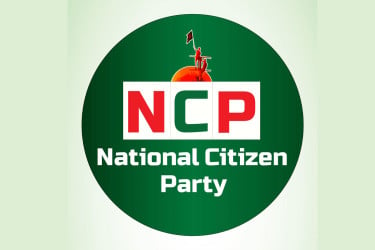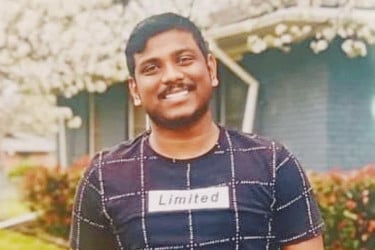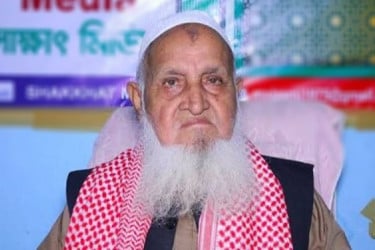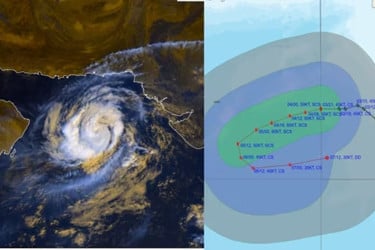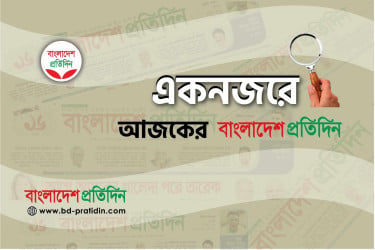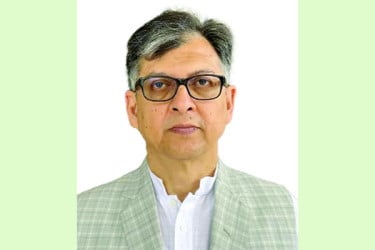‘আজি হতে শত বর্ষ পরে/কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি/ কৌতূহল ভরে’-
শতবর্ষ নয় জন্মের সার্ধশতবর্ষ পরও তাঁর কবিতা ও গান ছাড়া আমাদের জীবনে কোনো অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হয় না। তাঁর রচনাবলি আমাদের মতো মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরে ঘরে থাকে। কিন্তু তাঁর বই পঠনপাঠনের জন্য ততটা নয়। বলা যায়, তা শুধু শোভা বর্ধন অথবা স্ট্যাটাস সিম্বলের জন্য। এক কথায় ব্যাংকের লকারে রাখা সুরক্ষিত ধনরত্নের মতোই।
সে যা হোক, সেই কবির জীবন শহরকেন্দ্রিক নয়। পল্লির পরিসরে তিনি বড় হয়েছেন। পল্লিপ্রকৃতির পানি-আলোবাতাসে গড়া তাঁর জীবন। তাই এখানে তাঁর চিন্তাধারায় পল্লির উন্নয়ন কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে বা সমকালীন জনগণের মধ্যে তার প্রভাব পড়েছে, তা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার এক প্রয়াসমাত্র।
প্রথমেই হয়তো বলা দরকার, অন্য সবকিছুর মতোই পল্লিসমাজ সনাতন শাশ্বত কিছু বস্তু বা ভাবনা নয়। সবকিছুর মতো পল্লিচিত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। রবীন্দ্রনাথ সার্ধশতবর্ষ পূর্বে বাংলার পল্লিকে যেভাবে দেখেছিলেন আজ তার অনেকটাই পাল্টে গেছে। পল্লির অভাব-অভিযোগ, সমস্যা-দুঃখ, সংকটাদি আছে। কোনো কোনো দিক থেকে পল্লি হয়তো আরও তীব্রতর সমস্যায় জর্জরিত। কিন্তু আজ সুখদুঃখের চেহারা বা তার অনুভূতি সেদিনকার মতো নেই। রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ পল্লিতে পল্লিতে যে মানসিক জড়তা, অবসাদ দেখেছেন ইন্দিরা দেবীকে লেখা তাঁর চিঠিগুলোতে পল্লির মানুষদের যে অবসন্ন, শান্ত, নির্জীব চিত্র ফুটে উঠেছে তার পরিবর্তন ঘটে গেছে অনেক। কেননা ইতোমধ্যে পৃথিবীতে ও এই মহাদেশে এবং বাংলায় অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। যদিও সেসব ঘটনায় বাংলার পল্লিবাসীদের হাত ছিল না। তারা শিকার হয়েছেন এসব কর্মকাণ্ডের।
শতাব্দীতে ঘটেছে দুটি মহারণ। দেশ ভাগ হয়েছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা এক রক্তাক্ত-কাণ্ডের মধ্য দিয়ে ভাগ হয়েছে। হয়েছে পশ্চিম বাংলা, পূর্ব বাংলা। সুতরাং বলা চলে, উভয় বাংলার পল্লির জনজীবনের চেহারাটা এতটাই পাল্টে গেছে যে তা যদি রবীন্দ্রনাথ এসে দেখেন তাহলে চমকে যাবেন। তবে যা পাল্টেছে তা উন্নয়নের চেহারা নয়, বরং বলা চলে পল্লিসমাজের এক নগ্ন বীভৎস চেহারা, যার মধ্যে শান্ত-স্নিগ্ধতার লেশমাত্র নেই। তাই রবীন্দ্রনাথকে আজ বলতে পারি না আপনার বাংলার পল্লি আজ আর অবসাদে নেই। দেশগঠন যে মূলত পল্লিরই পুনর্গঠন, এই প্রত্যয় আজ স্বীকৃত। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি রবীন্দ্রনাথ কেন এত বিরক্ত হতেন তা আজ বোঝা যাচ্ছে। কারণ শহরের উন্ন্য়ন নিয়ে তাদের ভাবনাচিন্তা ছিল। পল্লির প্রতি ছিল তাদের অবহেলা, অনীহা, অনাদর, অথচ গণতান্ত্রিক দেশে ভোটই প্রধান চালিকাশক্তি। এই শক্তি রয়েছে পল্লির হতদরিদ্র মানুষের হাতে। তাই তাদের প্রলোভিত করতে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি শাসনকালে পল্লির যে চেহারা প্রত্যক্ষ করেছেন তাতে তিনি অনুতপ্ত। পল্লির স্বাবলম্বী জীবনশক্তি আর নেই। বাংলা যেন ভিতর থেকে উৎপাটিত ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই দরকার পল্লিগুলোর পুনর্গঠন, যে পুনর্গঠন ছাড়া তাদের উন্নয়নও সম্ভব নয়। কিন্তু সেই শক্তি বা আত্মশক্তি ভিতর থেকে আসতে হবে। বাইরে থেকে তা আসতে পারে না। সব দানের শ্রেষ্ঠ দান হলো আত্মশক্তির দান। এই আত্মশক্তি কী এবং কোথায় আছে সেটা দেখিয়ে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথের পল্লিসেবার বা সাধনার অনন্ত উৎসাহের প্রেরণা, দৈনন্দিন কর্ম যেখানে আত্মাকে ধর্মসাধনা ও অনন্তের দিকে প্রসারিত করে। পল্লিজীবনই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে, তাঁর গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, চিঠিপত্রে। পল্লির প্রান্তর, আকাশবাতাস, মেঘ, নদী ও অন্তহীন মানুষের স্রোত সবটার প্রতি মিলিত দৃষ্টি- বিশ্বদৃষ্টি। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মনে একটা ক্ষোভ বা দুঃখ থেকে গেছে। তা হলো, তিনি গ্রামের মানুষদের ভিতরে, গ্রামের ভিতরে ঢুকে তাদের জীবনের শরিক হতে পারেননি। প্রতিশ্রুতি ফুলঝুরি ফোটান নেতারা। তারপর হতদরিদ্র ও পল্লির জনজীবনের কথা তারা বেমালুম ভুলে যান। তবে ইদানীং কিছুটা হলেও বোধোদয় ঘটেছে। আজ পল্লির উন্ন্য়ন নিয়ে কিছুটা পরিকল্পনা তৈরি করছেন সরকার বাহাদুররা। কারণ তারা প্রত্যক্ষ করেছেন দেশের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি রয়েছে পল্লিবাসীদের কাছে।
কবির চিন্তাধারা পল্লিসমাজে প্রতিফলিত হয়েছিল ব্যাপকভাবে। বলা যায়, এ উপমহাদেশের পল্লি পুনর্গঠন ও পল্লি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগামী পুরোধা হলেন রবীন্দ্রনাথ। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মনে একটা ক্ষোভ বা দুঃখ থেকে গেছে। তা হলো, তিনি গ্রামের মানুষদের ভিতরে, গ্রামের ভিতরে ঢুকে তাদের জীবনের শরিক হতে পারেননি।
তিনি যেন কতকটা দূর থেকে মানুষদের দেখেছেন, তাদের খুব কাছাকাছি, ঘেঁষাঘেঁষি করে বসবাস করতে পারেননি। সেই আত্মিক দুঃখবোধ ও অপরাধবোধ তাঁর বিখ্যাত ‘ঐকতান’ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি অপেক্ষা করেছেন-
‘যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।’ তবে ঐকতান কবিতাতে তিনি বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে আধুনিক অনেক কবি শুধু ভঙ্গি দিয়ে জনসাধারণের মর্মবেদনা ফোটাতে চান, ভিতরে কোনো আন্তরিকতা নেই।
লেখক : প্রাবন্ধিক