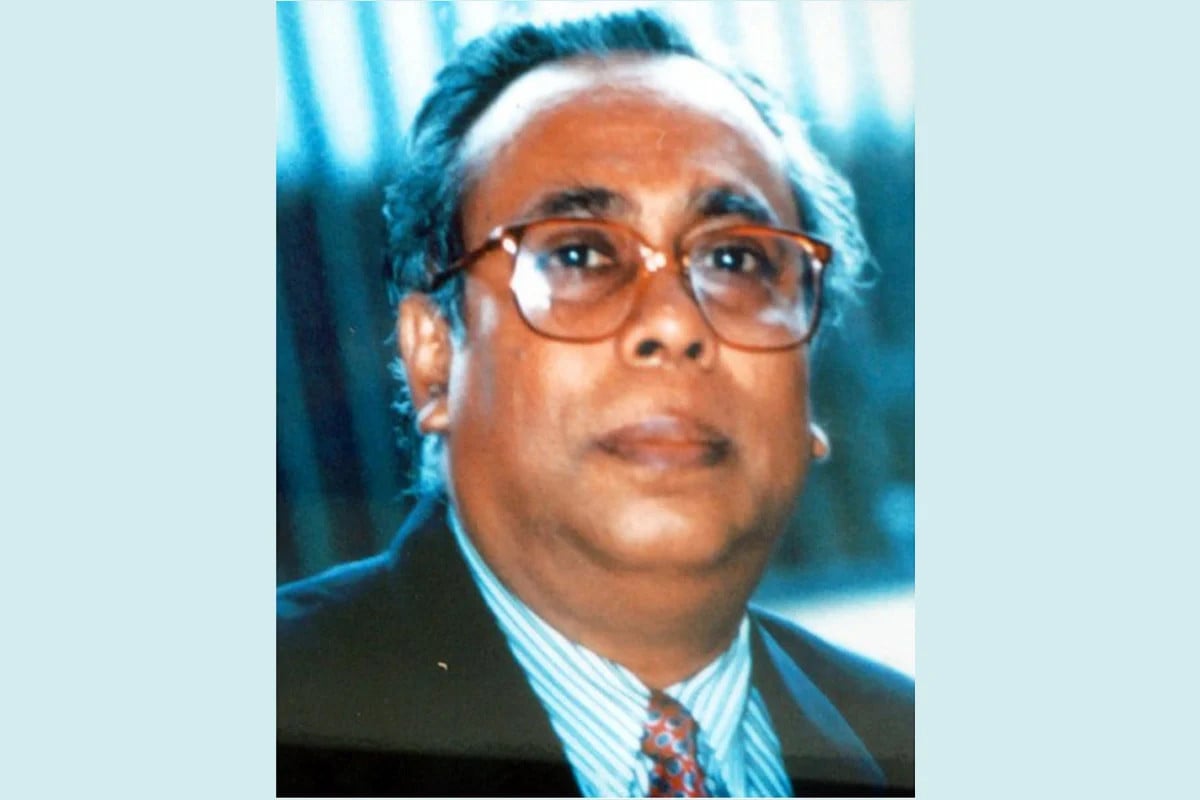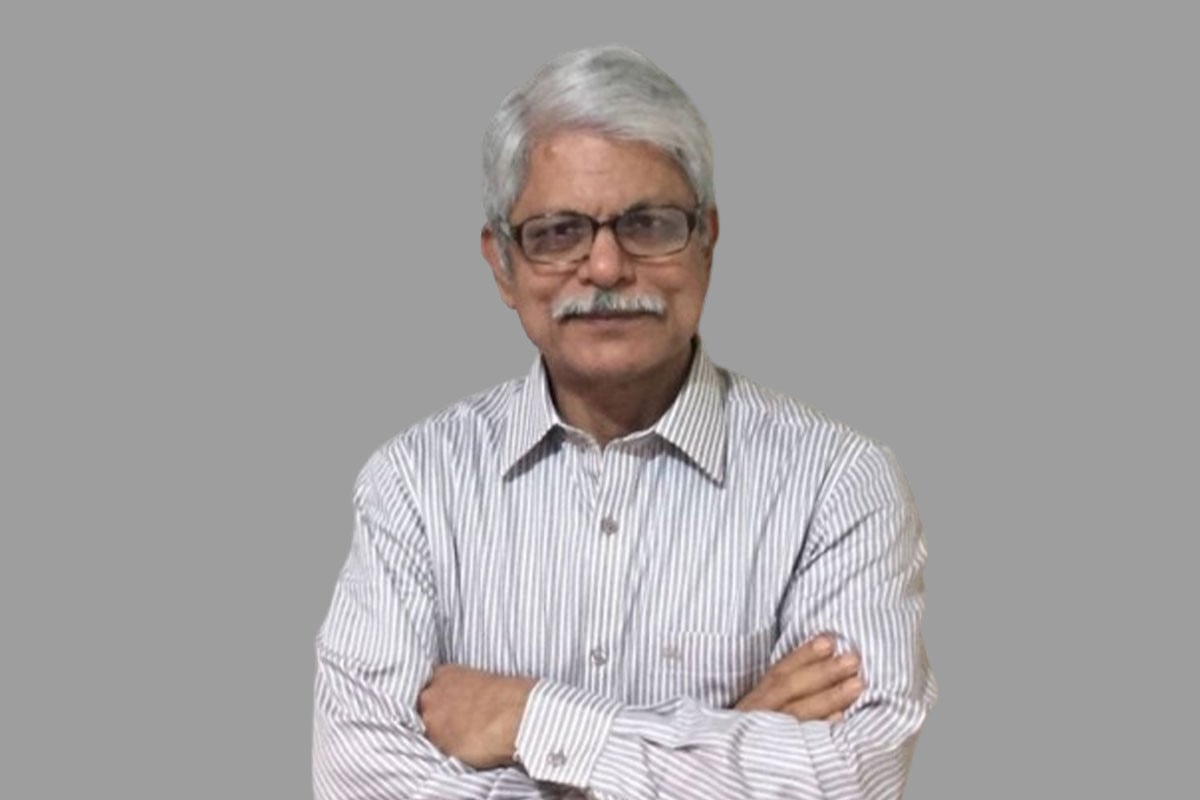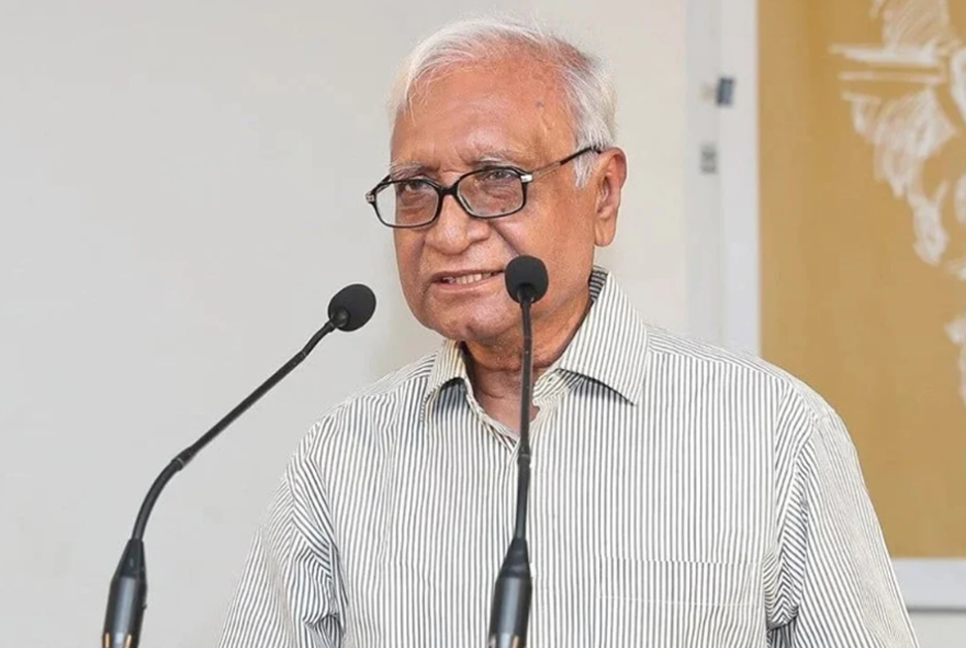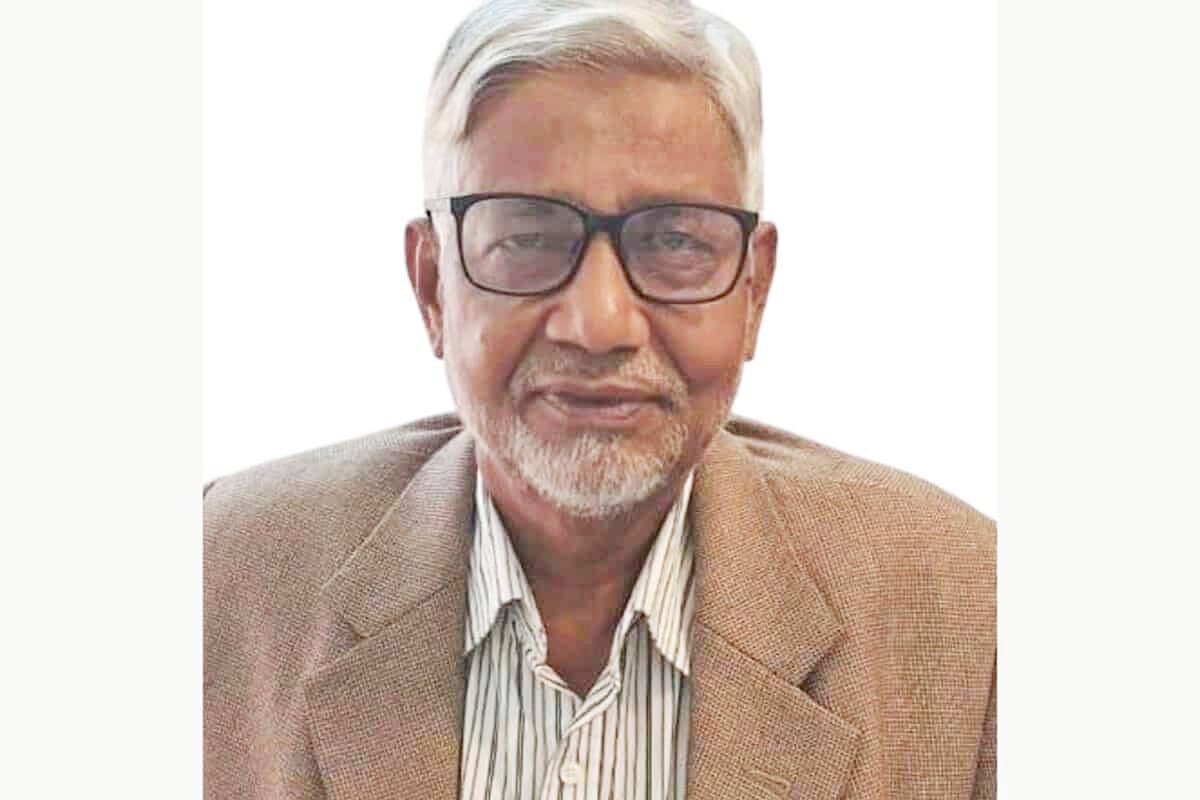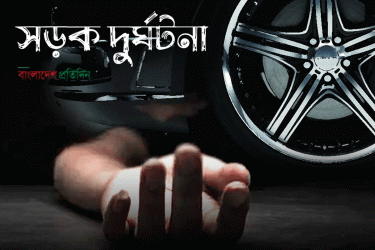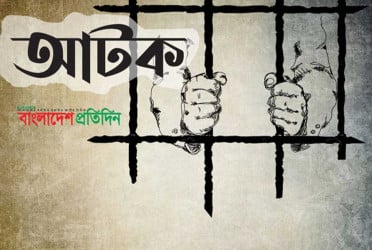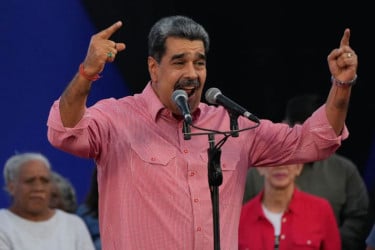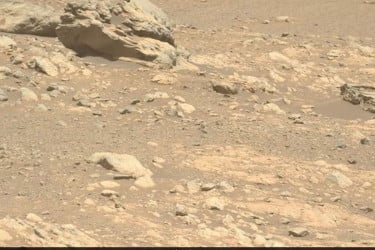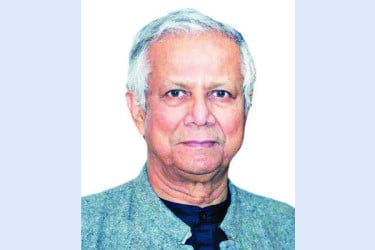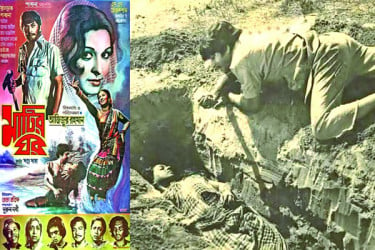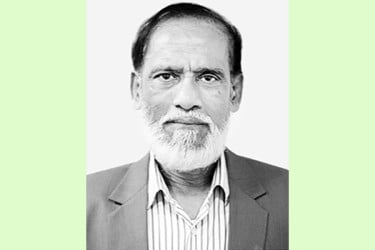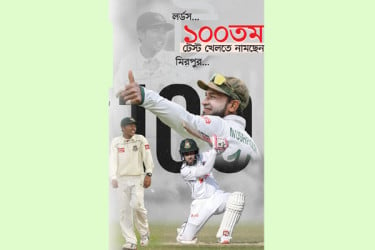শিক্ষকতার পেশা মানবসভ্যতার প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতম পেশাগুলোর একটি। মানুষ যখন প্রথম গুহাচিত্র এঁকে অন্যকে কোনো ধারণা বোঝানোর চেষ্টা করেছিল, তখন থেকেই শিক্ষকতার সূচনা। সেই থেকে আজকের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা ছড়িয়ে দিয়েছে সভ্যতার আলো। অথচ আজও সমাজে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব বিরাজমান।
শিক্ষককে আমরা শ্রদ্ধা করি, তাঁর প্রতি বাহ্যিকভাবে ভক্তি প্রকাশ করি, তাঁকে জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাতা বলি; কিন্তু একইসঙ্গে তাঁর জীবনের সামান্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেও ঈর্ষা ও সন্দেহের চোখে দেখি। যেন শিক্ষক মানেই চিরকালীন দারিদ্র্য, শিক্ষক মানেই অভাবগ্রস্ত জীবনযাপন, শিক্ষক মানেই সাদামাটা পোশাক, সাধারণ বাজার আর পরিশ্রান্ত মুখ। এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল শিক্ষককেই অপমানিত করে না, বরং পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকেই দুর্বল করে দেয়।
শিক্ষক একটি পূর্ণকালীন পেশার মানুষ। ডাক্তার যেমন চিকিৎসার জন্য, আইনজীবী যেমন আইনের জন্য, প্রকৌশলী যেমন নির্মাণের জন্য নিবেদিত, তেমনি শিক্ষক জ্ঞানের জন্য নিবেদিত। কিন্তু ডাক্তার যখন গাড়ি কিনে, সমাজ সেটিকে স্বাভাবিক মনে করে। আইনজীবী দামি পোশাক পরে কোর্টে গেলে কারো আপত্তি থাকে না। ব্যবসায়ী বিলাসবহুল রেস্টুরেন্টে খেলে সেটি সমাজে গর্বের বিষয় হয়। অথচ শিক্ষক যখন সামান্য ভালো পোশাক পরে ক্লাসে যান, বাজার থেকে একটু ভালো ফল-মাছ কিনে আনেন, কিংবা প্রয়োজনবশত একটি গাড়ি কেনেন, তখন সমাজের চোখে তিনি হঠাৎই সন্দেহজনক মানুষে পরিণত হন। যেন শিক্ষক হওয়া মানেই গরিব হয়ে বাঁচতে হবে, যেন দারিদ্র্য তাঁর পেশাগত অলংকার।
এই মানসিকতার শিকড় খুঁজতে গেলে আমরা দেখতে পাই, শিক্ষকতার ইতিহাসে একসময় সত্যিই দারিদ্র্যের একটি দীর্ঘ ছায়া ছিল। প্রাচীনকালে গুরুকুলে গুরু খুব সামান্য উপহার বা ‘গুরুদক্ষিণা’ গ্রহণ করতেন। মধ্যযুগে মক্তব-মাদ্রাসায় শিক্ষকরা প্রায়ই সমাজের দান-অনুদানের ওপর নির্ভর করতেন, এমনকি এখনও সেই প্রথা চলমান। উপনিবেশ আমলেও শিক্ষকতার বেতন ছিল অল্প, অনেক সময় তাঁরা কৃষিকাজ বা অন্য কোনো পেশার সহায়তায় সংসার চালাতেন। সেই থেকে সমাজে এক ধরনের স্থায়ী ধারণা তৈরি হয়েছে, শিক্ষক মানেই গরিব।
কিন্তু আজকের যুগ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজ শিক্ষকতা একটি পূর্ণকালীন রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পেশা। শিক্ষকরা তাদের যোগ্যতা, পরিশ্রম ও শ্রম দিয়ে একটি নির্দিষ্ট বেতন পান। অনেক দেশে শিক্ষকরা উন্নত বেতন, ভালো সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করেন। ফলে তারা সমাজে অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে ওঠেন। অথচ আমাদের সমাজের বহু অংশ এখনো সেই পুরোনো ধারণা আঁকড়ে ধরে আছে, শিক্ষক যেন কখনো ভালো পোশাক পরতে পারবেন না, ভালো খাবার খেতে পারবেন না, গাড়ি বা বাড়ি কিনতে পারবেন না।
এই দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষকদের প্রতি গভীর অবিচার। কারণ শিক্ষকও মানুষ। তাঁরও স্বপ্ন আছে, তাঁরও সন্তান আছে, তাঁরও একটি পরিবার আছে। তিনি যেমন শিক্ষার্থীর চোখে আলোর প্রদীপ জ্বালাতে চান, তেমনি নিজের ঘরেও আলো দেখতে চান। তাঁর পোশাক কেবল বাহ্যিকতা নয়, এটি তাঁর আত্মসম্মানের প্রতিফলন। একজন শিক্ষক যখন পরিষ্কার, মার্জিত ও মানসম্মত পোশাক পরে ক্লাসে প্রবেশ করেন, তখন শিক্ষার্থীরাও অনুপ্রাণিত হয়। তারা বুঝতে পারে শিক্ষক মানে কেবল জ্ঞানের আলো নয়, সৌন্দর্যের দৃষ্টান্তও।
কিন্তু সমাজের একাংশ সেই সৌন্দর্যকেও ঈর্ষার চোখে দেখে। শিক্ষক যদি গাড়ি চালান, তখন তারা মনে করে, “নিশ্চয়ই অন্য কোনো অসৎ পথে অর্থ উপার্জন করেছেন।” অথচ সেই গাড়ি হয়তো দীর্ঘদিনের সঞ্চয়ে কেনা, হয়তো পরিবারের জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্য নেওয়া। একজন ডাক্তার বা ব্যবসায়ী গাড়ি কিনলে সেটি প্রশংসার বিষয় হয়, কিন্তু শিক্ষক কিনলে সেটি ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই বৈপরীত্য কেবল একটি মানসিক বিভ্রান্তি নয়, বরং এটি শিক্ষকদের প্রতি সমাজের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ।
শিক্ষকের জীবনযাত্রা সম্পর্কে এই ভুল ধারণা শিক্ষার্থীদের মধ্যেও প্রভাব ফেলে। তারা দেখে, শিক্ষক হওয়া মানে আর্থিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ সহ্য করা। ফলে তারা শিক্ষকতার পেশার প্রতি অনাগ্রহী হয়ে পড়ে। আজকের তরুণেরা যখন দেখে শিক্ষকতা মানে দারিদ্র্য, তখন তারা মেধা নিয়ে অন্য পেশায় চলে যায়। ফলস্বরূপ, শিক্ষকতায় মেধার সংকট তৈরি হয়, শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতরে মানের ঘাটতি তৈরি হয়।
প্রকৃতপক্ষে সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গিই শিক্ষার মানোন্নয়নে বড় বাধা। শিক্ষক যদি তার শ্রমের ন্যায্য প্রতিদান পান, যদি তিনি স্বাভাবিকভাবে ভালো পোশাক পরতে পারেন, উন্নত জীবনযাপন করতে পারেন, তবে তিনি শিক্ষার্থীদের সামনে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাঁড়াতে পারবেন। তাঁর ক্লাস হবে প্রাণবন্ত, তাঁর ব্যক্তিত্ব হবে অনুকরণীয়। শিক্ষার্থীরা তখন শিক্ষককে শুধু জ্ঞানের উৎস হিসেবে নয়, জীবনযাত্রার আদর্শ হিসেবেও গ্রহণ করবে।
তাহলে কেন আমরা এখনো শিক্ষককে গরিবের প্রতীক হিসেবে দেখতে চাই? এর উত্তর হয়তো আমাদের সামাজিক মানসিকতার ভেতর লুকিয়ে আছে। আমরা চাই শিক্ষক হবেন নিঃস্বার্থ, ত্যাগী, নির্লোভ। কিন্তু আমরা ভুলে যাই, নিঃস্বার্থ হওয়া মানেই দারিদ্র্যের শৃঙ্খলে বাঁধা নয়। একজন শিক্ষক ধনীও হতে পারেন, আবার নীতিবানও থাকতে পারেন। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য মানেই নীতিভ্রষ্টতা নয়। বরং আর্থিক নিরাপত্তা থাকলে শিক্ষক আরো স্বাধীনভাবে, নিরপেক্ষভাবে জ্ঞান দিতে পারেন।
আমাদের প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। শিক্ষকও যদি গাড়ি কিনেন, সেটি সমাজের উন্নতির প্রতীক; কারণ তখন বোঝা যায় শিক্ষকও উন্নত জীবনযাপন করতে পারছেন। শিক্ষকও যদি ভালো রেস্টুরেন্টে খেতে যান, সেটি সমাজের স্বাভাবিকীকরণের প্রতীক। শিক্ষকও যদি ভালো পোশাক পরেন, সেটি তাঁর আত্মসম্মান রক্ষার প্রতীক। আমাদের এই সবকিছুকে স্বাভাবিকভাবে নিতে শিখতে হবে।
শিক্ষকের মর্যাদা কেবল তাঁর কথার ভেতর সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। তাঁর জীবনযাত্রার ভেতরেও সেই মর্যাদার প্রতিফলন ঘটতে হবে। যদি আমরা চাই সমাজে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়ুক, তবে সেই আলোকবর্তিকার বাহককে অন্ধকারে রাখলে হবে না। শিক্ষক সুখী না হলে সমাজ কখনো সুখী হতে পারে না। শিক্ষক যদি দারিদ্র্যের চাপে নুয়ে পড়েন, তবে তাঁর কণ্ঠে স্বাধীনতার গান ফুটবে না।
অতএব এখন সময় এসেছে সেই পুরোনো ধারণা ভাঙার- “শিক্ষক মানেই গরিব।” শিক্ষক মানেই মর্যাদাশীল মানুষ। শিক্ষক মানেই আত্মবিশ্বাসী জীবনযাপন। শিক্ষক মানেই সমাজের জন্য আলোকিত আদর্শ। শিক্ষক ভালো পোশাক পরলে সেটা হিংসার নয়, গৌরবের বিষয় হওয়া উচিত। শিক্ষক গাড়ি কিনলে সেটা ব্যঙ্গের নয়, বরং প্রমাণ হওয়া উচিত আমাদের সমাজ শিক্ষাকে মর্যাদা দিয়েছে।
আজকের পৃথিবী প্রতিযোগিতার। আমাদের সন্তানদের বিশ্বদরবারে দাঁড়াতে হলে প্রথম শর্ত হলো যোগ্য ও আত্মমর্যাদাবান শিক্ষক। তাই শিক্ষকের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান কেবল তাঁর ব্যক্তিগত প্রাপ্তি নয়, বরং জাতির ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের প্রধান শর্ত।
শিক্ষককে আমরা মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে শিখি। তাঁকে তাঁর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা উপভোগ করতে দিই। তাঁর হাসি, তাঁর আনন্দ, তাঁর উন্নত জীবনযাপন যেন আমাদের গর্বের বিষয় হয়। তখনই সমাজ বদলাবে, তখনই শিক্ষা হবে প্রাণবন্ত, তখনই জাতি হবে সত্যিকার অর্থে আলোকিত।
লেখক : সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ভেড়ামারা সরকারি কলেজ।