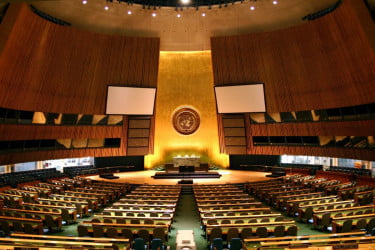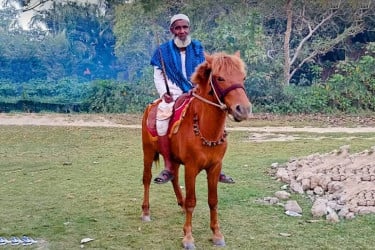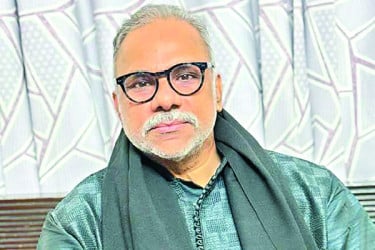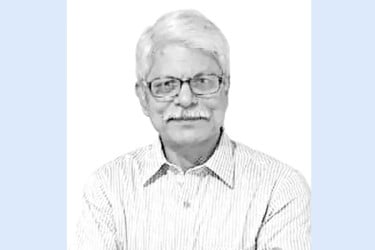গণ অভ্যুথানে শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর দায়িত্ব নেওয়া অন্তর্বর্তী সরকারের ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও দেশের অর্থনীতিতে দৃশ্যমান কোনো উন্নতি হয়নি। এমনকি কমবেশি স্থবিরতা বিরাজ করছে সব খাতেই। আস্থাহীনতায় ব্যবসায়ীরা। কমেনি মূল্যস্ফীতি। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়েনি। কমেছে বেসরকারি খাতের ঋণ। সংকট কাটেনি ব্যাংকে। এমন সব মতামত বিশ্লেষকদের। তারা বলছেন, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক অনিশ্চয়তাই মূল কারণ। অন্যান্য খাতের মতো এ খাত গুরুত্ব না পাওয়ায় গতি ফেরেনি দেশের অর্থনীতিতে।
২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগের শাসনামলের শুরুতে খেলাপি ঋণ ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। ২০২৪ সালের জুন শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ১১ হাজার ৩৯১ কোটি টাকা। ৮৪ টাকার ডলারের দর ১১০ টাকার বেশি। ঋণের নামে ব্যাংকের অর্থ লুটপাট ও পাচার হয়। খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১০ দশমিক ৪২ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বরে নিট বিদেশি বিনিয়োগ ছিল ৩৬ কোটি ডলার। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ছিল ৯ দশমিক ৮ শতাংশ। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা ছাড়ার আগে দেশের অর্থনীতির চিত্র মোটামুটি এমনটাই ছিল। এ কারণে দেশের অর্থনীতিকে খাদের কিনারে ফেলার অভিযোগ রয়েছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে।
ক্ষমতায় বসে অন্তর্বর্তী সরকার দেশের আর্থিক খাত বিভিন্ন ধরনের সংস্কার কর্মসূচি নিয়েছে। যার অংশ হিসেবে ব্যাংক খাত সংস্কারে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এসব উদ্যোগের ফলে গেল ছয় মাসে দেশের অর্থনীতির কতটা উন্নতি হয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাবেক মহাপরিচালক মুস্তফা কে মুজেরি বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, যদি আমাদের মূল্যস্ফীতি, প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের কথা বলি, সব ক্ষেত্রেই একই অবস্থা রয়ে গেছে। কাজেই সবকিছু মিলে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে একটা স্থবিরতা বিদ্যমান। কোথাও চলমান হওয়ার সম্ভাবনা চোখে পড়ছে না। তিনি আরও বলেন, ছয় মাসের বেশি হয়ে গেলেও সমস্যাগুলো এখনো জিইয়ে আছে। দুর্বল ব্যাংকগুলো এখনো ওইভাবেই চলছে। ব্যাংক খাত খাদের কিনারেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাজারব্যবস্থাপনা উন্নয়নের একটা বড় বিষয় ছিল। সেই বাজারব্যবস্থাপনার কি উন্নয়ন হয়েছে? আগের মতোই রয়েছে।
ঢাকা মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সভাপতি ও লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, এমন দেশ নেই, যেখানে ব্যবসায়ীরা দুই অঙ্কের ব্যাংক সুদহারে মুনাফা করতে পারেন। দেশে এখন সুদের হার ১৫ শতাংশের বেশি। বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনের সঙ্গে পণ্যের মান, ভাবমূর্তি ও সম্পৃক্ততা বাড়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) এই মুমূর্তে আসবে না। অর্থনীতির বিকাশের জন্য বিনিয়োগ করতে হলে ব্যবসা-বাণিজ্যকে সচল রাখতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা ব্যবসায়ীদের অনুকূল হতে হবে।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, চলতি বছরের জানুয়ারি শেষে খাদ্য মূল্যস্ফীতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ৭২ শতাংশ। যদিও গত বছরের ডিসেম্বরের তুলনায় ২ দশমিক ২ শতাংশ পয়েন্ট কমেছে। আগামী মাসে খেলাপি ঋণ ছাড়িয়ে যাবে ৫ লাখ কোটি টাকা। গত বছরের সেপ্টেম্বর শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৮৪ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকা। ডিসেম্বর শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ২ দশমিক ৫ শতাংশ কমে ৭ দশমিক ৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বরে নিট বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০ কোটি ৪০ লাখ ডলার। বেসরকারি বিনিয়োগ আটকে আছে ২৩ থেকে ২৪ শতাংশের মধ্যে। বিশ্লেষকরা বলেন, বর্তমান সরকারের কাছে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং বিষয় হচ্ছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও দেশের ব্যাংক খাতের ওপর আমানতকারীদের আস্থা ফেরানো। যার অংশ হিসেবে দুর্বল ব্যাংকগুলোর গ্রাহকদের অর্থ ফেরত দিতে ২২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কয়েক দফায় নীতি সুদহার বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। তার পরও এই দুটি খাতের তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, জনগণ আর্থিক খাতে দৃশ্যমান পদক্ষেপ দেখতে চায়। নমুনা হলেও কাজ করে দেখাতে হবে। এখন সবচেয়ে বড় চাপ মূল্যস্ফীতির। সুদহার বাড়ায় মূল্যস্ফীতি কিছুটা কম বাড়ছে। তবে এখনো অনেক বেশি। মূল সমস্যা, বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে না।’
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের সাবেক মহাপরিচালক তৌফিক আহমেদ চৌধুরী বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে সাধারণ মানুষের অনেক উপকার হতো। বলা যায়, রাজস্ব আদায় আগের তুলনায় অনেক কমেছে। অর্থনীতির কোনো প্রবৃদ্ধি হয়নি, আবার খারাপের দিকেও যায়নি। তিনি আরও বলেন, সামস্টিক অর্থনীতির উন্নতির জন্য অবশ্যই দেশের স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন সবার আগে প্রয়োজন।