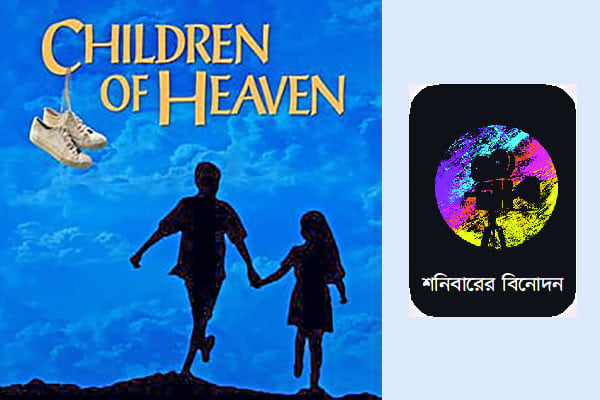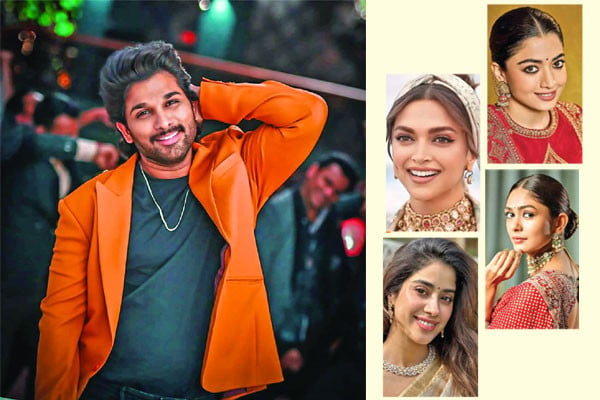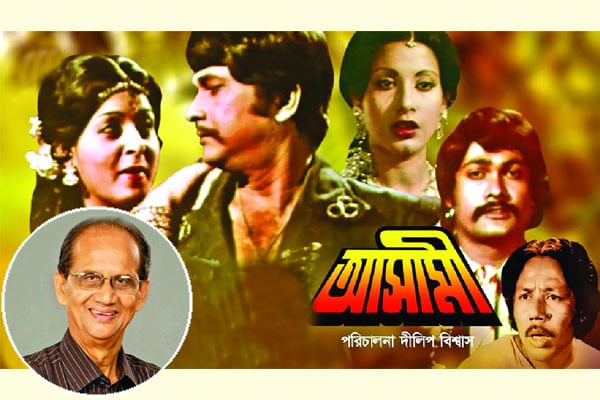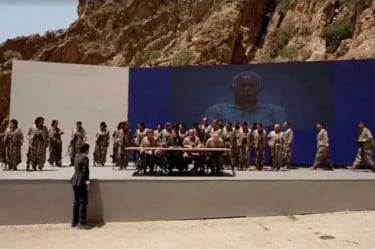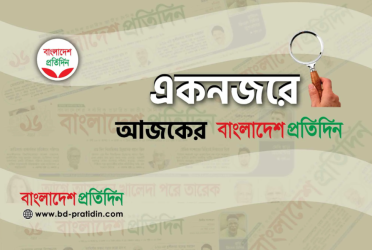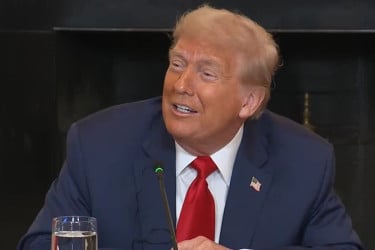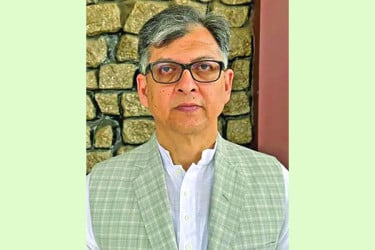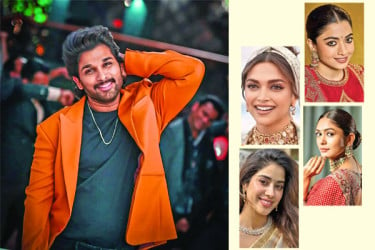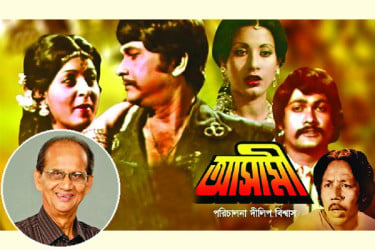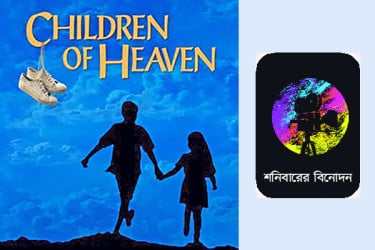১৯৬৪ সাল, এ বছর বাংলা ছবির ইতিহাসে ঘটে গেল মহাবিপ্লব। চলচ্চিত্রকার হিসেবে সুভাষ দত্তের তখনো খুব একটা নামডাক হয়নি। তিনি অতি সাধারণ একটি গল্প নিয়েই নিজের ছিপছিপে গড়নে নায়ক হয়ে নির্মাণ করলেন ‘সুতরাং’ ছবিটি। সুভাষ দত্তের এ সাহসী ভূমিকা বিশাল আকারে সফল হলো। ছবিটি শুধু দেশে নয়, বিদেশেও সম্মাননা পেল। প্রথম কোনো বাংলা ছবি তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসব জয় করে নিল। এর একটিই কারণ- ছবিটির গল্প ছিল এ দেশের মাটি ও মানুষের যাপিত জীবনকে ঘিরে।
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ববিতা বলেন, ‘আমাদের সময় যেসব সিনেমা হতো সে তুলনায় এখনকার সিনেমাগুলো কিছুই না। গল্পও সেরকম না, সেরকম চিত্রনাট্যও না, সেরকম চরিত্রও না।’ মূল কথা হলো, গল্প ও চিত্রনাট্যের দুর্বলতার কারণে এখনকার বেশির ভাগ সিনেমাই ব্যবসায়িকভাবে মার খাচ্ছে। এমন অভিযোগ আরও অনেকের। ১৯৫৬ সালে মুক্তি পেল এ দেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক বাংলা চলচ্চিত্র ‘মুখ ও মুখোশ’। মুখ ও মুখোশের পর আরও বেশ কিছু বাংলা ছবি নির্মাণ হলেও সেগুলো চলছিল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ১৯৬৪ সাল, এ বছর বাংলা ছবির ইতিহাসে ঘটে গেল মহাবিপ্লব। চলচ্চিত্রকার হিসেবে সুভাষ দত্তের তখনো খুব একটা নামডাক হয়নি। তিনি অতি সাধারণ একটি গল্প নিয়েই নিজের ছিপছিপে গড়নে নায়ক হয়ে নির্মাণ করলেন ‘সুতরাং’ ছবিটি। বাংলা ছবির দুর্দিনে সুভাষ দত্তের এ সাহসী ভূমিকা বিশাল আকারে সফল হলো। ছবিটি শুধু দেশে নয়, বিদেশেও সম্মাননা পেল। প্রথম কোনো বাংলা ছবি তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসব জয় করে নিল। এর একটিই কারণ- ছবিটির গল্প ছিল এ দেশের মাটি ও মানুষের যাপিত জীবনকে ঘিরে। এ ছবিটি দিয়েই দেশীয় চলচ্চিত্রের ট্রেন্ড বদলে গেল। শুরু হলো বাংলা ছবির জয়জয়কার। কিন্তু গত প্রায় কয়েক দশক ধরে বাংলা ছবির অঙ্গনে লেগেছে চরম খরা। কিন্তু কেন এ অবস্থা? এর জবাবে অনেক বাংলা ছবিপ্রেমী সচেতন দর্শকের মতে, তারা এ সময়ের জীবনযাপনের চিত্র দেখতে চায়। তাছাড়া ছবির নির্মাতারা মুখে মুখে দেশপ্রেমের কথা বলেন, বাস্তবে বিদেশি ছবির নকল করেন। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র গবেষক, সাংবাদিক অনুপম হায়াৎ বলেন, ‘মানসম্মত ছবি নির্মাণ ও মৌলিক গল্প উদ্বেগজনক হারে কমেছে। তাতে দর্শক সিনেমা হলে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়েছেন। আগে কারা কী গল্প লিখতেন, চিত্রনাট্যকার, গীতিকার এবং নির্মাতার মেধা কোন উচ্চতায় ছিল? তাদের মেধাবী ও সময়োপযোগী কর্মযজ্ঞ একটি ছবি দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধের মতো সিনেমা হলে আটকে রাখত। এখন এসবের অভাব প্রবলভাবে দৃশ্যমান’। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক জুনায়েদ হালিম বলেন, ‘সত্যি বলতে দেখার উপযোগী ছবি হচ্ছে না। আগে বক্তব্যধর্মী ছবি নির্মাণ হতো। সুস্থ ধারার ছবিও তেমন তৈরি হচ্ছে না। ফলে দর্শকদের ওপর সিনেমা হলে না যাওয়ার দায় চাপানো যাবে না। যানজট ঠেলে সময় আর অর্থ নষ্ট করে কেন সিনেমা হলে ছবি দেখতে যাবে। তাই ছবির গল্প জীবনঘেঁষা ও আধুনিক নির্মাণেই বাণিজ্যিক ছবির সুদিন ফেরানো সম্ভব’। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগের চেয়ারপারসন হাবিবা রহমান বলেন, ‘বর্তমানে আমাদের দেশের প্রায় ছবির গল্প, চিত্রনাট্য ও নির্মাণ মানসম্মত নয়। নেটে ছবি দেখে বাইরের ছবির সঙ্গে এ দেশের ছবির তুলনা করার সুযোগ পাচ্ছেন দর্শক। তাই তাদের যেমন-তেমন নির্মাণ আর গল্পের ছবি দিয়ে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ নেই। ভালো গল্পের ছবি নির্মাণ করতে হবে। চিত্রনাট্যেও জোর থাকতে হবে।’ প্রায় অভিন্ন সুর নবীন অভিনয় শিল্পীদের মুখেও। তারা সবাই ভালো গল্পের অভাবের কথা বলছেন। শুধুই গল্পের ঘাটতি নাকি গল্পকে ভালো চিত্রনাট্যে রূপ দেওয়ারও অভাব আমাদের? অনেকে গল্প ও চিত্রনাট্য বা স্ক্রিপ্টকে এক করে ফেলেন। বিষয়টা হচ্ছে- প্রথমত গল্প থেকেই স্ক্রিপ্ট হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেকেই গল্পের দ্বারস্থ না হয়ে মাথায় একটা ভাবনা রেখে সরাসরিই স্ক্রিপ্ট তৈরি করেন। অনেকে ২০-৪০টি নাটক-সিনেমা দেখে স্ক্রিপ্ট তৈরি করেন। এজন্য বিশেষ পেশাদার লোকও থাকেন। অ্যাসাইনমেন্টের চিত্রনাট্য এমনই। অথচ গল্প সৃজনশীল, কারিগরি নয়। যদিও এখন চিত্রনাট্যের বেশির ভাগই কারিগরি হয়ে গেছে। একসময় সিনেমাকে দর্শক ‘বই’ বলতেন। গ্রামবাংলায় আজও সিনেমাকে ‘বই’ বলা হয়। বই মানেই গল্প। ফলে দর্শকরুচিতেও থাকে এ ‘গল্প’ বা ‘বই’। এজন্য একজন নির্মাতাকেও দর্শকরুচিকে বোঝার ক্ষমতা থাকতে হবে। পাশাপাশি দর্শক তৈরির ক্ষমতাও থাকতে হবে। বহু বিখ্যাত সিনেমা বইয়ের চিত্রনাট্য রূপ থেকেই হয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের অমর সিনেমা ‘পথের পাঁচালী’ ধ্রুপদী উপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর উপন্যাস ‘পথের পাঁচালী’র চিত্রনাট্যরূপ থেকেই হয়েছে। গৌতম ঘোষের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ ও আরেক ধ্রুপদী উপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বখ্যাত উপন্যাস ‘পদ্মা নদীর মাঝি’র চিত্রনাট্যরূপ থেকে হয়েছে। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও চলচ্চিত্রনির্মাতা সাদেক খানের একমাত্র চলচ্চিত্র ‘নদী ও নারী’ও হয়েছে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ও লেখক হুমায়ুন কবিরের ‘নদী ও নারী’ উপন্যাসের চিত্রনাট্যরূপ থেকে। কালজয়ী উপন্যাসিক অদ্বৈত বর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’-এর চিত্রনাট্যরূপ থেকে একই শিরোনামের চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন প্রখ্যাত নির্মাতা ঋত্বিক ঘটক। এখন এমন গুণী চিত্রনাট্যকারও নেই যারা ভালো চিত্রনাট্য দিয়ে ভালো সিনেমা নির্মাণে সহযোগিতা করবেন। আর যাদের যোগ্যতা আছে তারাও নিজ গুণের প্রতিফলন ঘটাতে পারছেন না ওই বাজারি নির্মাতাদের বাজারি চাহিদার কারণে। অথচ আমাদের চলচ্চিত্রের সোনালি সময় গড়ে উঠেছিল সৈয়দ শামসুল হক, সুভাষ দত্ত, আমজাদ হোসেন, চাষী নজরুল ইসলাম, আজিজুর রহমান, আলমগীর কবির, নারায়ণ ঘোষ মিতা, খান আতাউর রহমান, ছটকু আহমেদ প্রমুখের মতো গল্পকার ও চিত্রনাট্যকারের দক্ষ কর্মযজ্ঞে। একটা সময় যে সিনেমাতে ভালো গল্প দেখেছেন সে সিনেমাতেই উপচে পড়ছেন দর্শক। এ দর্শকও একদিনে তৈরি হয়নি। এ দেশে যখন উর্দু সিনেমার বাজার একচেটিয়া তখন আমাদের নির্মাতারা অপেক্ষা করছিলেন এমন একটি গল্পের ছবি যা দর্শকের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। সেই কাজটিই করেছিলেন প্রখ্যাত নির্মাতা সালাহউদ্দিন তাঁর ‘রূপবান’ চলচ্চিত্রে। এটির চিত্রনাট্য রূপও গ্রামবাংলার যাত্রাপালা কাহিনি ‘রূপবান’ গল্পের। রাতারাতি উর্দু সিনেমার দর্শক লোককাহিনিনির্ভর সিনেমার দিকে মোড় নিল। এভাবে বাংলা চলচ্চিত্রে নবজাগরণ সৃষ্টিতে লোককাহিনিনির্ভর সিনেমা একটা ঐতিহাসিক জায়গা করে নিল। এতেই বোঝা যায়, দর্শক তৈরিতে ভালো গল্প ও চিত্রনাট্যের জুড়ি নেই।