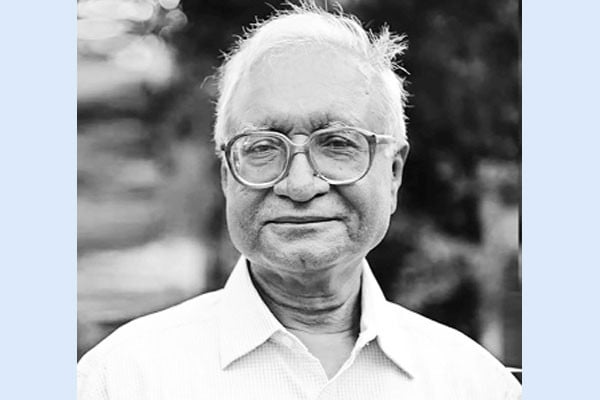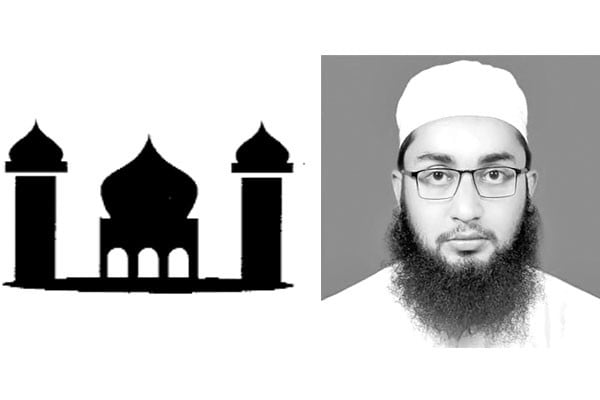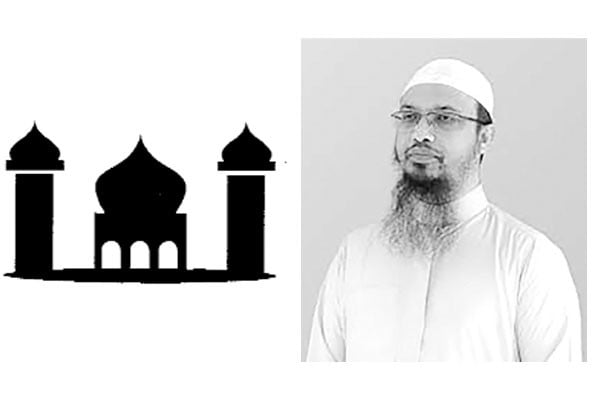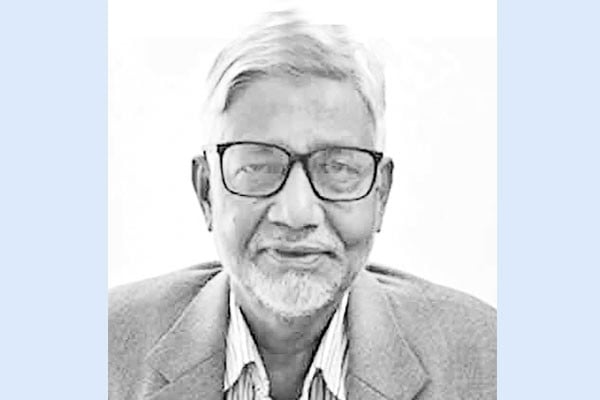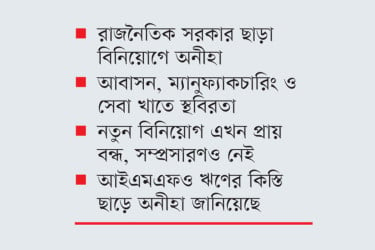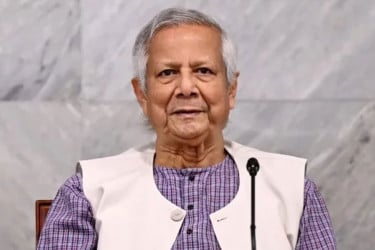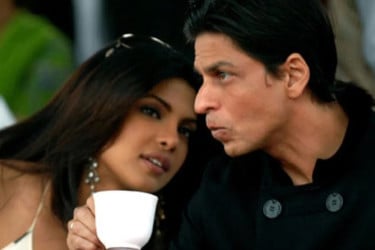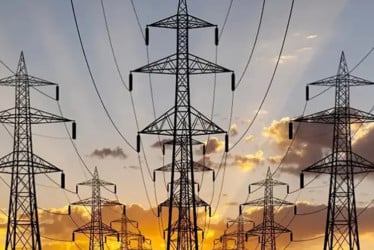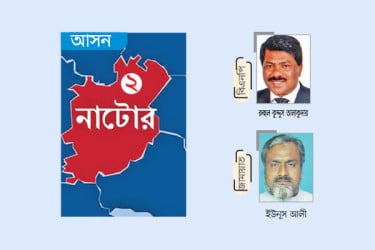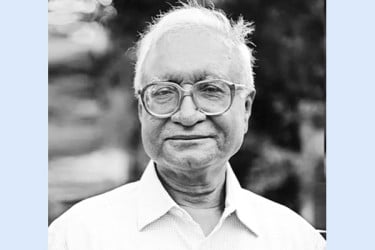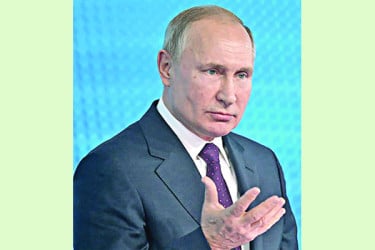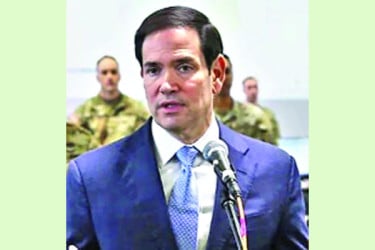মানুষ বড়, নাকি মনুষ্যত্ব? মানুষই তো বড়, মনুষ্যত্বের চেয়ে। কিন্তু যদি মানুষের মনুষ্যত্ব না থাকে তবে তো সে আর মানুষই থাকে না। আমরা যে বলি, সে তো মিথ্যা বলি না, মনুষ্যত্বহীনতায় মানুষ পশু হয়ে পড়ে। মানুষ পশু হলে পশুর চেয়েও বড় পশু হয়- যেমন আতঙ্কের দিক থেকে তেমনি নিষ্ঠুরতার দিক থেকে। মানুষের পশুত্ব অস্বাভাবিক পশুত্ব। হয়তো আতঙ্কগ্রস্ত; হয়তো নিষ্ঠুর; হয়তো দুই-ই।
মানুষের নিষ্ঠুরতার দিকটার কথা শিল্পসাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে বলা হয়েছে। মানুষ পশু হয়ে উঠেছে অর্থাৎ হিংস্র, নিষ্ঠুর, বিবেচনাহীন হয়ে পড়েছে, এমন চিত্র জীবনে যেমন পাওয়া যায়, শিল্পসাহিত্যেও তেমনি পাই। কিন্তু মানুষ তো পশু হয় শুধু নিষ্ঠুরতার দিক দিয়েই নয়, হয় আতঙ্কের, পরাজয়ের, হতাশার দিক থেকেও। যে মানুষ সন্ত্রস্ত, পরাজিত, হতাশ, সে মানুষ আর মানুষ নেই, অপরিহার্য মনুষ্যত্ব হারিয়ে সে পশুতে রূপান্তরিত হয়েছে, নিজের অজ্ঞাতেই। খাঁচার পাখি যেমন পাখি নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে; সন্ত্রস্ত, পরাজিত, হতাশ মানুষও তেমনি মানুষ নয়, যথার্থ অর্থে। এই কথাও, সন্ত্রস্তের এই মনুষ্যত্ব হারানোর কথাও, আমাদের শিল্পসাহিত্যে আছে। কিন্তু যা নেই, খুব করে নেই, যত করে থাকা উচিত ছিল ততো নেই, তা হচ্ছে- কেমন করে মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে তার বিনষ্ট মনুষ্যত্ব, সেই পথের কথা। দুঃখ আছে, কথা নেই দুঃখমোচনের।
মানুষকে ভালোবাসো, এই কথাটা নানাভাবে, বহু বিভিন্ন স্বরে ও সুরে, ইনিয়েবিনিয়ে কখনো, কখনো স্পষ্টাস্পষ্টি, কতবার বলা হয়েছে। কিন্তু কোন সে মানুষ যে মানুষকে ভালোবাসব আমি? মানুষ যদি খুইয়ে থাকে তার মনুষ্যত্ব, নিপীড়নে ও অভাবে সে যদি হারিয়ে থাকে তার মানুষ পরিচয়, তবে তাকে ভালোবাসব কেমন করে, কীসের তাগিদে, কোন প্রেরণায়? পথের পাশের কুকুরকে দেখে কে করবে অশ্রুপাত? কার হৃদয় দ্রবীভূত হবে শোকে? যাকে ভালোবাসব তাকে অবশ্যই যোগ্য হতে হবে ভালোবাসার এবং যখন যোগ্য হবে পাত্র, তখন ভালোবাসা আসবেই, শিখিয়ে দিতে হবে না, পরামর্শের আবশ্যকতা দেখা দেবে না। প্রেম উপদেশ চায় না, যোগ্য পাত্র চায়।
 মানুষকে তাই মানুষ করে তোলা চাই আগে। কিন্তু মানুষ করে তোলার অর্থটা কী? আমরা ছেলেমেয়েদের মানুষ করি, অহরহ, প্রতিনিয়ত। বিদ্যালয়ে পাঠাই, সেখানে যোগ্য, দক্ষ, অভিজ্ঞ শিক্ষকরা আছেন, তাদের শক্তিশালী প্রকৌশলী হস্তক্ষেপে ছেলেমেয়েরা মানুষ হয় অর্থাৎ লায়েক হয়। সামন্তবাদী ধ্যানধারণার সঙ্গে বুর্জোয়া আকাক্সক্ষার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একটা মূল্যবোধ গড়ে তুলে তারা মানুষ হয়। অর্থাৎ প্রধানত স্বার্থপর এবং হয়তো প্রতারক হয়। কিন্তু বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে আসে না, এলেও ঝরে পড়া আমের মুকুলের মতো ঝরে পড়ে। অকালেই শেষ হয়। আম হয় না। হলেও পাকে না। সমাজের ঝড় ও সামাজিক দুর্বৃত্তদের ঢিল খেয়ে ছিঁড়ে ঝরে পড়ে।
মানুষকে তাই মানুষ করে তোলা চাই আগে। কিন্তু মানুষ করে তোলার অর্থটা কী? আমরা ছেলেমেয়েদের মানুষ করি, অহরহ, প্রতিনিয়ত। বিদ্যালয়ে পাঠাই, সেখানে যোগ্য, দক্ষ, অভিজ্ঞ শিক্ষকরা আছেন, তাদের শক্তিশালী প্রকৌশলী হস্তক্ষেপে ছেলেমেয়েরা মানুষ হয় অর্থাৎ লায়েক হয়। সামন্তবাদী ধ্যানধারণার সঙ্গে বুর্জোয়া আকাক্সক্ষার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একটা মূল্যবোধ গড়ে তুলে তারা মানুষ হয়। অর্থাৎ প্রধানত স্বার্থপর এবং হয়তো প্রতারক হয়। কিন্তু বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে আসে না, এলেও ঝরে পড়া আমের মুকুলের মতো ঝরে পড়ে। অকালেই শেষ হয়। আম হয় না। হলেও পাকে না। সমাজের ঝড় ও সামাজিক দুর্বৃত্তদের ঢিল খেয়ে ছিঁড়ে ঝরে পড়ে।
আমাদের মধ্যে প্রকৃত মানুষ কই? স্বার্থপর ও প্রতারক তো মানুষ নয়, মনুষ্যত্বের গুণ নেই যার, দুর্বৃত্ত সে, পশু। অন্যদিকে পশুর স্তরে যে জীবনযাপন করছে সে-ও তো মানুষ নয়, তাকে আমরা যতই করুণা করি না কেন। ঘাতক অমানুষ করে তুলছে পলাতককে। প্রথম দলের মনুষ্যত্বহীনতা কেড়ে নিচ্ছে দ্বিতীয় দলের মনুষ্যত্ব। এক অমানুষ আরও পাঁচজনকে অমানুষ করে তুলছে। মনুষ্যত্বহীনতা মনুষ্যত্বহীনতার জন্ম দিচ্ছে। এটাই ব্যবস্থা। আজকের নয়, যুগযুগান্তরের। না, মানুষ করার অর্থ একটাই। সরল অর্থ মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বকে সুবিকশিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা। যারা পণ্ড হয়ে উঠেছে হৃদয়হীনতায়, নিষ্ঠুরতায় তাদের মানুষ করতে হবে। অর্থাৎ শাসন করা চাই তাদের, ধমক দেওয়া চাই। সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা চাই তার পশুত্বকে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, প্রয়োজনীয় বিষয়, যারা মনুষ্যত্ব হারিয়েছে এই পশুদের নিপীড়নে তাদের প্রতিষ্ঠিত করা মনুষ্যত্বে। দুই কারণে এর গুরুত্ব অধিক। প্রথমত মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার হারিয়ে মানুষের চেয়ে নীচু স্তরে নেমে গেছে যারা তাদের সংখ্যাই অধিক, সংখ্যায় তারা অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত নিচের মানুষদের মনুষ্যত্ব ফিরে পাওয়ার সঙ্গে ওপরের মানুষদের পুনরায় মানুষ হওয়া অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত। নিপীড়িত মানুষ উঠে না দাঁড়ালে, ধমক না দিলে নিপীড়নকারী দুর্বৃত্ত নিবৃত্ত হবে না, হয়নি কখনো। গৃহস্থের সতর্কতাই ডাকাতির ওপর সবচেয়ে বড় নিষেধাজ্ঞা।
নিপীড়িত মানুষকে তাই মানুষ করে তোলা চাই। অর্থাৎ তাকে দেওয়া চাই মানবিক অধিকার, জীবনের নিরাপত্তা, জীবিকার নিশ্চয়তা। আহার দিতে হবে, দিতে হবে বাসস্থান। কিন্তু শুধু বাঁচা তো নয়, মানুষের মতো বাঁচা, বেঁচে থাকা তো শুধু টিকে থাকা নয়। গাছ, মাছ, কীটপতঙ্গ টিকে থাকে, বেঁচে থাকে না। মানুষের মতো বাঁচার অর্থ স্বাধীনতা নিয়ে, মর্যাদার সঙ্গে বাঁচা। স্বাধীনতা কথা বলার, মতামত প্রকাশের, সংগঠন গড়ার, চলাফেরার, দেশের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের। বোবা, অক্ষম, খঞ্জ মানুষ মানুষও নয়, পশুও নয়, সে মানুষেরা বিকৃত, নয়তো ব্যঙ্গচিত্র। এ কথাও সর্বদা স্মরণ রাখা বোধ করি কর্তব্য যে স্বাধীনতা এক ও অবিভাজ্য। স্বাধীনতা শুধু যে দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তে রক্ষিত পরীক্ষিত হয় তা কখনো নয়, তার রক্ষা ও পরীক্ষার কাজ দেশের প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে অবিরাম চলতে থাকে, সর্বক্ষণ। মানুষের জীবনে যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকে, তবে স্বাধীনতা আছে এ কথা যতই বলা যাক না কেন, বাস্তবে সে দাবি সত্য হবে না। এক স্বাধীনতা অন্য স্বাধীনতার অভাবের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। স্বাধীনতার অভাব দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু তার চেয়েও বড় দুঃখের ব্যাপার আছে। সে হলো অভাববোধের অভাব। অভাব যত না আছে, তার চেয়ে বেশি আছে অভাববোধের অভাব।
অভাব সাংস্কৃতিক চেতনার ব্যাপার। সংস্কৃতি নিয়ে গৌরব, উচ্চকথন, হট্টগোল ইত্যাকার ব্যাপার অনেক করেছি, আজও করছি। কিন্তু এই যে স্বদেশি সাহিত্য সংগীত, চলচ্চিত্র, চিত্রকলা এদের বাহ্যিক সৌন্দর্যের যত বড়াই করি না কেন, এদের অভ্যন্তরে কী আছে? পোশাকের অভ্যন্তরের চরিত্রটা কী?
সেই চরিত্রের দিকে তাকালে অন্তঃসারশূন্যতার বড় বড় গর্তই চোখে পড়বে নানা স্থানে। অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব নেই, শুধু সমন্বয়ের কথাই অধিকাংশ সময়ে কোমল সুরে, কখনো বা উচ্চকণ্ঠে বলা হয়েছে। অভ্যন্তরে সংস্থাপিত বুদ্ধিবৃত্তিক তথা দার্শনিক চিন্তার স্তরটি উদ্বেগজনকরূপে সামান্য। একদা রবীন্দ্রনাথ এক ঔপন্যাসিককে বলেছিলেন এই কথা, ‘আপনি কোন রকম ঐতিহাসিক বা উপদেশিক বিড়ম্বনার মধ্যে যাবেন না এবং শীতল ছায়া, আম-কাঁঠালের বন, পুকুরের পাড়, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা, এরই মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে তরল কলধ্বনি তুলে বিরহমিলন হাসিকান্না নিয়ে যে মানব জীবনস্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাই আপনি আপনার ছবির মধ্যে আনবেন।’ এই ছবির বর্ণনাও ছবি একটা, সুন্দর ছবি। কিন্তু কোন চেতনার কথা আছে এই সুন্দর করে তুলে ধরা চিত্রের ভিতরে? এই জীবনস্রোত অবিশ্রান্ত বটে, কিন্তু সে তো ‘প্রচ্ছন্ন’ শুধু, কেবলি তরল কলধ্বনি তোলা, প্রাকৃতিক দৃশ্যের অংশ শুধু। এই বর্ণনায় যে জীবনের আদর্শ প্রতিফলিত সে জীবন মানুষের নয়। সে জীবনে মানুষের জীবন নেই, গাছগাছড়া, পশুপাখি, কীটপতঙ্গের মতো কোনোমতে টিকে থাকা আছে শুধু। রবীন্দ্রনাথের এই বর্ণনা নিঃসন্দেহে প্রতিনিধিত্বমূলক। এর পেছনে যে দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সেটাই প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি। স্মরণযোগ্য এই সত্যও যে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রকৃতির ওপর মানুষের যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংবাদ পরিবেশিত তা সব সময়ে সমর্থন করেননি, তাঁর স্বাভাবিক সমর্থন প্রকৃতি ও মানুষের প্রাচ্য-দেশীয় ঐক্যের প্রতি।
তাহলে মূল কথা হচ্ছে, দ্বন্দ্বে যাব না, খুঁজব সমন্বয়। কেন আসে না দ্বন্দ্ব? আসে না মানুষের জীবন সম্পর্কে উন্নত চিন্তা নেই বলে। মনুষ্যত্বের প্রশ্ন, অর্থাৎ মানুষের মতো বাঁচার অধিকারের প্রশ্নে যে কোনো আপস নেই, সেই দাবিতে যে অনড় থাকবে, লড়বে প্রতিনিয়ত এই বোধের অভাবই দ্বন্দ্ব-ভীরুতার জন্ম দেয়, সমর্থন জোগায় সমন্বয় পন্থার, আপসকামিতার, সুবিধাবাদিতার। নইলে দেখা যেত জীবনযাত্রার ক্ষণে ক্ষণে, পদে পদে দ্বন্দ্ব বাধছে প্রকৃতির সঙ্গে, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সঙ্গে, শাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। দেখা যেত, সেই দ্বন্দ্বে জীবনের মানদণ্ডে গুণগত পরিবর্তন আসছে। শত শত বছরের সঞ্চিত গ্লানি ও দারিদ্র্য দূর হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অভাববোধ প্রবলভাবে আসেনি। অভাববোধ ছাড়া মানুষ যে মানুষই নয়, মনুষ্যত্বহীনতার সেই চেতনা এবং মনুষ্যত্বহীনতার প্রতি ক্ষমাহীন ঘৃণা গড়ে ওঠেনি সংবিতে। তাই তো দেখি অধিকার আজও বিকাশের বিষয় যতটা না, তার চেয়ে বেশি অর্জনের বিষয় হয়ে আছে। তাই তো দেখি নিষ্পিষ্ট মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য-যন্ত্রণা নিয়ে নিম্ন-মধ্যবিত্তসুলভ প্রচুর করুণা-প্রকাশ ও অশ্রুপাত ঘটে, কিন্তু প্রতিকারের অভীষ্ট লক্ষ্য ও বাস্তব উপায় সম্পর্কে খুব কম বলা হয়। ভিক্ষা দেওয়া হয়, ভিক্ষাবৃত্তির কুফল বিষয়েও আলোকপাত করা হয়, কিন্তু যা হয় না তা হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনের কার্যকর সামাজিক-অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ। সমালোচনা থাকে, প্রতিবাদ থাকে না।
লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়