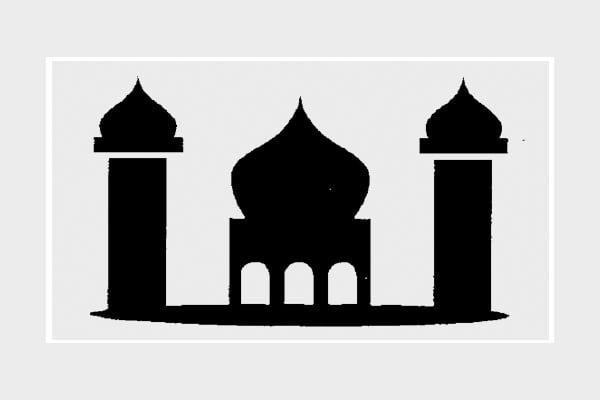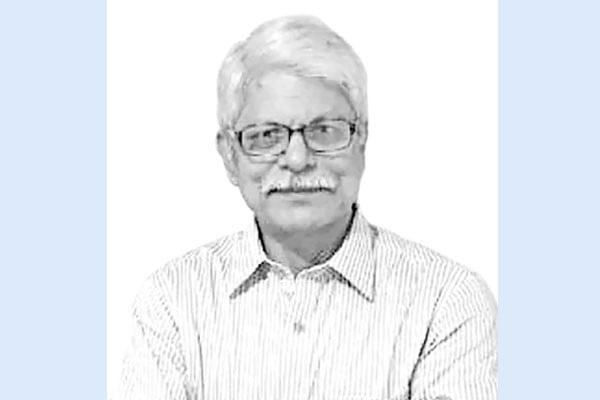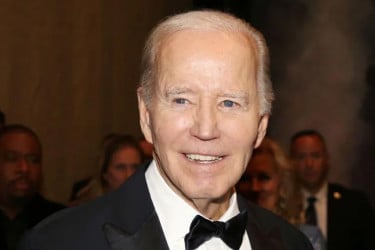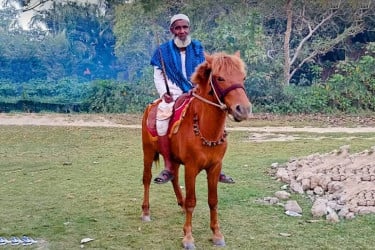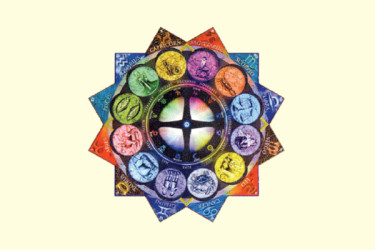জিয়াউর রহমান- একটি নাম, একটি ইতিহাস। নিজ গুণেই তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিলেন। বলা যায়, সৌভাগ্যের বরপুত্র ছিলেন তিনি। স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনি নন্দিত হবেন অনন্তকাল ধরে। মুক্তিযুদ্ধের বীর উত্তম হিসেবে তাঁর অবদানকে কৃতজ্ঞ জাতি শ্রদ্ধা করবে বছরের পর বছর। রাষ্ট্রপতি হিসেবেও জিয়াউর রহমান ছিলেন অনন্য।
 কারও কারও ধারণা, চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে তরুণ মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল কাকতালীয় ঘটনা। পরিস্থিতি তাঁকে বিদ্রোহী হতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু বাস্তব আলাদা। স্কুলজীবন থেকেই তিনি দীক্ষা নেন স্বাধীনতার পক্ষে। স্বাধীনতার পর ‘একটি জাতির জন্ম’ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। বীর উত্তম জিয়ার ভাষায়, ‘স্কুলজীবন থেকেই পাকিস্তানিদের দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা আমার মনকে পীড়া দিত। আমি জানতাম, অন্তর দিয়ে ওরা আমাদের ঘৃণা করে। স্কুলজীবনে বহু দিনই শুনেছি আমার স্কুলবন্ধুদের আলোচনা। তাদের অভিভাবকরা বাড়িতে যা বলত তাই তারা রোমন্থন করত স্কুল প্রাঙ্গণে। আমি শুনতাম, তাদের আলোচনার প্রধান বিষয় হতো বাংলাদেশ আর বাংলাদেশকে শোষণ করার বিষয়। পাকিস্তানি তরুণসমাজকেই শেখানো হতো বাঙালিদের ঘৃণা করতে। বাঙালিদের বিরুদ্ধে একটা ঘৃণার বীজ উপ্ত করে দেওয়া হতো স্কুলছাত্রদের শিশুমনেই। শিক্ষা দেওয়া হতো তাদের বাঙালিকে নিকৃষ্টতম মানবজাতি রূপে বিবেচনা করতে। অনেক সময়ই আমি থাকতাম নীরব শ্রোতা। আবার মাঝেমধ্যে প্রত্যাঘাতও হানতাম। সেই স্কুলজীবন থেকেই মনে মনে আমার একটা আকাক্সক্ষাই লালিত হতো, যদি কখনো দিন আসে, তাহলে এই পাকিস্তানবাদের অস্তিত্বেই আমি আঘাত হানব। সযতেœ এই ভাবনাটাকে আমি লালন করতাম। বড় হলাম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই কিশোরমনের ভাবনাটাও পরিণত হলো। জোরদার হলো। পাকিস্তানি পশুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার, দুর্বারতম আকাক্সক্ষা দুর্বার হয়ে উঠত মাঝেমধ্যেই। উদগ্র কামনা জাগত পাকিস্তানের ভিত্তিভূমিটাকে তছনছ করে দিতে। কিন্তু উপযুক্ত সময় আর উপযুক্ত স্থানের অপেক্ষায় দমন করতাম সেই আকাক্সক্ষাকে।’
কারও কারও ধারণা, চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে তরুণ মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল কাকতালীয় ঘটনা। পরিস্থিতি তাঁকে বিদ্রোহী হতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু বাস্তব আলাদা। স্কুলজীবন থেকেই তিনি দীক্ষা নেন স্বাধীনতার পক্ষে। স্বাধীনতার পর ‘একটি জাতির জন্ম’ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। বীর উত্তম জিয়ার ভাষায়, ‘স্কুলজীবন থেকেই পাকিস্তানিদের দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা আমার মনকে পীড়া দিত। আমি জানতাম, অন্তর দিয়ে ওরা আমাদের ঘৃণা করে। স্কুলজীবনে বহু দিনই শুনেছি আমার স্কুলবন্ধুদের আলোচনা। তাদের অভিভাবকরা বাড়িতে যা বলত তাই তারা রোমন্থন করত স্কুল প্রাঙ্গণে। আমি শুনতাম, তাদের আলোচনার প্রধান বিষয় হতো বাংলাদেশ আর বাংলাদেশকে শোষণ করার বিষয়। পাকিস্তানি তরুণসমাজকেই শেখানো হতো বাঙালিদের ঘৃণা করতে। বাঙালিদের বিরুদ্ধে একটা ঘৃণার বীজ উপ্ত করে দেওয়া হতো স্কুলছাত্রদের শিশুমনেই। শিক্ষা দেওয়া হতো তাদের বাঙালিকে নিকৃষ্টতম মানবজাতি রূপে বিবেচনা করতে। অনেক সময়ই আমি থাকতাম নীরব শ্রোতা। আবার মাঝেমধ্যে প্রত্যাঘাতও হানতাম। সেই স্কুলজীবন থেকেই মনে মনে আমার একটা আকাক্সক্ষাই লালিত হতো, যদি কখনো দিন আসে, তাহলে এই পাকিস্তানবাদের অস্তিত্বেই আমি আঘাত হানব। সযতেœ এই ভাবনাটাকে আমি লালন করতাম। বড় হলাম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই কিশোরমনের ভাবনাটাও পরিণত হলো। জোরদার হলো। পাকিস্তানি পশুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার, দুর্বারতম আকাক্সক্ষা দুর্বার হয়ে উঠত মাঝেমধ্যেই। উদগ্র কামনা জাগত পাকিস্তানের ভিত্তিভূমিটাকে তছনছ করে দিতে। কিন্তু উপযুক্ত সময় আর উপযুক্ত স্থানের অপেক্ষায় দমন করতাম সেই আকাক্সক্ষাকে।’
বলা হয়ে থাকে, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের মহান স্বাধীনতার সূতিকাগার। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যখন কিশোর, তখন ভাষা আন্দোলন তাঁর ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। বাবার চাকরির সূত্রে করাচিতে তিনি পড়াশোনা করতেন। ভাষা আন্দোলনের সময়কালে পাকিস্তানিদের বাংলাবিদ্বেষী মনোভাব জিয়াউর রহমানকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল।
তাঁর মতে, ‘পাকিস্তানি সংবাদপত্র, প্রচারমাধ্যম, পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবী, সরকারি কর্মচারী, সেনাবাহিনী আর জনগণ সবাই সমানভাবে তখন নিন্দা করেছিল বাংলা ভাষার। নিন্দা করেছিল বাঙালিদের। তারা এটাকে বলত বাঙালি জাতীয়তাবাদ। তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা এটাকে মনে করেছিল এক চক্রান্ত বলে। এক সুরে তাই তারা চেয়েছিল একে ধ্বংস করে দিতে। আহ্বান জানিয়েছিল এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের। কেউ বলত, বাঙালি জাতির মাথা গুঁড়িয়ে দাও। কেউ বলত, ভেঙে দাও এর শিরদাঁড়া। এর থেকেই আমার তখন ধারণা হয়েছিল, পাকিস্তানিরা বাঙালিদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে চায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা চায় বাঙালিদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে। কেড়ে নিতে চায় বাঙালিদের সব অধিকার। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক রূপে বাঙালিদের মেনে নিতে তারা কুণ্ঠিত।’
জিয়াউর রহমান বাবার চাকরির সূত্রে করাচিতে বসবাস করতেন। কলেজে পড়া অবস্থায় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। দক্ষ ও স্মার্ট অফিসার হিসেবে সেনাবাহিনীতে নবীন বয়সেই পরিচিত ছিলেন। বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানিদের বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব জিয়াউর রহমানকে পীড়া দিত। এ সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য, ‘পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতেও বাঙালি অফিসারদের আনুগত্য ছিল না প্রশ্নাতীত। অবশ্য গুটি কয়েক দালাল ছাড়া। আমাদের ওরা দাবিয়ে রাখত, অবহেলা করত, অসম্মান করত। দক্ষ ও যোগ্য বাঙালি অফিসার আর সৈনিকদের ভাগ্যে জুটত না কোনো স্বীকৃতি বা পারিতোষিক। জুটত শুধু অবহেলা আর অবজ্ঞা। বাঙালি অফিসার ও সৈনিকরা সব সময়ই পরিণত হতো পাকিস্তানি অফিসারদের রাজনৈতিক শিকারে। সব বড় বড় পদ আর লোভনীয় নিয়োগপত্রের শিকাগুলো বরাবরই ছিঁড়ত পাকিস্তানিদের ভাগ্যে। বিদেশে শিক্ষার জন্য পাঠানো হতো না বাঙালি অফিসারদের। আমাদের বলা হতো ভীরু কাপুরুষ। আমাদের নাকি ক্ষমতা নেই ভালো সৈনিক হওয়ার। ঐতিহ্য নেই যুদ্ধের, সংগ্রামের।’
জিয়াউর রহমানের সৈনিক জীবনের এক যুগের মধ্যেই বাঙালি সৈনিকদের প্রতি পাকিস্তানিদের অবজ্ঞার জুতসই জবাব দেওয়ার সুযোগ আসে। মুক্তিযুদ্ধের বীর উত্তম ও স্বাধীনতার ঘোষকের ভাষায়, ‘১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হচ্ছে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সে সময়ে আমি ছিলাম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যার নামে গর্ববোধ করত তেমনি একটা ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার। সেই ব্যাটালিয়ন এখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীরও গর্বের বস্তু। খেমকারান রণাঙ্গনের বেদিয়ানে তখন আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। সেখানে আমাদের ব্যাটালিয়ন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। এই ব্যাটালিয়নই লাভ করেছিল পাকবাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক বীরত্ব পদক।
ব্যাটালিয়নের পুরস্কার বিজয়ী কোম্পানি ছিল আমার কোম্পানি আলফা কোম্পানি। এই কোম্পানি যুদ্ধ করেছিল ভারতীয় সপ্তদশ রাজপুত ঊনবিংশ মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি ষোড়শ পাঞ্জাব ও সপ্তম লাইট ক্যাভালরির (সাঁজোয়া বহর) বিরুদ্ধে।
‘... পাকিস্তানিরা ভাবত বাঙালিরা ভালো সৈনিক নয়। খেমকারানের যুদ্ধে তাদের এই বদ্ধমূল ধারণা ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। পাকিস্তানি বাহিনীর সবার কাছেই আমরা ছিলাম তখন ঈর্ষার পাত্র। সে যুদ্ধে এমন একটা ঘটনাও ঘটেনি যেখানে বাঙালি জওয়ানরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। ভারতের সঙ্গে সেই সংঘর্ষে বহু ক্ষেত্রে পাকিস্তানিরাই বরং লেজ গুটিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। সে সময় পাকিস্তানিদের সমন্বয়ে গঠিত পাকবাহিনীর এক প্রথম শ্রেণির সাঁজোয়া ডিভিশনই নিম্নমানের ট্যাঙ্কের অধিকারী ভারতীয় বাহিনীর হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছিল। এসব কিছুতে পাকিস্তানিরা বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বাঙালি সৈনিকদের ক্ষমতা উপলব্ধি করে হৃৎকম্পন জেগেছিল তাদের।’
১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে মেজর জিয়াউর রহমানকে চট্টগ্রামে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটালিয়নের সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁকে চট্টগ্রাম থেকে পাঠানো হয় ঢাকায়।
১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় তিনি ছিলেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। পরে ফিরে যান চট্টগ্রামে। একাত্তরের মার্চে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের আহূত অধিবেশন স্থগিত করা হয়। এর প্রতিবাদে স্বাধীনতার আকাক্সক্ষায় উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। চট্টগ্রামে জিয়াউর রহমানের পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যাটালিয়ন কমান্ডার বাঙালি অফিসারদের ওপর নজরদারি শুরু করেন। জিয়াউর রহমানের কথায়, ‘এই সময়ে আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানজুয়া আমার গতিবিধির ওপর লক্ষ রাখার জন্যও লোক লাগায়। মাঝে মাঝেই তার লোকেরা গিয়ে আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করে। আমরা তখন আশঙ্কা করছিলাম, আমাদের হয়তো নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে কাজ করে যাই এবং তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেওয়ার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি।
আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব ...মেজর শওকতও আমার কাছে তা জানতে চান। ক্যাপ্টেন শমসের মবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নিই তাহলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। ক্যাপ্টেন অলি আহমদ আমাদের মাঝে খবর আদান-প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনসিওরাও দলে দলে বিভক্ত হয়ে আমার কাছে বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকল। তারাও আমাকে জানায় যে কিছু একটা না করলে বাঙালি জাতি চিরদিনের জন্য দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনতাম। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, উপযুক্ত সময় এলেই আমি মুখ খুলব। সম্ভবত ৪ মার্চে আমি ক্যাপ্টেন অলি আহমদকে ডেকে নিই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। ক্যাপ্টেন আহমদও আমার সঙ্গে একমত হন। আমরা পরিকল্পনা তৈরি করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে শুরু করি।
৭ মার্চে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক সমাবেশের পর পাকিস্তান বাহিনীতে বাঙালি সৈনিকদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈনিকদের দূরত্ব বাড়তে থাকে। বাঙালিদের দেখা হতো অবিশ্বাসের চোখে। ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরের জাহাজ থেকে অস্ত্র নামানোর জন্য পাকিস্তানি বাহিনী জোর করে বন্দরমুখী রাস্তা দখলে নেয়। ওই সময় জনতার ওপর পাকিস্তানি বাহিনী শক্তি প্রয়োগ করে। মেজর জিয়াউর রহমানকে নৌবাহিনীর ট্রাকে করে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। জিয়াউর রহমান বুঝে ফেলেন তাঁকে চিরতরে শেষ করার ষড়যন্ত্রে এঁটেছে পাকিস্তানিরা। তিনি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেন। বন্দি করেন তাঁর কমান্ডিং অফিসারকে। তাঁকে নিয়ে আসেন নিজেদের ব্যাটালিয়নে। মেজর শওকত ও অন্যান্য বাঙালি অফিসারকে বললেন বিদ্রোহের কথা। তাঁরাও সম্মতি জানালেন তাতে। পরদিন কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে গিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন মেজর জিয়াউর রহমান। এভাবেই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।
♦ লেখক : বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব, সাবেক সংসদ সদস্য ও ডাকসুর সাবেক জিএস