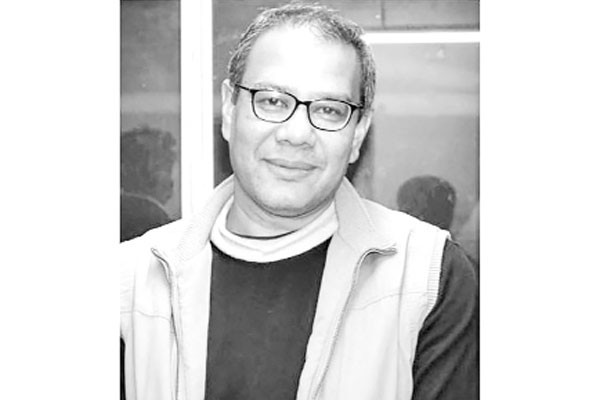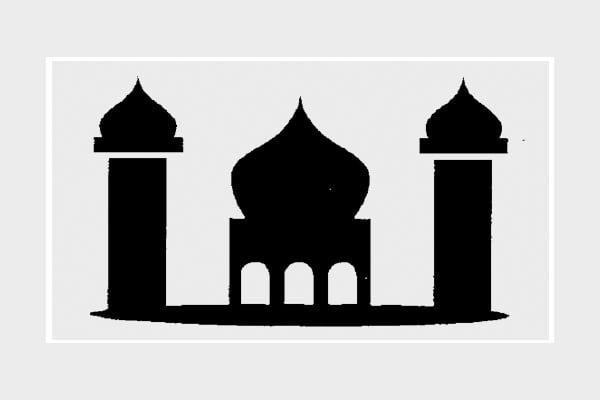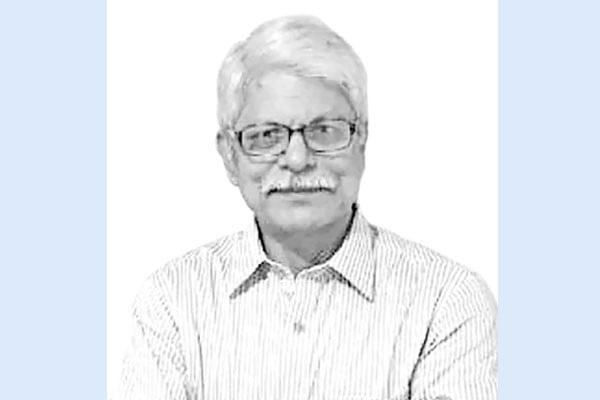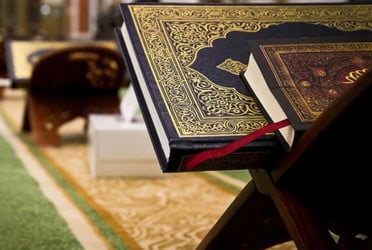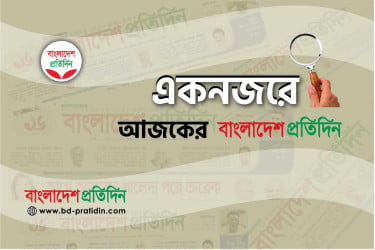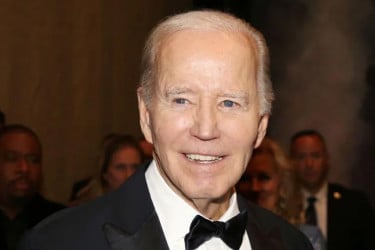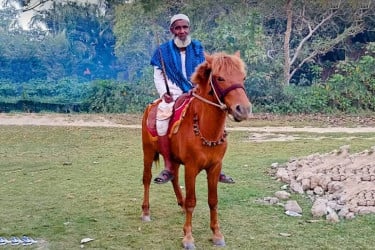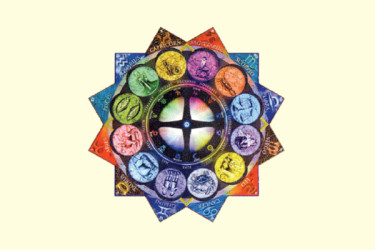১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলা ভূখন্ড পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হয়। কার্যত পাকিস্তান রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমর্থনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক দূরত্ব অনেক। কৃষ্টিগত পার্থক্যও তীব্র। এতদসত্ত্বেও পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরিতে পূর্ব বাংলার মানুষের পূর্ণ সমর্থন ছিল। ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধার মনস্তত্ত্বটি বোধ করি এর অন্যতম কারণ। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র-কেন্দ্রের ক্ষমতা-কর্তৃত্বের কারণে এটি শুরু থেকেই অনাস্থা ও আশঙ্কার মধ্যে পড়ে। বলা হয়, ১৯৩৭ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান-চিন্তার সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা উর্দুর বিষয়টি সহজভাবে মিলিয়ে নেন। পরে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ জিয়াউদ্দিন আহমদকে স্বাধীন পাকিস্তানের শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিকল্পনার দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনিও ভারতের হিন্দি ভাষার ন্যায় পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা উর্দুর বিষয়টি বিবেচ্য করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে যৌক্তিকভাবে তুলে ধরেন; তখন তিনি উপস্থিত সবার প্রবল উষ্মার মুখে পড়েন। পাকিস্তান গণপরিষদের কর্তাব্যক্তিরা একে বিভ্রান্তিমূলক আখ্যা দেন। ফলে তাঁর প্রস্তাবটি একপ্রকার অগ্রাহ্য হয়। পরে ২৬ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। ১১ মার্চ ‘দাবি দিবস’ পালিত হয়। এবং ওই দিন ঢাকায় ধর্মঘট হয়। ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’-এর নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলনের মুখে অনেকে গ্রেপ্তার হন। এবং তৎকালীন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে আপস করে ছাত্র-জনতার আট দফা দাবি মেনে নেন। মার্চ মাসেই পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসেন। তিনি বাংলা ভাষার দাবিটি দ্ব্যর্থহীনভাবে নাকচ করে দেন। পূর্ব পাকিস্তানে তেভাগা, কৃষক-শ্রমিক স্বার্থ, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, লবণসংকট, দুর্ভিক্ষ, শিক্ষা সমস্যা-শিক্ষাসংকট ইত্যাদি সদ্য স্বাধীন ও আশাপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মনে বিপরীতাত্মকভাবে নব্য-ঔপনিবেশিক পরাধীনতা ও হতাশার চূড়া তৈরি করে। নৈমিত্তিক জীবনযাপনে পূর্ব বাংলার মানুষ নানা রকম অবহেলার শিকার হয়। উপদ্রুত বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলায় একধরনের তাঁবেদার ও বশংবদ শ্রেণি তৈরির অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়। সে কারণে জনবিচ্ছিন্ন প্রশাসন নানাভাবে অনৈতিক ও দুর্নীতিগ্রস্তও হয়ে পড়ে। একধরনের জাতিগত অবহেলা আর অনিষ্টের আশঙ্কায় সাতচল্লিশ সালের সেপ্টেম্বরে ভাষার প্রশ্নে যখন ‘তমদ্দুন মজলিস’ ও সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে, এরপর সেটি ছিল আন্দোলনের মৌল সূচনা। যা প্রবলভাবে নানামুখী হয়ে পড়ে। যেমন তমদ্দুন মজলিসের পুস্তিকায় পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে যৌক্তিকতা তুলে ধরেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী মোতাহার হোসেন ও অধ্যাপক আবুল কাশেম প্রমুখ। কিন্তু এর বিপরীতে সরকারের অবস্থান কঠোর হলে তা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যন্ত এলাকায় অনেকেই এ আন্দোলনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। ক্রমশ তা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, ছাত্র-জনতা ছাড়িয়ে সব শ্রেণি-বর্ণ-পেশার মানুষের আবেগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে গঠিত হয় ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’। সর্বদলীয়ভাবে এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির এ আন্দোলন শুধু শহর-বন্দর নয়- প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে। প্রসঙ্গত, শুধু ভাষার আন্দোলন নয়, এ সময় রাজনৈতিক ডামাডোলও বাড়ে। মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, আওয়ামী মুসলিম লীগসহ অন্যান্য দল দুর্নীতি-অব্যবস্থাপনা ও লুটপাটের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করে। শামসুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, তাজউদ্দীন আহমদ, কামরুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আতাউর রহমান প্রমুখ নেতা রাজনৈতিক মত ও পথে ভিন্ন হলেও, সরকারবিরোধী আন্দোলনে সভাসমিতি, জেলজুলুম উপেক্ষা করে মানুষের অধিকারের প্রশ্নে সম্মিলিত সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হন। রাজনৈতিক দাবির সঙ্গে ভাষার দাবিটি তখন অনেকটা এক হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রভাষা উর্দুর নামে বাংলা ভাষার প্রতি যে অপমান ও অবজ্ঞা সেটি কেউ সহ্য করবে না- ফলে ১৯৫১ পর্যন্ত এ নিয়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তেমন কিছু ঘটায়নি। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ব বাংলার ভাষা প্রশ্নের বিষয়টি সভাসমিতিতে একপ্রকার এড়িয়েই যান। কিন্তু জনমনে ক্ষোভ ছিল। অমীমাংসিত বিষয়গুলোর কর্মপ্রয়াসে একপর্যায়ে ‘পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিনের এ সম্মেলনে ভাষা-সংস্কৃতির বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। কিন্তু এসব এক প্রকার অগ্রাহ্য করে অযৌক্তিকভাবে আরবি হরফে বাংলা লেখার ‘তত্ত্ব’ হাজির করা হয়। ‘পূর্ব বাঙলার ভাষা কমিটি’ গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি সম্মেলনের ফলে আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়।
সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ততার আন্দোলন অধিক দুর্বার হয়ে ওঠে- যখন ১৯৫২-এর ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন আগের আট দফার সঙ্গে প্রতারণা করে জিন্নাহর বক্তৃতার প্রতি অভিন্ন সমর্থন প্রকাশ করেন। এর প্রতিবাদে তাৎক্ষণিক ধর্মঘট হয়। এবং আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ নতুনভাবে গঠিত হয়। তবে এর আগেই ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫১ ‘বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ’ ইশতেহার প্রকাশ করে এবং তাতে বলা হয় : ‘স্থানীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি স্থাপন করুন ও বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করুন’। ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট এবং রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ভাষার দাবিতে অনড় থাকারও ঘোষণা আসে। কিন্তু সরকার এর বিপরীতে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করে, সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আসে। অলি আহাদ, শামসুল হক, গাজীউল হক প্রমুখ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বেলা ১১টায় সমাবেশ করেন এবং ১০ জন গুচ্ছ করে মিছিল করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তৎপর হলে পুলিশ ধরপাকড়ের একপর্যায়ে গুলিবর্ষণ করে এবং সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার নিহত হন। পরদিন বিশাল শোকমিছিল বের করলে পুলিশের গুলিতে শফিউর মারা যান। আন্দোলন দেশজুড়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। এরপর বাকি ইতিহাসটুকু ধরেই অগ্রবর্তী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়।
♦ লেখক : সভাপতি, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়