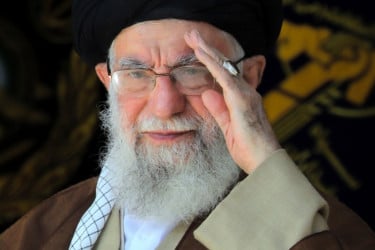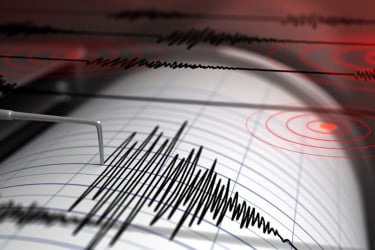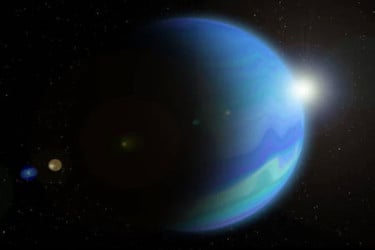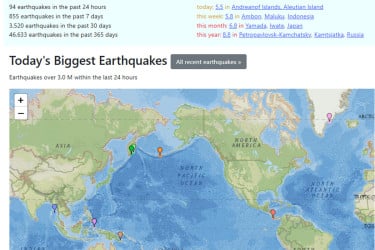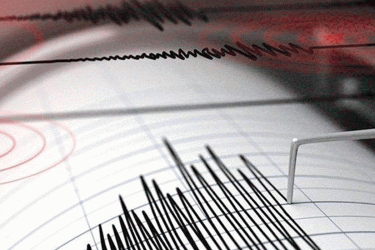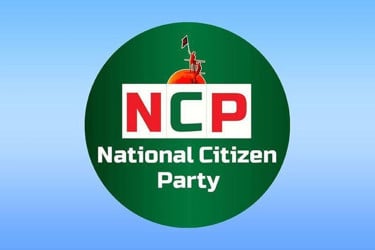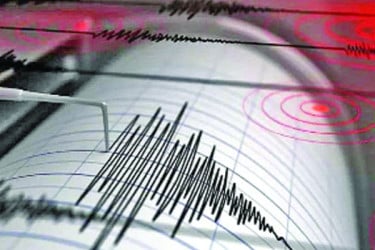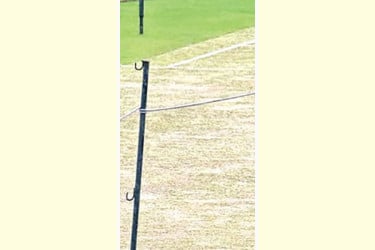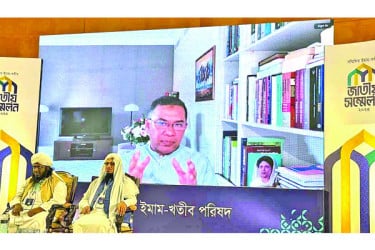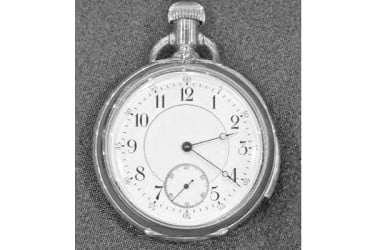বাংলাদেশের রাজনীতি আজ এক গভীর অবিশ্বাসের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। একদিকে শত্রু-মিত্রের খেলা, অন্যদিকে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা সব মিলিয়ে রাজনীতির ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। অথচ এই সংকট হঠাৎ আসেনি; এর শিকড় আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চর্চার গভীরে।
ইতিহাসের শিকড়
বাংলার রাজনীতিতে অবিশ্বাস নতুন নয়। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটেছিল তাঁর নিজের মহলের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে। মীর জাফরের মতো সহযোগীরা ব্যক্তিস্বার্থে ব্রিটিশদের হাত শক্ত করেছিল। ফলে বাংলার স্বাধীনতা হারায়। ব্রিটিশরা এখান থেকেই শিখেছিল ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ বা বিভাজন করে শাসনের কৌশল। বঙ্গভঙ্গ, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও শিক্ষানীতিতে বৈষম্য সবই সেই অবিশ্বাসের রাজনীতির ফল। ইতিহাসের সেই ধারা আজও অন্যরূপে বয়ে চলেছে।
শত্রু-মিত্রের খেলা
স্বাধীনতার পরও এই ঐতিহাসিক ধারা থামেনি। মুক্তিযুদ্ধোত্তর রাজনীতিতে আদর্শের জায়গা নিয়েছে ক্ষমতা ও স্বার্থের প্রতিযোগিতা। একসময়ের সহযোদ্ধারা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে শত্রুতে পরিণত হন। ১৯৯০ সালের গণ অভ্যুত্থানের পর যে ঐক্যের রাজনীতি দেখা গিয়েছিল, তা দ্রুতই মøান হয়ে যায়। ২০০৬ সালের পর রাজনীতি আবার মেরূকৃত হয়ে পড়ে। গতকাল যে ছিল প্রতিপক্ষ, আজ সে-ই জোটসঙ্গী; কাল আবার শত্রু। এই ‘পাল্টা-গেম’ জনগণকে বিভ্রান্ত ও ক্লান্ত করেছে।
জুলাই সনদ ও গণভোট : আস্থার পরীক্ষা
ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশে যে গণভোটের প্রশ্নটি নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটি এখন রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। প্রশ্নটি হলো :
‘আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং এর তফসিল-১-এ সন্নিবেশিত সংবিধান সংস্কার-সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন?’
কমিশনের মতে, প্রয়োজনে ‘খসড়া বিলের’ শব্দ দুটি বাদ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই প্রশ্নটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে ভিন্নমত বা ‘নোট অব ডিসেন্ট’-এর কোনো প্রতিফলন গণভোটে বিবেচনায় আসবে না। অর্থাৎ জনগণ যদি জুলাই সনদের পক্ষে ভোট দেন, তবে সংবিধান সংস্কারের ৪৮টি প্রস্তাব সরাসরি কার্যকর হবে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমতের কোনো স্থান থাকবে না।
এটি ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ দেশের সব ভোটার যে সংবিধান সংস্কারের ৪৮টি প্রস্তাব পুরোপুরি বোঝেন বা সমর্থন করেন, তা বলা কঠিন। অনেকেই কিছু প্রস্তাবের পক্ষে, কিছু প্রস্তাবের বিপক্ষে। কিন্তু ভোটদানে তাদের সামনে থাকবে কেবল দুটি বিকল্প ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’। এমন কাঠামো জনগণের বিচারের সূক্ষ্মতা ও বহুমাত্রিক মতামত প্রকাশের সুযোগকে সীমিত করে।
ঐকমত্য কমিশনের উদ্দেশ্য হয়তো ছিল জুলাই সনদের প্রস্তাবগুলোকে বৈধতা দেওয়া। কিন্তু এই প্রশ্নপদ্ধতি আসলে রাজনৈতিক ঐকমত্য নয়, নতুন বিভাজনকে উসকে দিতে পারে। জুলাই সনদ পাস হলে ভবিষ্যতের সংসদ কেবল কমিশনের নির্ধারিত প্রস্তাব অনুযায়ী সংবিধান সংশোধনে বাধ্য থাকবে যা রাজনৈতিক দলগুলোর নীতি, ইশতেহার ও জনমতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করবে।
বিএনপি ইতোমধ্যেই কিছু প্রস্তাব যেমন সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বভিত্তিক উচ্চকক্ষ গঠন বা প্রধানমন্ত্রী একাধিক পদে থাকতে না পারা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। যদি গণভোটে সনদ অনুমোদিত হয়, তাহলে বিএনপি পরবর্তী নির্বাচনে জয়ী হলেও এই সংস্কারগুলোর বাস্তবায়ন তাদের ওপর বাধ্যতামূলক হবে। প্রশ্ন হলো, এমন বাধ্যবাধকতা কি গণতান্ত্রিকভাবে গ্রহণযোগ্য?
আরও একটি বাস্তবতা হলো, যদি বিএনপি গণভোটে সনদের বিরোধিতা করে, তবে তা গণভোটকে দ্বিদলীয় মেরূকরণের নতুন মঞ্চে পরিণত করবে। এতে জনগণ বিভ্রান্ত হবে, রাজনৈতিক সহমতের পরিবর্তে মুখোমুখি অবস্থান আরও তীব্র হবে। আগের তিনটি গণভোটের অভিজ্ঞতা বলছে, এ ধরনের ভোটে জনগণের অংশগ্রহণ সাধারণত কম থাকে এবং বর্জনের ডাক পরিস্থিতিকে আরও অস্থিতিশীল করে তোলে।
সবচেয়ে যুক্তিসংগত হতো যদি গণভোটটি জাতীয় নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত হতো। নির্বাচিত সরকার সংসদে গিয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য ও নির্বাচনি ইশতেহারের আলোকে সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন করলে জনগণ তখন স্পষ্ট প্রেক্ষাপটে মত দিতে পারত। ঐকমত্য কমিশন দীর্ঘ পরিশ্রমে যে জুলাই সনদ তৈরি করেছে, তা গণভোটের প্রস্তাবে এসে আস্থার পরীক্ষায় হোঁচট খাচ্ছে। এ গণভোট দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।
তরুণ ও ছাত্ররাজনীতি : আস্থার নতুন সংকট
বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তরুণদের হাতে। একসময় ছাত্ররাজনীতি ছিল আদর্শ, নীতি ও ত্যাগের প্রতীক। কিন্তু আজ এর বড় অংশই ক্ষমতা ও পদলাভের প্রতিযোগিতায় নিমজ্জিত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও নিয়োগে প্রভাব বিস্তার করছে, যা গণতন্ত্র নয়, বরং দলীয় প্রভাবের সম্প্রসারণ। তরুণরা রাজনীতিকে জনগণের সেবার পথ নয়, বরং ব্যক্তিগত সুবিধার সিঁড়ি মনে করছে- এটি ভবিষ্যতের জন্য এক অশনিসংকেত।
বিশ্বরাজনীতির তুলনা
এই সংকট শুধু বাংলাদেশের নয়। ভারতের রাজনীতিতেও মেরূকরণ ও অবিশ্বাস প্রবল; পাকিস্তানে সেনাবাহিনী ‘নিরপেক্ষতার’ ছদ্মবেশে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অন্যদিকে পশ্চিমা গণতন্ত্রে সরকার বদল মানে নীতির ধারাবাহিকতা, ব্যক্তিগত শত্রুতা নয়। যুক্তরাজ্য, জার্মানি বা কানাডায় প্রতিপক্ষকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হয়, শত্রু হিসেবে নয়। আমাদের দেশে সরকার বদল মানে সব নতুন করে শুরু। যা প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতাকে ধ্বংস করে দেয়।
শিক্ষণীয় উদাহরণ : জাপানের উন্নয়ন
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপান ধ্বংসপ্রায় অবস্থা থেকে দ্রুত উন্নয়নের পথে ফিরে আসে। এর মূল কারণ ছিল নেতৃত্বের নৈতিকতা, স্থায়ী নীতিমালা, জনগণের আস্থা এবং শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে সরকার জনগণের আস্থা অর্জন করেছিল। প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেরেছিল- নির্বাচন, বিচার, প্রশাসন, সবই আস্থার ভিত্তিতে। বাংলাদেশের জন্য এখানেই শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। আস্থাভিত্তিক রাজনীতি, নৈতিক নেতৃত্ব, স্বচ্ছ প্রশাসন ও শিক্ষায় বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে পারলে আমাদেরও জাপানের মতো স্থিতিশীল উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব।
আসন্ন সরকারের সতর্কবার্তা
যে সরকারই আগামী দিনে ক্ষমতায় আসুক যদি সুশাসন, ন্যায়বিচার ও আস্থার রাজনীতি অনুসরণ না করে, তবে তার ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলেও, যদি তারা জনগণের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়, প্রশাসনিক স্থিতি ও আন্তর্জাতিক আস্থা দুটোই হারাবে। সুশাসন মানে শুধু দুর্নীতি দমন নয়, বরং স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং জনগণের আস্থার পুনর্গঠন। যে সরকার এই নীতিগুলো মানবে না, সে সরকার দীর্ঘ মেয়াদে টিকবে না- এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।
অনিশ্চয়তার দোলাচল
রাজনীতিতে অবিশ্বাস জাতিকে এক অনিশ্চয়তার দোলাচলে ঠেলে দিয়েছে। নির্বাচন, অর্থনীতি, বিনিয়োগ, শিক্ষার ভবিষ্যৎ- সবই এখন দোলাচলে। যে রাষ্ট্রে নাগরিক আস্থা ভেঙে যায়, সেখানে উন্নয়নের মাটি শক্ত থাকে না।
আগামীর দিকনির্দেশনা : আস্থার রাজনীতি
এই অবিশ্বাসের ঘূর্ণি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে দরকার আস্থার রাজনীতি।
১. সংলাপ ও সহনশীলতা : মতভেদ মানেই শত্রু নয়।
২. প্রাতিষ্ঠানিক আস্থা পুনর্গঠন : নির্বাচন কমিশন, সংসদ ও বিচারব্যবস্থা জনগণের বিশ্বাসের প্রতীক হতে হবে।
৩. তরুণদের নৈতিক নেতৃত্ব : রাজনীতি মানে হবে নীতি, যুক্তি ও সেবা।
ভবিষ্যৎ ভাবনা
১. সুশাসন ছাড়া কোনো সরকার দীর্ঘ মেয়াদে টিকবে না।
২. ‘সনদ’ ও ‘গণভোট’ জনমতের প্রকৃত প্রতিফলন হতে হবে, আনুষ্ঠানিকতা নয়।
৩. তরুণ প্রজন্ম যদি আস্থাভিত্তিক রাজনীতি না শেখে, আগামী নেতৃত্বও অনিশ্চিত থাকবে।
৪. শিক্ষা ও নাগরিক সচেতনতা রাজনীতিতে আস্থার ভিত্তি গড়তে পারে।
৫. আস্থাভিত্তিক রাজনীতি গড়ে উঠলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ‘বিশ্বাস ও সহযোগিতার মডেল’ হতে পারে।
বাংলাদেশের রাজনীতি আজ এক সংকটময় সময়ে যেখানে সবাই একে অপরকে সন্দেহ করে, অথচ একে অপরকেই প্রয়োজন। ইতিহাস প্রমাণ করেছে- যে জাতি বিশ্বাস হারায়, সেদিক হারায়।
এখনই সময় রাজনীতিকে সনদ, আস্থা ও সুশাসনের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করার। রাজনীতি যদি আস্থা ফিরে পায়, জাতিও ফিরে পাবে তার নৈতিকতা, স্থিতি ও ভবিষ্যতের আলো।
লেখক : অধ্যাপক ও গবেষক, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম