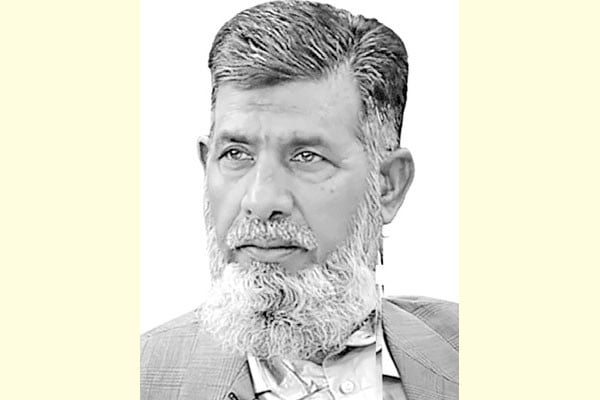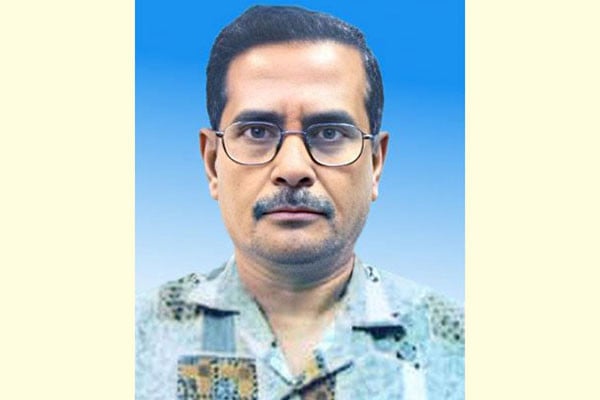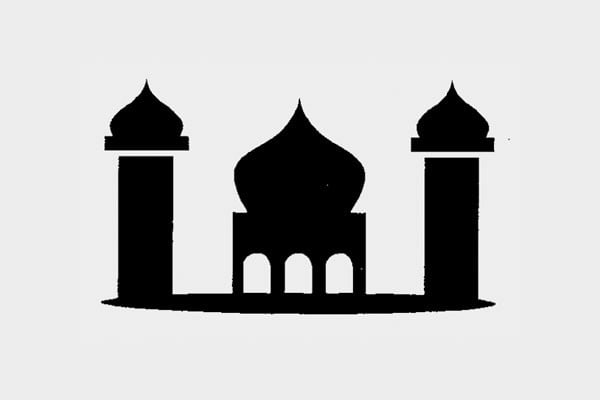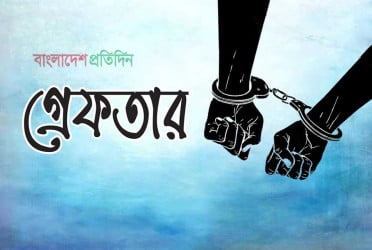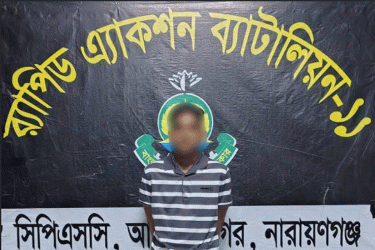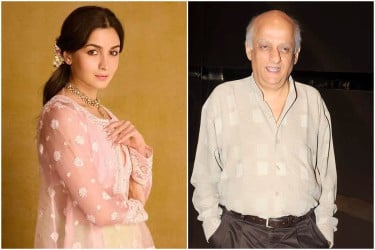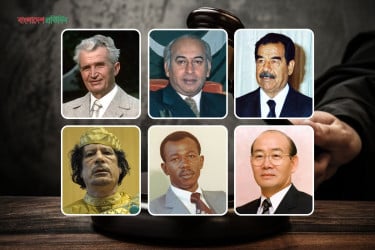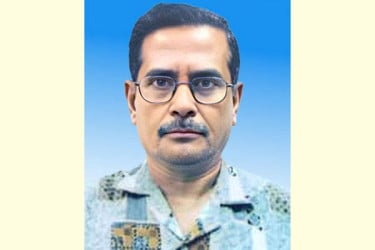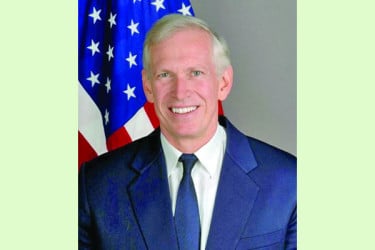ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন ১৭৫২ সালে। সে সময় বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব ছিলেন আলিবর্দি খাঁ। এই সময় মূলত স্বাধীন বাংলার শেষ দিনগুলোর মধ্যে পড়ে। এ সময়ের মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলার বিপর্যয় পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধ সাধারণ মানুষের মনে প্রাথমিকভাবে কোনো বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারার কারণ হিসেবে অনেকে মনে করেন, তখন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে যুদ্ধ সাধারণ ক্ষমতার পরিবর্তন বলেই তারা ধরে নিয়েছিল। এটা মনে হওয়ার বড় কারণ নবাব আলিবর্দি খাঁ ও তাঁর সমসাময়িক সময় এবং কিছুটা পূর্ব থেকে বাংলা মূলত উপদ্রুত অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। এ সময়ে বাংলায় বর্গি তথা ঠগি দস্যুদের আক্রমণ, লুট, আফগানি আক্রমণ সব মিলে বাংলার জনগণ এতটাই নিঃস^ হয়ে পড়েছিল যে তারা খাজনা দিতে অসমর্থ হয়েছিল।
যেহেতু তখন খাজনা উৎপাদিত ফসলে হতো, তাই কোষাগার শূন্যে পরিণত হয়েছিল। বাংলার মানুষের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে মায়েরা ভয়ে বর্গি দস্যুদের নাম উচ্চারণ না করে, ছেলে ভোলানো ঘুমপাড়ানি গানে বর্গিদের নামে ভয় দেখাত। বিখ্যাত সেই লোককথা ‘ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গি এলো দেশে/ বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে?’ বুলবুলি কথাটা বর্গিদের নামের প্রতীক হিসেবে বলা হতো। বর্র্গিরা মাথায় লাল কাপড় বেঁধে লুটতরাজ করত। সেটি বোঝাতেই বুলবুুলি বোঝানো হতো। কারণ বুলবুলির মাথায় লাল ঝুঁটি রয়েছে। বর্গি আফগানি হায়নাদের চেয়েও বড় কথা ছিল- তত দিনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জেঁকে বসেছিল। সামগ্রিক দুর্ভোগে সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরেছিলেন ভারতচন্দ্র তাঁর মঙ্গলকাব্যে। তাঁর কাব্যের একটি শ্লোক এখনো মানুষের মুখে মুখে ঘুরে ফেরে। আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। দেবীকে তাঁর নৌকায় পেয়ে সে বর চেয়েছিল ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।’
গোলা ভরা ধান, গোয়ালে গাভি, পুকুর ভরা মাছের যুগে দুধেভাতে থাকা অধিক সচ্ছলতার প্রতীক কি না, আজকের যুগে দাঁড়িয়ে তা বলা যাবে না। এখন দুধভাত দূরের কথা মাছভাতকেও ভাবা যায় না মধ্যবিত্তের জন্য। দেশের সাধারণ মানুষ পুঁটি মাছ থেকে জাতীয় মাছ ইলিশে হাত দিতে পারে না। শাকভাতের কথা হয়তো এখন মধ্যবিত্ত ভাবছে। সে কারণে ভারতচন্দ্র এখনো সমভাবে গ্রহণযোগ্য। প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, মাসে অন্তত এক দিন না খেয়ে থাকে শতকরা ৯ শতাংশ মানুষ। দেশে দারিদ্র্য বেড়েছে ২৮ শতাংশ। অন্য প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে দারিদ্র্য হ্রাসের ধারাবাহিক অগ্রযাত্রা তিন দশক ধরে চললেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেই ধারা উল্টো দিকে ঘুরছে। গবেষণায় উঠে এসেছে, দেশে বর্তমানে প্রতি চারজনের একজন দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। ধারণা করা হচ্ছে, পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, সামান্য আঘাত অসুস্থতা চাকরি হারানো কিংবা হঠাৎ সংকট তাদের দরিদ্রের কাতারে ঠেলে দিতে পারে। কেন এ অবস্থা সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত হচ্ছে, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বিনিয়োগ স্থবিরতা, কর্মসংস্থান না হওয়ায় করোনা মহামারি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাসহ ১০টি কারণ রয়েছে। এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী বিগত তিন মাসে কোটিপতির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে, ১ লাখ ২২ হাজার ৮১-তে। গত তিন মাসে বেড়েছে ৪ হাজার ৯৫৪। বাংলাদেশে এখন মধ্যবিত্তের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে চিত্র অন্যভাবেও উঠে এসেছে। বলা হচ্ছে, গাজীপুরে অসংখ্য গার্মেন্ট বন্ধ হওয়ায় উত্তরা এলাকায় ছিনতাই বেড়েছে। নিরাপত্তাহীনতা এসব এলাকায় নতুন মাত্রা নিয়েছে। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনা করলে এটা সবাই স্বীকার করবেন যে সাধারণ মানুষের বিন্দুমাত্র নিরাপত্তা নেই।
দেখা যাচ্ছে, খবর প্রকাশিত হওয়ার পর এক এলাকায় বন্ধ হয় তো অন্য এলাকায় শুরু হয়। কোনো জটিল বা বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট ছাড়াই বলা যায়, বাজারে পণ্যমূল্য কমেনি অথচ প্রতিদিন মানুষ কর্মহীন হচ্ছে। নতুন কোনো কর্মসংস্থানের বিপরীতে দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অজানা আশঙ্কা ভর করেছে। চাঁদাবাজি সন্ত্রাস বহাল রয়েছে। ঘুষ-দুর্নীতির বিন্দুমাত্র সুরাহা করা যায়নি। কথাবার্তা যা-ই হোক ফলাফল একই থাকল। একটি গণ অভ্যুত্থানের পর মানুষের প্রত্যাশার সঙ্গে কোনো ধরনের সংগতি স্থাপন করতে পারেনি সংশ্লিষ্টরা। উপরন্তু রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা অস্থিরতা বাড়ছে। পরিস্থিতি যে দিনদিন ঘোলাটে হচ্ছে বোধ করি তা লিখে বলার প্রয়োজন নেই। বাংলায় যে কটি বড় দুর্ভিক্ষ হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ’৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ। নবাবি আমল থেকে ব্রিটিশরা রাজ্য দখলে নেওয়ার পর যে ভূমিকর ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল তার বিষবাষ্পই হলো ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। এই মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষের সময়ও কেউ কেউ প্রহসন করে বলেছেন, বাংলায় কি এতই দুর্ভিক্ষ যে দিনান্তে এক বেলা পোলাউও খেতে পারে না? ইতিহাস বলে এই দুর্ভিক্ষে এত লোক মারা গিয়েছিল যে শিয়াল কুকুর শকুনে খেয়েও শেষ করতে পারেনি। মৃতের সৎকার করার মতো কেউ ছিল না। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, ইংরেজদের বাংলা দখলের পর শত শত নৌকা-জাহাজে বাংলার সম্পদ ব্রিটেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জমির ওপর করারোপের ফলেই কৃষক সর্বস্বান্ত হয়েছিল। সে অবস্থা এমন ছিল যে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে মানুষ নিজেই নিজেকে দলিল করে বিক্রি করেছে। এসব কথা ইতিহাসেই উল্লেখ রয়েছে। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ নিয়েও বলা হয়, এটিও ছিল অব্যবস্থাজনিত। এসব দুর্ভিক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত, সর্বস্বান্ত হয় সাধারণ মানুষ। আর লাভবান হয় বিত্তবানরা। এই লুটপাট কখনো দেখা যায় না খালি চোখে। আস্তে আস্তে বোঝা যায়। যা দু-একটা খবর বেরোয় তাকে হয় আমরা উড়িয়ে দিই, নয়তো অবজ্ঞা করি। রাজনৈতিক সমাবেশে সভা মিছিলে নির্বাচনের জন্য কোটি কোটি টাকা রাজনীতিবিদরা খরচ করেন, কালো টাকা সাদা করার আইন প্রণীত হয় অথচ সম্প্রতি দুজন সাংবাদিক আত্মহত্যা করেছেন। আমরা নিয়তই বাক্স্বাধীনতার কথা বলছি।
এ নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। মত-পথ নিয়ে কথা বলা নয়। সত্যি হচ্ছে আর্থিক সংকট সামাল দিতে না পেরে অন্য কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে শেষমেশ আত্মহননের পথই বেছে নিয়েছেন। এটি সমাজের একটি বড় চিত্র। নমুনা হিসেবেও গ্রহণ করা যেতে পারে। আমরা যারা এখনো কায়ক্লেশে বেঁচে আছি, তাদের মূলত বিদ্রুপ করছে এই মৃত্যু। বারবার ধিক্কার দিয়ে বলছে, একটি স্বাধীন দেশে যদি বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকে অধিকতর পছন্দনীয় মনে করতে হয়, তাহলে স্বাধীনতার অর্থ কী? ’৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতীয় স্বাধীনতার পর প্রথম বার্ষিকী পালন উপলক্ষে এবং কবিতায় একজন প্রশ্ন করেছিলেন স্বাধীনতার অর্থ কী? সন্ধ্যার পর যখন মাঠের সব পতাকা নামিয়ে নেওয়া হলো, রঙিন কাগজের ব্যানার ফেস্টুন নামানো হলো তখন থেকে গেল শুধু বাঁশটা। প্রথম স্বাধীনতা দিবস দেখতে আসা ভারতীয় কৃষকের মনে হয়েছিল এটাই কি তাহলে স্বাধীনতা? না বুঝে কৃষকের ভাষায় হয়তো এ কথা। আমরা তা বলব না। তবে আমরা যে একের পর এক বৈষম্য নিরসনের লড়াই করছি তার মূলে কী? অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। এখন সংগত বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, এর থেকে মুক্তির উপায় কী?
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। ক্ষুধাতুর শিশু চায়না স্বরাজ, তার কাছে পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। সে কারণেই সময় এসেছে মানুষের জন্য কিছু করার। মানুষ কাজ চায়, বাঁচতে চায়। আমাদের মতো দেশ যেখানে নাগরিকরা রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক নিরাপত্তাবলয়ে নেই, সেখানে নিজে করি কর্মসূচির অধীনেই বাঁচতে হয়। এই বাঁচার পথ হচ্ছে কাজ। আমাদের অর্থনীতির প্রাণ বলে কথিত যে রেমিট্যান্স অর্থ, সেটি আসলে কায়িক শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত। এই অর্থ আয় করতে গিয়ে সমুদ্রে মরছে, নিখোঁজ হচ্ছে, দালালের হাতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে, মায়ের কোল খালি হচ্ছে। অথচ দেশে কাজ করার সুযোগ পেলে এই শ্রমশক্তি থেকে দেশ অনায়াসে উপকৃত হওয়ার সুযোগ ছিল। আমরা মাঝে মাঝেই দেশকে সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন উন্নত ও মাঝারি উন্নত দেশের সঙ্গে মিলিয়ে কথা বলি। আসলে আমরা কোথায় আছি, আমাদের মাথাপিছু প্রকৃত আয় কত তা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। আমাদের অর্থনীতি এখনো করনির্ভর। করনির্ভরতা হচ্ছে শোষণের ব্যবস্থা।
উৎপাদনের আওতা বাড়ানো না গেলেও মানুষের আয়-কর্মসংস্থান বাড়ানো সম্ভব নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির আনুপাতিক হারের সঙ্গে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা না গেলে শুধু কথামালা মূল সমস্যা সমাধানে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখবে না, রাখতে পারে না। সম্প্রতি নেপালে যে গণ অভ্যুত্থান বিপ্লব হয়ে গেল, যারা নাকি বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নিয়েছে; তাদের দেশেও কর্মসংস্থানের অভাব দুর্নীতি বড় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মানুষকে খেয়েপরে বেঁচে থাকার সাধারণ গ্যারান্টি দেওয়া না গেলে রাজনীতির যত বড় বড় বুলি আওড়ানো হোক না কেন, তা আষাঢ়ে গল্পই থেকে যাবে।
লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক, কলামিস্ট