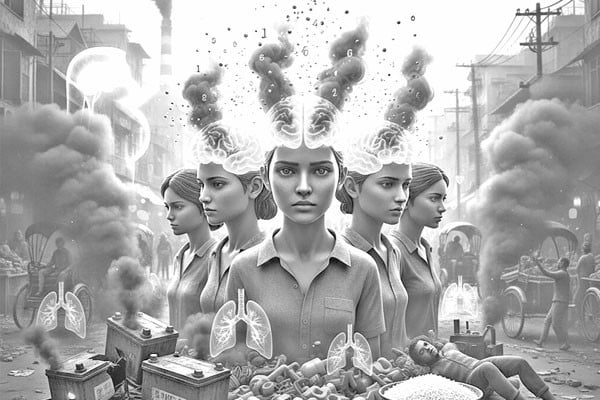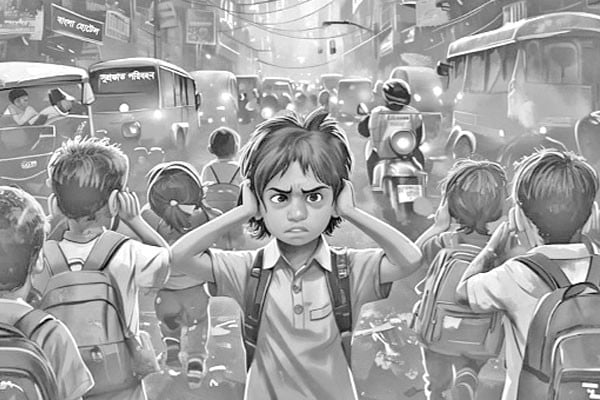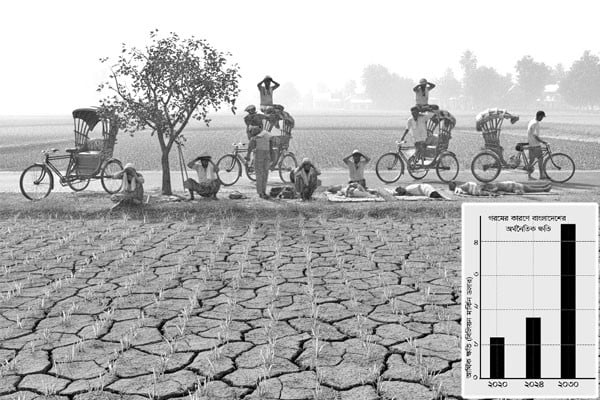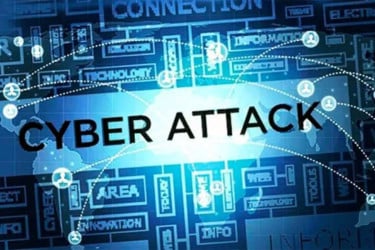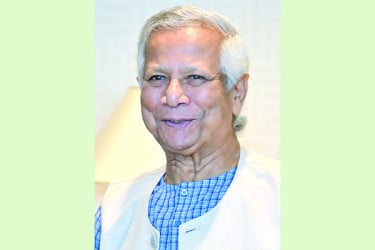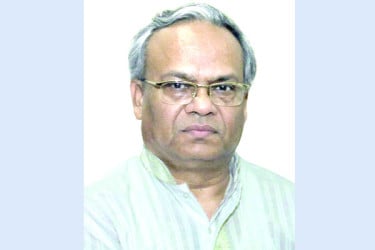আমরা সাধারণত মশাকে বিরক্তিকর ও ক্ষতিকর প্রাণী হিসেবে জানি। কারণ তারা ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়া, ফাইলেরিয়া, জিকা ভাইরাসসহ নানা রোগ ছড়ায়। কিন্তু প্রকৃতির ভারসাম্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, মশারও কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপকারী ভূমিকা রয়েছে। মশা প্রকৃতির খাদ্যশৃঙ্খলের একটি অপরিহার্য অংশ। মশার লার্ভা পানিতে বাস করে এবং মাছ, ব্যাঙাচি, ড্রাগনফ্লাইয়ের লার্ভাসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণীর জন্য প্রধান খাদ্য হিসেবে কাজ করে। আবার প্রাপ্তবয়স্ক মশা পাখি, বাদুড়, মাকড়সা ও ফড়িংয়ের মতো কীটভুক প্রাণীর খাবার। অর্থাৎ, মশা না থাকলে এদের খাদ্যাভাব তৈরি হতো।
অনেকেই জানেন না, স্ত্রী মশা রক্ত খায় ডিমের প্রোটিনের অভাব পূরণের জন্য। রক্ত না খেলে তাদের ডিম ফুটে লার্ভা হবে না। তাই স্ত্রী মশা তাদের পেটে ডিম আসার পর রক্ত পান করে। কিন্তু মশার প্রধান খাদ্য আসলে ফুলের মধু। ফুল থেকে মধু সংগ্রহের সময় তারা এক ফুল থেকে অন্য ফুলে পরাগ ছড়িয়ে দেয়। ফলে কিছু গাছপালা ও বুনো উদ্ভিদের পরাগায়ণে মশার অবদান রয়েছে। অন্যদিকে মশার লার্ভা পানিতে জন্মে এবং শেওলা ও অণুজীব খেয়ে বেড়ে ওঠে। এতে পানির ভিতরে অণুজীবের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং প্রাকৃতিকভাবে পানির ভারসাম্য রক্ষা পায়।
বিশ্বে কিছু প্রজাতির মশা রয়েছে যাদের হাতি মশা বা টক্সোরাইনসাইটিস মশা বলা হয়। এরা একেবারেই মানুষের রক্ত খায় না, বরং ফুলের মধু খেয়ে বেঁচে থাকে। এদের লার্ভা অন্য মশার লার্ভা খেয়ে বেড়ে ওঠে। অর্থাৎ, এই মশাগুলো প্রাকৃতিকভাবে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া বা ম্যালেরিয়ার বাহক মশার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এজন্য একে জৈব নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মানবজাতির জন্য মশা একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ক্ষেত্র। মশার মাধ্যমে ছড়ানো রোগ নিয়ে গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা নতুন ভ্যাকসিন, ওষুধ এবং রোগপ্রতিরোধের কৌশল আবিষ্কার করছেন। এমনকি মশাকে ব্যবহার করে জেনেটিক গবেষণা এবং জীববৈজ্ঞানিক পরীক্ষাও করা হচ্ছে। মশার ক্ষতিকর দিক আমরা সবাই জানি। তবে এটাও সত্য যে, প্রকৃতির প্রতিটি প্রাণীর মতো মশারও একটি পরিবেশগত ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে টক্সোরাইনসাইটিস মশা রোগবাহী মশাকে দমন করতে সাহায্য করে। তাই মশাকে পুরোপুরি ধ্বংস করার চেয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা এবং রোগবাহী প্রজাতিগুলোকে কমানোই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে মানুষ ও পরিবেশ, উভয়ের জন্যই নিরাপদ সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব।
লেখক : পরিবেশ-জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়