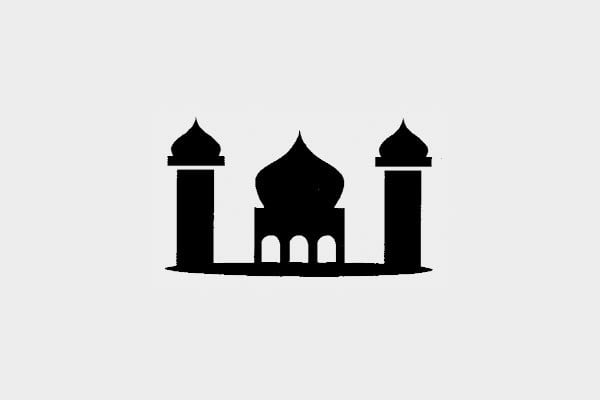চব্বিশের গণ অভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে শুধু একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ফল নয়, বরং এটি ছিল দীর্ঘকাল সমাজে জমে ওঠা বঞ্চনা, বৈষম্য ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এক বিশাল গণজাগরণের বিস্ফোরণ। এই সময় দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ, নগর থেকে গ্রাম পর্যন্ত হাজার হাজার তরুণ-তরুণী, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, পেশাজীবী এবং সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল প্রতিবাদের স্লোগান, চোখমুখে ছিল নিপীড়নের বিরুদ্ধে জেদি প্রত্যয়, আর হৃদয়ে বহমান ছিল একটি ন্যায়ের সমাজের স্বপ্ন- একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক ও মানবিক রাষ্ট্রের আকাঙ্খা।
এই আন্দোলনের মর্মমূলে নিহিত ছিল দুটি শব্দ : ‘বৈষম্যহীন’ ও ‘স্বৈরাচারমুক্ত’। শব্দ দুটি নিছক সেøাগানের শব্দ ছিল না, বরং তার পেছনে ছিল দশকের পর দশক ধরে সঞ্চিত এক নিঃশব্দ আর্তনাদ, যা এ প্রজন্মের মুখে এসে উচ্চারিত হলো বিদ্রোহের ভাষায়। এই দ্বৈত দাবির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে সেই জনমানস, যাদের প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতা হয়ে উঠেছিল বৈষম্যমূলক অর্থনীতি, রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং ন্যায়বিচারহীন রাষ্ট্রব্যবস্থার নির্মমতার শিকার হওয়া। চিন্তাবিদ ফ্রান্ৎস ফ্যাননের ভাষায়, যখন উপনিবেশ বা দমনমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা একটি জনগোষ্ঠীর আশা ও স্বপ্নকে দাবিয়ে রাখে, তখন সেই জনগোষ্ঠী বিদ্রোহকেই জীবনের স্বাভাবিক পথ হিসেবে বেছে নেয়। চব্বিশের বাংলাদেশ যেন সেই ফ্যাননীয় বাস্তবতারই প্রতিফলন।
আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গণ আন্দোলনকে প্রায়ই রাজনৈতিক পুনর্জাগরণের সূচক হিসেবে দেখা হয়। এই প্রেক্ষাপটে চব্বিশের গণ অভ্যুত্থান ছিল একপ্রকার নৈতিক প্রতিরোধ, যা শুধুই ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে ছিল না, বরং তা ছিল একটি নতুন ধরনের সমাজ গঠনের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সমবেত আকাঙ্খা। এ গণ অভ্যুত্থান প্রশ্ন তোলে পূর্ববর্তী শাসকদের বৈধতা নিয়ে, তেমনি নতুন ভবিষ্যতের প্রতি দায়বদ্ধতাও সৃষ্টি করে। এই আন্দোলন তাই শুধু একটি রাজনৈতিক ঘটনাই ছিল না; এটি ছিল একটি সমাজ-সাংস্কৃতিক গতিধারার নতুন বাঁক, যেখানে একটি নতুন প্রজন্ম তার অতীতের সব ব্যর্থতার দায়ভার ঝেড়ে ফেলে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মমর্যাদার দাবিতে আত্মপ্রকাশ করে। এটি ছিল ইতিহাসের সেই ক্ষণ, যখন বহু শোষিত, নিঃস্ব ও অপদস্থ মানুষ একযোগে বলেছিল, ‘আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে’।
বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রথম দৃশ্যমান প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল তরুণ প্রজন্মের হাত ধরে, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ছিলেন এই আন্দোলনের সূচক ও চালিকাশক্তি। বাংলাদেশের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রায়শ ছাত্রসমাজই প্রথম আওয়াজ তোলে। যেমনটি আমরা দেখেছি ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানে, কিংবা ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে। ২০২৪-এর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু এই আন্দোলনের ভিত্তিভূমি ছিল পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় অনেক বেশি জটিল ও বহুমাত্রিক। এটি শুধু ধনী-দরিদ্রের আর্থিক ব্যবধানের প্রশ্ন ছিল না; বরং এর গভীরে ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কাঠামো শক্তির অপব্যবহার ও রাজনৈতিক আনুগত্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বৈষম্য, যা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মানবিক মর্যাদাকে প্রতিনিয়ত আঘাত করছিল।
সরকারি চাকরিতে দলীয়করণ, উচ্চশিক্ষায় রাজনৈতিক আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া, কোটাব্যবস্থার নামে একপক্ষীয় সুবিধাবণ্টন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকারকে অবহেলা করার মাধ্যমে তৈরি হচ্ছিল একটি পক্ষপাতদুষ্ট ও অনৈতিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো। মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকা স্বাভাবিক হলেও, যখন সেই দায়িত্ব কৃতজ্ঞতার গণ্ডি পেরিয়ে একচোখা সুযোগসন্ধানী ব্যবস্থায় পরিণত হয় তখন সেটি বৈষম্যের রূপ পরিগ্রহ করে। আন্দোলনকারীদের মধ্যে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিল : যদি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক সমান মর্যাদার অধিকারী হয়, তবে কেন জন্মপরিচয়, রাজনৈতিক পরিচয় কিংবা সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী তার শিক্ষার অধিকার বা চাকরির সুযোগ নির্ধারিত হবে?
এখানে আমরা জন রলসের ‘ন্যায়বিচারের তত্ত্ব’ (থিওরি অব জাস্টিস)-এর কথা স্মরণ করতে পারি, যেখানে তিনি বলেন, একটি ন্যায্য সমাজ গঠনের জন্য সবচেয়ে দুর্বল এবং সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু তা হতে হবে সর্বজনীন নীতির আলোকে, পক্ষপাতহীনভাবে। চব্বিশের ছাত্ররা যেন রলসের এই নৈতিক দর্শনকেই বাস্তবে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা শুধু নিজেদের স্বার্থে নয়, বরং পুরো সমাজব্যবস্থার ভিতরকার সাংগঠনিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে উৎসারিত এই বিদ্রোহ তাই নিছক রাজনৈতিক নয়; এটি ছিল একধরনের নৈতিক অভ্যুত্থান। এখানে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থের চেয়ে বৃহত্তর সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন প্রাধান্য পেয়েছে। তরুণদের চোখে ধরা পড়েছে, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ছাড়া উন্নয়ন কেবল একটি পরিসংখ্যানগত ছলনা। সেই উপলব্ধি থেকেই তারা নিজেদের ক্লাসরুমের সীমা ছাড়িয়ে রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছিল, মানবিক মর্যাদা, সমতা ও সুবিচারের দাবিতে দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিল, ‘এই বৈষম্য করা চলবে না।’
ছাত্রদের ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করে সরকার যখন কঠোর ও দমনমূলক অবস্থান নেয়, তখন আন্দোলন একটি নতুন মোড় নেয়। এটি হয়ে ওঠে কেবল একটি দাবি-দাওয়ানির্ভর প্রতিবাদ নয়, বরং এক স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণের সুতীব্র প্রতিরোধ। এ আন্দোলনের গন্তব্য ছিল না কেবল আর্থিক বা প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যের অবসান; বরং এর লক্ষ্য ছিল সেই রাষ্ট্রীয় মানসিকতা ও কাঠামোর বিরুদ্ধাচরণ, যেখানে জনতার চেয়ে ক্ষমতাই মুখ্য, যেখানে নাগরিক অধিকার নয়, বরং আনুগত্যই একমাত্র গ্রহণযোগ্যতা। স্বৈরাচার এখানে কোনো ব্যক্তিনির্ভর অভিশাপ নয়, বরং একটি প্রতিষ্ঠানিক রূপান্তর- এক প্রকার শাসনতান্ত্রিক অন্ধকার, যার মূল চিহ্ন হলো ক্ষমতার এককেন্দ্রিকতা, ভিন্নমতের দমন, এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোর স্থলে কর্তৃত্ববাদী নিয়ন্ত্রণ। প্লেটোর ‘দ্য রিপাবলিক’-এ স্বৈরতন্ত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যখন জনগণের নিরাপত্তার নামে একটি শাসক ক্রমশ ক্ষমতা কুক্ষিগত করে, তখন ধীরে ধীরে গণতন্ত্র সরে গিয়ে জন্ম নেয় স্বৈরাচার। চব্বিশের আন্দোলন যেন এই রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে বুঝে নিয়ে তার বিরুদ্ধে সময়োচিত ও নৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেছিল।
তরুণদের প্রতিরোধে ফুটে উঠেছিল প্রতীকী ও সাংস্কৃতিক প্রতিবাদের এক নতুন ভাষা। কখনো তা ছিল দেয়ালে আঁকা ছায়াময় কবিতায়, কখনো তা ছিল হাতে লেখা পোস্টারে, কখনো বা নিঃশব্দ প্ল্যাকার্ডে লেখা একটিমাত্র বাক্যে ধরা পড়ত গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রের গণবিচ্ছিন্ন অপ্রত্যাশিত মূর্তি। এসব অভিব্যক্তি ছিল সরাসরি রাষ্ট্রের ছায়াতলে শাসকশ্রেণির দমননীতি ও গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে এক সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের অস্ত্র। তরুণদের এক একটি প্রশ্ন যেন রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সংকটকে উন্মোচন করছিল: কেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে? কেন সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করতে হয়? কেন মুক্তবুদ্ধির চর্চা রাষ্ট্রের কাছে হুমকি হয়ে দাঁড়ায়? এই প্রশ্নগুলো শুধু প্রশাসনকে নয়, বরং গোটা সমাজকেই আত্মসমালোচনার মুখে দাঁড় করিয়েছিল। আন্দোলনকারীদের অবস্থান ছিল সুস্পষ্ট, তারা কোনো আপসে বিশ্বাস করেনি। ‘স্বৈরাচারকে আর প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না’-এই উচ্চারণ ছিল কেবল একটি স্লোগান নয়, বরং আন্দোলনে নামা নতুন প্রজন্মের নৈতিক শপথ। আমাদের মনে রাখতে হবে, কোনো দেশে শুধু শাসক স্বৈরাচারী হয় না; সমাজও হয় স্বৈরতান্ত্রিক, আর সাধারণ মানুষের চিন্তাও হয়ে ওঠে দাসত্বে অভ্যস্ত। কিন্তু ২০২৪-এর এই প্রজন্ম সেই দাসত্বভীতি থেকে মুক্ত হয়ে স্বৈরাচারী রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। তাদের অনিরুদ্ধ কণ্ঠস্বর ছিল ভবিষ্যতের পক্ষে, ন্যায়বিচারের পক্ষে, এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে এক অনড় প্রতিরোধ।
সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে গিয়ে নবপ্রজন্ম যে আত্মদায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছে, তা নিছক নৈতিক অবস্থান নয় বরং ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে এসে রক্তাক্ত প্রতিরোধের মাধ্যমে তারা ভবিষ্যতের পথচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। চব্বিশের আন্দোলন তাই কেবল একটি রাজনৈতিক মোড় নয়, এটি ছিল এক জনজাগরণ, যা তরুণদের বিবেক ও চেতনার গভীরতম স্তর থেকে উৎসারিত। ‘স্বৈরাচার পতনের এক দফা’ এই উচ্চারণটি ছাত্র-জনতার মুখে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল এক সম্মিলিত সংগ্রামের শপথে। এ ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের আড়ালে বাসা বাঁধা স্বৈরশাসক ও জনগণের মধ্যকার বৈরী সম্পর্কের বিরুদ্ধে একটি মৌলিক প্রতিবাদ, যেখানে তরুণরা কেবল শিকার নয়, হয়ে উঠেছিল পরিবর্তনের কারিগর।
লেখক : ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য