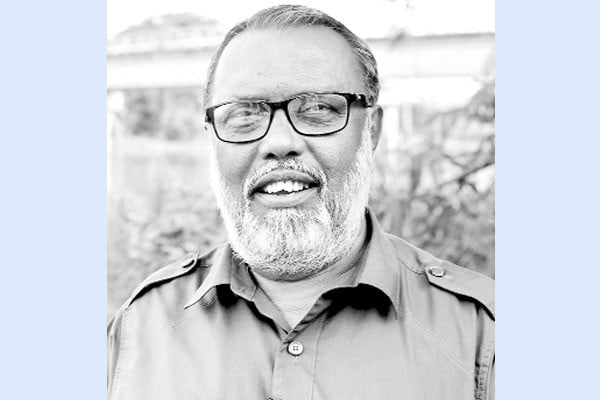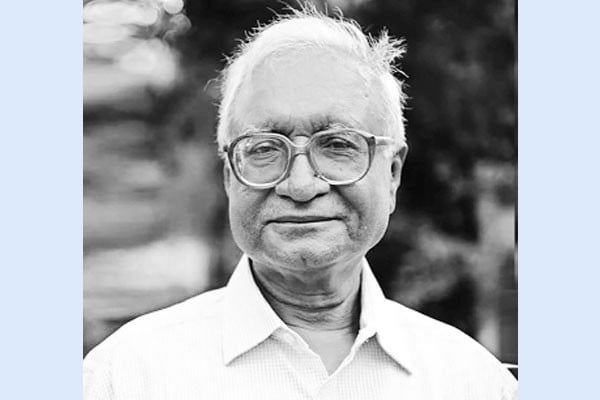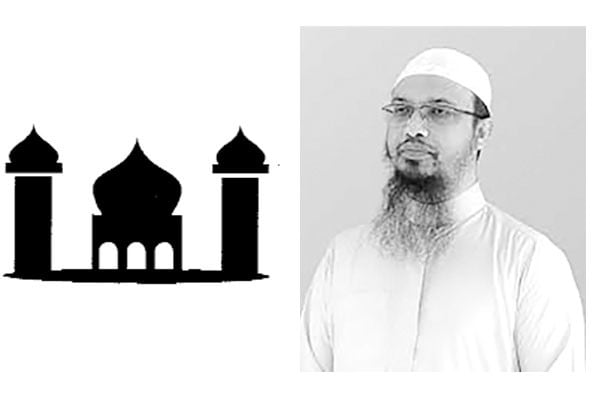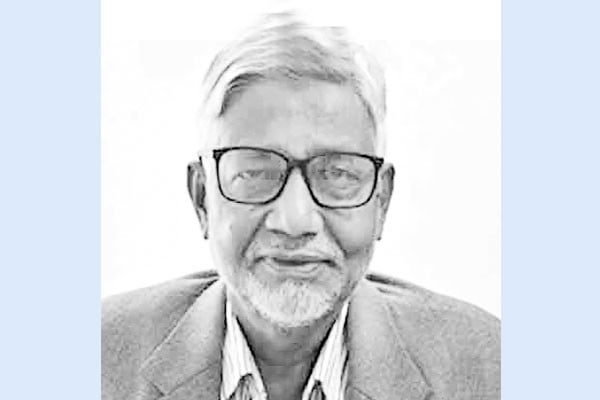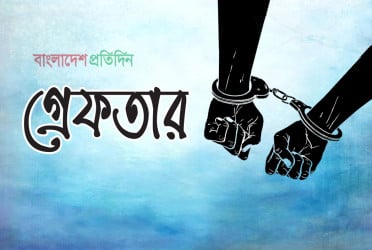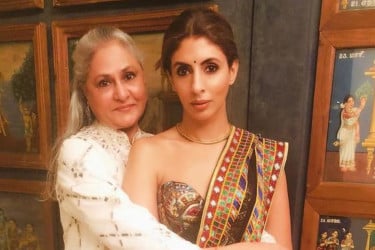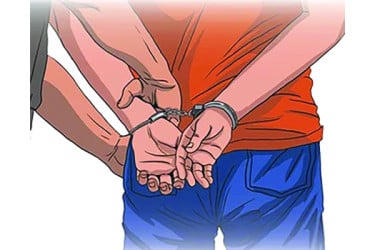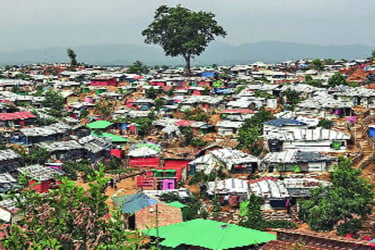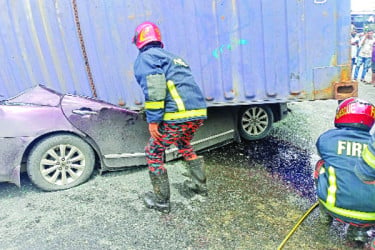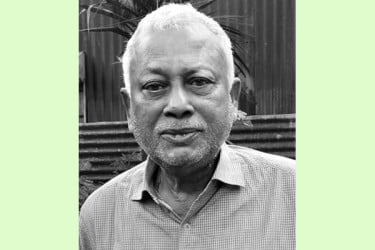রাজধানীর মতিঝিল থেকে মিরপুরে যাব। মেট্রোরেলে উঠেছি। যাত্রীতে ভরপুর সেই বাহনের গতিজনিত দুলুনি সামলানোর জন্য হাতল ধরে থাকার ব্যবস্থা আছে। সেদিন সন্ধ্যায় ওটা ব্যবহার করতে হয়নি। ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে দাঁড়ানো যাত্রীরা আমায় টলতে দিচ্ছিলেন না। চতুর্মুখী চাপ চলছেই। এরই মধ্যে উড়ে এসে কানে ঢুকছে বিশেষজ্ঞদের মতো আওড়ানো বিচিত্র সব কথামালা।
অসহ্য ভিড় যাঁর মেজাজ তিরিক্ষি করে দিয়েছে তিনি মেট্রো কর্তৃপক্ষকে ‘স্ত্রীর বড় ভাইয়ের পুত্র’ বলে অভিহিত করে বলেন, ‘এই ওয়ার্থলেসদের গুলিস্তানের মোড়ে লটকিয়ে রাখা দরকার। এরা এত দিনেও রাতভর ট্রেন চালানোর সিস্টেম চালু করতে পারল না।’ তরুণ এক যাত্রী বলেন, ‘জ্যাঁতা না মরা লটকাতে হবে, তা তো বললেন না আংকল। মিরপুর ১০ নম্বরের গোলচক্কর গুলিস্তান মোড়ের চেয়ে অনেক সুন্দর। লটকিয়ে কোনো জিনিস জনগণকে দেখানোর জন্য ওটাই ফার্স্ট ক্লাস জায়গা। অমন জায়গাকে উপেক্ষা করাটা কি উচিত হলো?’
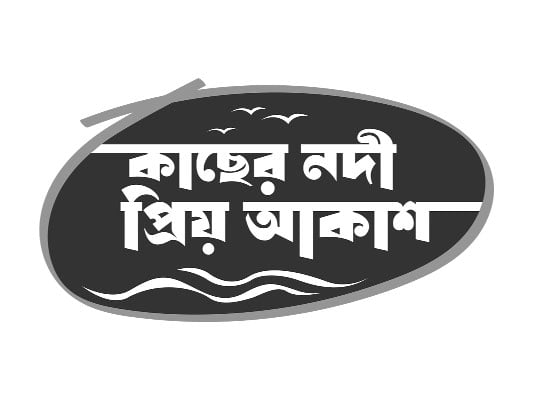 ‘দেখলেন! ফাজিল পোলাপানের কী উৎপাত!’ বলেন, সেই মেট্রো সমালোচক, ‘এদের সামনে ভালো একটা কথা বলতে যাবেন তো এক শটা কথা শুনিয়ে আপনার বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে।’ কথাগুলো তিনি বললেন, আমার চোখে চোখ রেখে। তাঁকে মনে মনে দুটি প্রশ্ন করেছি। এক. মেট্রো কর্তৃপক্ষ যে সম্পর্কে আপনার ‘সুমুন্দির পুত’ সে বিষয়ে কোনো ডকুমেন্ট আছে? দুই. যুবকরা আমার পিতার নাম ভুলিয়ে দিতে পারবে, নিশ্চিত হলেন কীভাবে?
‘দেখলেন! ফাজিল পোলাপানের কী উৎপাত!’ বলেন, সেই মেট্রো সমালোচক, ‘এদের সামনে ভালো একটা কথা বলতে যাবেন তো এক শটা কথা শুনিয়ে আপনার বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে।’ কথাগুলো তিনি বললেন, আমার চোখে চোখ রেখে। তাঁকে মনে মনে দুটি প্রশ্ন করেছি। এক. মেট্রো কর্তৃপক্ষ যে সম্পর্কে আপনার ‘সুমুন্দির পুত’ সে বিষয়ে কোনো ডকুমেন্ট আছে? দুই. যুবকরা আমার পিতার নাম ভুলিয়ে দিতে পারবে, নিশ্চিত হলেন কীভাবে?
ট্রেনে, বাসে বা লঞ্চে ভ্রমণকালে যাত্রীদের কথা শোনার উদ্দেশ্যে কান পেতে রাখা আমার বহু দিনের অভ্যাস। এতে তথ্য পাই; বিনোদনও পাই অনেক। ‘শুনব বেশি/বলব খুব কম’ পন্থা অনুসরণ করি। তাই মেট্রো কর্তৃপক্ষের ‘ফুফা সাহেব’কে এড়ানোর জন্য একটু বাঁদিকের যাত্রী জটলায় ভিড়ে গেলাম। এখানে দেখি লম্বাদেহী দাড়িশোভিত মুখ এক নাগরিক ‘আগুনে পুড়ে ছারখার হওয়া থেকে বাঁচার জন্য লোভ-লালসায় কাতর না হওয়ার’ উপায় বর্ণনা করছেন।
তিনি বলেন, খাই খাই করে জিন্দেগি বরবাদ না করে শক্তিমান যেসব ব্যক্তি জনকল্যাণী কাজে সময় খরচ করেছেন, স্বনামখ্যাত সেই মহানরা মনে রাখতেন, একদিন তো আমায় সাধারণ হয়ে যেতেই হবে। অসাধারণ হওয়ার জন্য ওপরে উঠেছি। উঠতে মই ব্যবহার করেছি, নিচে নামার জন্যও মই লাগবে। ক্ষমতা যাদের অন্ধ করে, তারা ওপরে ওঠামাত্র, মইটায় লাথি মারেন। মাটিতে পড়ে থাকে মই। থাকতে থাকতে পচে যায়। কালক্রমে পরিস্থিতি এমন হয় যে শক্তিমান ব্যক্তিটি নিচে নেমে আসার জন্য মই হাতড়ান। পান না।
কারওয়ান বাজার স্টেশনে নেমে যাওয়ার আগে লম্বাদেহী দাড়িমুখ যাত্রী একটি ফারসি কবিতার কয়েক পঙ্ক্তি শোনালেন। মনোরম আবৃত্তি। আমি তাঁকে কবিতাংশের বাংলা করতে অনুরোধ করলাম। তিনি বলেন, ‘নিশাকালে রাজা আঁকেন লুণ্ঠনের ছক অতি পরিষ্কার/প্রভাতে তার দেহ মাথা মুকুট একেবারে চুরমার।’
ফারসি কবি যে ‘রাজা’র পরিণাম দেখালেন সেইজন প্রতীকী রাজা, ক্ষমতার মাদকতা যাকে বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। তাই, রাজা মনে করেন রোজ কেয়ামত তক তিনি ক্ষমতাভোগ করবেন। নিজের কুকর্ম যে তাকে ক্রমশ রসাতলের দিকে টানছে, তা তিনি টের পান না। হঠাৎ এক সকালে রাজা দেখেন পায়ের নিচে মাটি নেই। প্রকৃতির প্রতিশোধের দুর্বিণীত ছায়া তাকে ঘিরে ফেলেছে। দৃষ্টি যে দিকে যায়, যতদূর যায়, শুধু অন্ধকার।
ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়ি। ঘুম আসে না। লম্বাদেহী দাড়িমুখ নিঃসৃত ‘প্রভাতে দেহ মাখা মুকুট চুরমার’ কথাটি কানে বাজতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে চোখে ভেসে ওঠে প্রকৃতির প্রতিশোধের নানা ঐতিহাসিক ছবি। যিশুকে হত্যা করেছিল জুদার্স এস্করিয়ট। জুলিয়াস সিজার খুন হয়েছেন ব্রুটাসের হাতে। প্রকৃতি এমন বন্দোবস্ত করে যে দুই ঘাতককেই আত্মহত্যা করতে হয়েছিল।
মাহমুদ গজনভির বংশধর সুলতান আবদুর রশিদ গজনভির ছিল বিরাট সেনাবাহিনী। এক বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি সেনাপতি তুগরালকে পাঠালেন। দমন অভিযান সফল হলো। তুগরাল এবার লক্ষ্যমাত্রা করলেন তার মনিবকে। বাহিনী নিয়ে রাজধানীতে ঢুকে তিনি হত্যা করলেন সুলতানকে। খতম করে ফেললেন সুলতানের পরিবারের ৯ জনকে। জোর করে বিয়ে করলেন সুলতানের এক মেয়েকে। ঘোষণা করলেন ‘নওরোজ’ (নববর্ষের প্রথম দিন)-এ আমার অভিষেক হবে। কিন্তু ঘোষণার ৪০ দিনের মধ্যেই সুলতানপন্থি সেনা অভ্যুত্থানে প্রাণ যায় তুগরালের। সিংহাসনের নিচে পড়ে থাকে তার লাশ। কেউ সরনোরও প্রয়োজন বোধ করেননি। অবহেলায় লাশটি পচে গিয়েছিল।
মোঙ্গল রাজ্যাধিপতি হালাকু খান (১২১৭-১২৬৫) নিষ্ঠুরতার জন্য বিশ্বময় কুখ্যাত। তার ভয়ংকর অভিযানের কারণে আব্বাসীয় খেলাফতের অবসান ঘটে। হালাকুর বাহিনী ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ নগরী দখলের পরই খলিফা আল মুস্তাসিমকে উৎখাত করে। হালাকুর নির্দেশে খলিফার দুই ছেলেকে বন্দি করে তরবারির কোপে তাদের মাথা ধড় থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছিল। খলিফার সামনেই বাগদাদ নগরী পোড়ানো ও লুণ্ঠনের উৎসব চালায় মোঙ্গল সেনাদল। নগরীর ৬ লাখ বাসিন্দাকে হত্যা করেন হালাকু খান। সেকালে বাগদাদ ছিল জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলনের প্রাণকেন্দ্র; নগরীর লাইব্রেরিতে ছিল ১০ লাখেরও বেশি বই। হালাকু বাহিনী সেই লাইব্রেরি পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। এই বর্বরতার প্রতিশোধ নেয় প্রকৃতি। হালাকুর হাতেই অস্তমিত হয়েছে মোঙ্গল শক্তিসূর্য। মিসর ও তুরস্কের সম্মিলিত বাহিনীর ধাওয়া খেয়ে পলায়নপর হালাকু বাহিনী একসময় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বন্দি হওয়ার পর নরপিশাচ হালাকুর দেহের নানা জায়গায় বাটালি ঠেকিয়ে হাতুড়ি মারা শুরু হয়, হালাকুর প্রাণবায়ু বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বাটালি-হাতুড়ি সক্রিয় থেকেছে।
ইরাকের বাদশাহ ফয়সল (বয়স ২৩) ১৯৫৮ সালের ১৪ জুলাই রক্তক্ষয়ী সেনা অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারান। অভ্যুত্থানের নেতা জেনারেল করিম কাসেমের নির্দেশে বাদশাহ ফয়সল ও প্রধানমন্ত্রী নূরী আস সাঈদ এবং শাহি পরিবারের সব সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। জনগণের দেখার সুবিধার্থে বাদশাহ ও প্রধানমন্ত্রীর মৃতদেহ বেশ কয়েক দিন রাজধানী বাগদাদের প্রধান সড়কের পাশে রাখা হয়েছিল। এ ধরনের নির্দয় আচরণ জনগণ পছন্দ করেনি। তারা ক্ষমতা দখলকারী সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে মিছিল করার সাহস পায়নি। মনে মনে নবাগতদের শাসনাবসান চেয়েছে। তাদের কাক্সিক্ষত সময়ের অনেক আগেই ১৯৬৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কর্নেল আবদুস সালাম আরিফের নেতৃত্বে সেনা অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারান। প্রাণও যায় তার। ফয়সল ও নূরীর মৃতদেহ জনগণকে দেখানোর জন্য যেভাবে শুইয়ে রাখা হয়েছিল, সেই একই কায়দায় করা হয় জেনারেল কাসেমের মৃতদেহ প্রদর্শনী।
‘দুনিয়ার বুকে মুসলমান আর খ্রিস্টানদের চিহ্নও রাখব না’- সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ। দুই সম্প্রদায়কে হাওয়া করে দেওয়ার জন্য বিস্তর ছক এঁকে সেগুলো একের পর এক কার্যকর করছিলেন তিনি। তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য অভিযানে নামেন খ্রিস্টান রাজা হেরাক্লিয়াস। এক যুদ্ধে তিনি পারস্য বাহিনীকে হারিয়ে দেন এবং খসরু পারভেজকে বন্দি করেন। বন্দি খসরুকে শুকনো রুটি আর পানি খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়। চোখের সামনে তাঁর ছেলেদের একজন একজন করে প্রাণ বধ করা হয়েছিল। শিরোইয়াস নামে খসরুর এক ছেলেকে বলা হয়, ‘তোর বাপের গলা কেটে ফেল।’ গলা কেটে বাপ হত্যায় সে বাধ্য হয়। শিরোইয়াসের গোটা শরীর ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছিল গুটি বসন্ত রোগে। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে দুনিয়া ছেড়েছিলেন শিরোইয়াস।
ভারত শাসক সুলতান জালালুদ্দিন ফিরোজ খিলজি তার ভাইপো আলাউদ্দিনকে নিজের ছেলের চেয়েও বেশি স্নেহ করতেন। তাকে দিয়েছিলেন গুরুত্বপূর্ণ পদ। বিনিময়ে চাচাকে তিনি ক্ষমতাচ্যুত করে ‘সম্রাট’ হওয়ার ফন্দিতে মেতে ওঠেন। এক অনুষ্ঠানে চাচা-ভাতিজা কোলাকুলি করছিলেন। এ সময় ভাতিজার নিযুক্ত ঘাতক মাহমুদ বিন সেলিম আমূল ছোরা ঢুকিয়ে দেন প্রজাবৎসল দয়ার্দ্রচিত্ত সুলতানের পাঁজরে। ঘটনাস্থলেই মারা গেলেন জালালুদ্দিন খিলজি। মারা যাওয়ার সময় তিনি বিড়বিড় করে বলেন, ‘তোরে অন্ধ হয়ে সব স্নেহ উজাড় করে দেওয়ার পুরস্কার তুই এভাবে দিলি!’
প্রকৃতি তখন হয়তো হাসছিল। কেননা পরে দেখা যায়, আলাউদ্দিনের ভাড়া করা খুনি মাহমুদ বিন সেলিমের কুষ্ঠ হয়েছে। ওই রোগেই তার মৃত্যু ঘটে। মাহমুদকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন জালালুদ্দিনের এক আত্মীয় ইখতিয়ারুদ্দিন। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে আবোল-তাবোল বলতে বলতে দিল্লির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছেন ইখতিয়ার। এদিকে জালালুদ্দিন হত্যার সুবিধাভোগী আলাউদ্দিন খিলজি সিংহাসনে বসে ‘সন্দেহ রোগে’ ভুগতে থাকেন। কেবলই তার মনে হয়, তাকে খুন করার পাঁয়তারা চলছে। নিজেকে নিরাপদ করার প্রক্রিয়ায় তিনি এক এক করে তার ঘনিষ্ঠ দোস্তদের সবাইকে হত্যা করেন। নিজের ছেলেদের তিনি কারাগারে নিক্ষেপ করেন। মানসিক বিকারগ্রস্ততা তাকে ভীষণ একা করে ফেলেছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অস্থিরতা-উৎকণ্ঠায় থেকেছেন আলাউদ্দিন খিলজি।
রোম যখন আগুনে পুড়ছিল সে সময় তা নির্বাপণে মনোযোগী হওয়ার বদলে বংশীবাদনে মগ্ন থাকায় যুগ যুগ ধরে ‘নিষ্ঠুরতার দানব’ নামে চিহ্নিত সম্রাট নিরোর মা এগ্রিপিনা কী করলেন? বিষমিশ্রিত মাশরুম খাইয়ে স্বামী সম্রাট ক্লদিয়াসকে মেরে ফেললেন। স্বামীকে মেরে তিনি সম্রাটের ক্ষমতা হাতে নিতে সচেষ্ট হওয়ায় তার ওপর ক্ষিপ্ত হন নিজের ছেলে। ছেলের হাতেই খুন হয়েছেন এগ্রিপিনা।
বিশ্বাসঘাতক প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলী খানের চক্রান্তে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হন বাংলা বিহার ওড়িশ্যার নবাব সিরাজদ্দৌলা। মীর জাফরের ছেলে মিরনের নির্দেশে খুন করা হয় নবাবকে। মেঘমুক্ত আকাশ থেকে নেমে আসা বজ্রপাতে মারা গিয়েছিলেন মিরন। অনন্তকাল ক্ষমতায় থাকার লালসায় যারা নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন, তাদের সবাই অপঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন।
সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নও চিরকাল ক্ষমতায় থাকার স্বপ্ন দেখতেন। একবার ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ফ্রান্স থেকে পালিয়ে তিনি ইংল্যান্ডে আশ্রয় নেন। ওই সময় আইরিশ লেখক-সাংবাদিক সুন্দরী মার্গারিটা গার্ডিনারের সঙ্গে সখ্য হয়। ‘কাউন্টেস’ পদবিধারী মার্গারিটা নানাভাবে সহায়তা করেন নেপোলিয়নকে। কালক্রমে আবার ক্ষমতাসীন হন তৃতীয় নেপোলিয়ন। এর কিছুকাল পর কয়েক সপ্তাহের ভ্রমণে প্যারিসে এলেন মার্গারিটা। তাকে সৌজন্যবশত রাজপ্রাসাদে ডাকলেনও না সম্রাট। এতে দুঃখ পান তিনি। কয়েক দিন পর প্যারিসের এক অনুষ্ঠানে মার্গারিটাকে দেখতে পেয়ে তার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তৃতীয় নেপোলিয়ন বলেন, ‘আপনি এখানে অনেক দিন থাকতে এলেন?’ মার্গারিটা বলেন, ‘না। আপনি কি মনে করেন আপনি ফ্রান্সে বেশি দিন থাকবেন?’
বছর না পেরোতেই জার্মানির অটোভন বিসমার্কের নেতৃত্বাধীন বাহিনী প্যারিসে ঢুকে সিংহাসন উল্টে দেয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন আবার আশ্রয় নেন ইংল্যান্ডে। সেখানেই ১৮৯৮ সালের ৩০ জুলাই ৮৩ বছর বয়সে ঘটল তৃতীয় নেপোলিয়নের জীবনাবসান।
♦ লেখক : সাংবাদিক