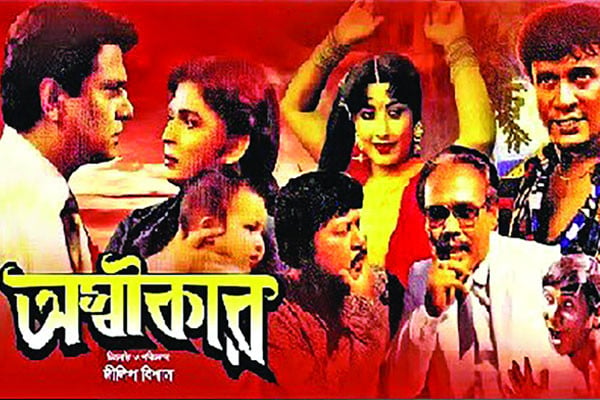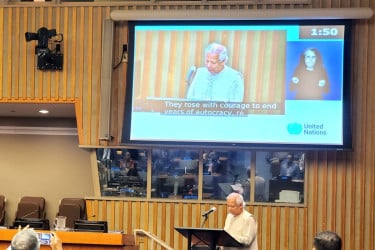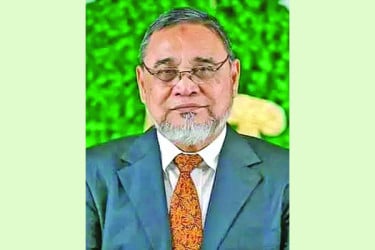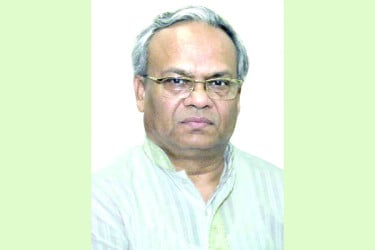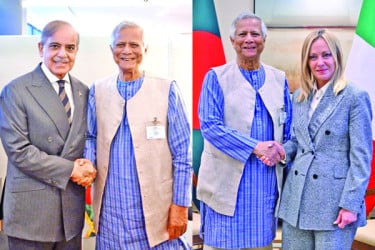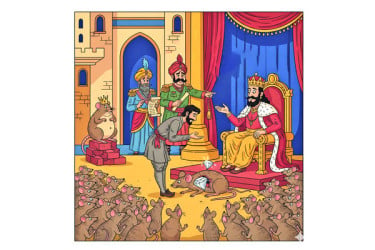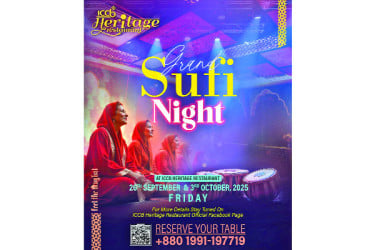বাংলাদেশের সংগীতশিল্পীরা কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। অধিকাংশই কাজহীন, আয়হীন, আর্থিক অনিরাপত্তায় দিন কাটাচ্ছেন- হোক তিনি কোনো সংগীতশিল্পী বা মিউজিশিয়ান। ডিজিটাল যুগে শ্রোতাদের কাছে গান পৌঁছালেও শিল্পীদের হাতে পৌঁছায় না ন্যায্য রয়্যালটি। ক্যাসেট-ফিতা ও সিডির যুগ শেষে অ্যালবামের জগৎটাও সংকুচিত আজ। তেমন করে শিল্পীরা প্রকাশ করছেন না একক গান। স্পন্সরের অভাবে শিল্পীরা গান প্রকাশ থেকে রয়েছেন দূরে। দেশের নামকরা সব অডিও প্রতিষ্ঠান অধিক লাভের আশায় ঝুঁকছে নাটক প্রযোজনায়। কারণ নাটকের সঙ্গে বাড়তি পাওনা তারকাবহুল গান-এক ঢিলে দুই পাখি। যত ভিউ বেশি তত আয়। কেউ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে মরিয়া নয়; দেশের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে নেই কারও কোনো চিন্তা। সবাই কেবল নিজের আখের গোছাতেই ব্যস্ত এখন। আগের মতো ফিজিক্যাল অ্যালবাম বিক্রির হার না থাকায় এবং মোবাইল ফোনে গান শোনার প্রবণতা বাড়ায় পাইরেসি ও কপিরাইট সমস্যা শিল্পীদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে। গুটিকয় বড় করপোরেশন পুরো সংগীত বাজার নিয়ন্ত্রণ করার ফলে নতুন ও স্বাধীন শিল্পীদের জন্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সংকুচিত হচ্ছে। সিনেমা তেমন করে নেই; তাই শিল্পীদের প্লেব্যাকেও ব্যস্ততা কম। দেশের এখনকার সার্বিক পরিস্থিতিতে দেশ-বিদেশে স্টেজ শোও কম শিল্পীদের। নতুন গানের রেকর্ড নিয়েও তেমন করে ব্যস্ততা নেই। ফলে মিউজিকের সঙ্গে জড়িত থাকা শিল্পী, যন্ত্র সংগীতশিল্পীসহ স্টুডিওর কর্মরত মানুষেরা বেকার হয়ে পড়েছেন। জুলাই পরবর্তীতে শিল্পীরাও পড়েছেন অস্তিত্ব সংকটে। যে যেভাবে পারছেন, নতুন করে গান নিয়ে ভাবছেন, করছেন। অন্যদিকে ডিজিটাল মিডিয়া তথা ইউটিউব, অ্যাপ, টিকটক আর স্পটিফাইয়ের যুগে শিল্পীরা ঘরোয়াভাবে গান তৈরি করে নিজেদের চ্যানেলে ছাড়ছেন। কোনোভাবে টিকে আছেন কিছু শিল্পী। দেশের রিয়্যালিটি শোও কম হচ্ছে। তেমন করে নেই নতুন মৌলিক গান। নতুন ধারার প্রযুক্তি, যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের ধীরগতিতে বৃদ্ধি, শিল্পীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর চাপ এবং সামগ্রিকভাবে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সংকুচিত অবস্থা। এই সংকটগুলো শিল্পীদের রোজগার, নতুন প্রতিভাদের সুযোগ তৈরি এবং সংগীতশিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে বড় প্রভাব ফেলছে। সব মিলিয়ে শত শত শিল্পী আজ সংগীত জগৎ থেকে ছিটকে পড়েছেন। এমনিতেই বাংলাদেশে সংগীতশিল্পীদের জন্য কোনো নির্ভরযোগ্য পেশাগত কাঠামো নেই, নেই সংগঠনভিত্তিক সুরক্ষা, নেই রয়্যালটির নিশ্চয়তা। ডিজিটাল যুগের দাপটে ও বাজারের বাণিজ্যিকতার চাপে সংগীতশিল্প আজ এক কঠিন সংকটে। দেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক অঙ্গন সংকুচিত হয়ে যাওয়ায়, সংগীতশিল্পের মতো মাধ্যমগুলোও টিকে থাকার লড়াই করছে। মোটকথা, সংকটে রয়েছে গোটা সংগীত ইন্ডাস্ট্রি। ইন্ডাস্ট্রিতে চলছে অসুস্থ প্রতিযোগিতা। ‘যত ভিউ, তত বাণিজ্য’- এটিই যেন এখনকার সময়ে টিকে থাকার মূলমন্ত্র। এখন শিল্পীর যোগ্যতার মানদণ্ড বিচার হচ্ছে সামাজিক মাধ্যম আর ইউটিউবে তার গানের ভিউ লাখ না কোটি। যেখানে জনপ্রিয়তা আর যোগ্যতার মাপকাঠি কেবল ভিউ। এটাই কি আসলে হওয়া উচিত? একটা সময় ক্যাসেট বা সিডি বিক্রির হিসাবে শিল্পীর জনপ্রিয়তা বিচার করতেন সংগীতপ্রেমীরা। যত বেশি বিক্রি, তত বেশি টিআরপি। প্রতিষ্ঠানগুলো এ ধরনের শিল্পীকে যথাযোগ্য সম্মান দিত। তার সম্মানি হু হু করে বাড়ত। ঘুরে যেত শিল্পীর ভাগ্য। সেই জায়গা দখল করেছে এখন ভিউ।
বাংলাদেশে অধিকাংশ সংগীতশিল্পী ‘ফ্রিল্যান্সার’ হিসেবে কাজ করেন। অর্থাৎ তারা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বেতনভুক্ত কর্মী নন। তারা স্টেজ শো, কনসার্ট, অ্যালবাম বা ইউটিউব কনটেন্ট থেকে আয় করেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এসব উৎস থেকে খুবই সীমিত পরিমাণ আয় হয়, তাও নির্ভর করে জনপ্রিয়তা ও চ্যানেলের মনিটাইজেশন ব্যবস্থার ওপর। উল্লেখ সংখ্যক শিল্পী স্টেজ শো বা ব্যান্ড পারফরম্যান্সের মাধ্যমে আয় করছেন। কিন্তু করোনা মহামারি, এরপর জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান- সব মিলিয়ে স্টেজ শোগুলো বড় ধাক্কা খায়, যার থেকে এখনো পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। অনেক শিল্পী তখন পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। অনেক সময় শিল্পীর গান অন্য কেউ নিজের নামে আপলোড করে, শিল্পী না পারেন আইনি ব্যবস্থা নিতে, না পারেন ভিডিও নামাতে। কপিরাইট ব্যবস্থার দুর্বলতা এখানে বড় প্রতিবন্ধক। এদিকে দেশে অনেক প্রতিশ্রুতিশীল গায়ক থাকলেও খুব কম গানই কালজয়ী হয়, মানুষের মুখে মুখে ফেরে। কারণ দেশের গানগুলো নিয়ে খুব বেশি গবেষণা হয় না। এদের নিয়ে ভাবার লোকগুলো খুব কম এ দেশে। এজন্য এত এত প্রতিশ্রুতিশীল গীতিকার, সুরকার, গায়ক, মিউজিক ব্র্যান্ড থাকার পরও গানে বৈচিত্র্য কিন্তু খুব একটা দেখা যায় না।
অভিনয়শিল্পীদের জন্য গঠনমূলক কিছু সংগঠন রয়েছে, যেখানে সদস্যরা প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা পান। কিন্তু সংগীতশিল্পীদের জন্য এ ধরনের সংগঠন কার্যকর নয়। কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে শিল্পীরা সরকারি সহায়তা পান না। পেশাগত নিরাপত্তাহীনতার কারণে তরুণরাও সংগীতকে পূর্ণাঙ্গ ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে ভয় পান। দীর্ঘমেয়াদে কোনো স্থায়ী সমাধান বা শিল্পীবান্ধব নীতিমালা গৃহীত হয়নি এখনো।
বর্তমানে গান নির্মাণের ক্ষেত্রে মানের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ভাইরাল হওয়া, ট্রেন্ডিং টিকটক বিট, কিংবা সস্তা কথা। এতে হারিয়ে যাচ্ছে লোকগান, আধুনিক গান এবং ক্ল্যাসিকাল সংগীতের চর্চা। প্রতিভাবান নবীন শিল্পীরা উঠে আসার সুযোগ পাচ্ছেন না। বড় ব্যানার বা স্পন্সরের অভাবে তারা পিছিয়ে পড়ছেন। অন্যদিকে যেসব নবীন শিল্পী সত্যিকার অর্থে প্রতিভাবান, তারা কাক্সিক্ষত প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছেন না। এদিকে বাংলাদেশে কপিরাইট আইন থাকলেও এর বাস্তব প্রয়োগ অত্যন্ত দুর্বল। অনেক সময় গানের সুর বা কথা চুরি হয়, অথচ মূল শিল্পী বা সুরকার কিছুই করতে পারেন না। আবার অনেক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম রয়্যালটির কোনো হিসাব দেয় না।
সংগীত কেবল একটি শিল্প নয়, এটি একটি সমাজের আবেগ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বাহক। সংগীতশিল্পীদের অবহেলিত রেখে একটি জাতি কখনোই তার সাংস্কৃতিক ভিত্তি মজবুত করতে পারে না। সময় এসেছে, শিল্পীদের শুধু হাততালি নয়, তাদের জীবনমান ও প্রাপ্য মর্যাদাও নিশ্চিত করতে হবে।

টিকে থাকার লড়াই করছেন শিল্পীরা
নকীব খান
দেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক অঙ্গন সংকুচিত হয়ে যাওয়ায়, সংগীত শিল্পের মতো মাধ্যমগুলোও টিকে থাকার লড়াই করছে। ফলে শিল্পীরাও টিকে থাকার চেষ্টা করছেন। সব মিলিয়ে সংকটে রয়েছে পুরো সংগীত ইন্ডাস্ট্রি। একসময় আয়ের ক্ষেত্রে অ্যালবাম যথেষ্ট ভূমিকা রাখত না, এখনো রাখে না। নরমালি কনসার্ট বা অন্য মাধ্যম থেকেই শিল্পীরা আয় করে থাকেন। সেটা এখন সংকুচিত হয়ে গেছে।

গানের রয়্যালটির সুব্যবস্থা নেই
সাবিনা ইয়াসমিন
অন্যান্য দেশে থাকলেও আমাদের এখানে গানের রয়্যালটির সুব্যবস্থা নেই। সরকার এদিকে সুদৃষ্টি না দিলে ঠিক হবে না। আবদুল আলীম, আবদুর রহমান বয়াতি থেকে বহু শিল্পীর পরিবার রয়্যালটি পেলে অনেক ভালো থাকতেন। যদি এই সিস্টেমটা ঠিক হতো, তাহলে শিল্পীরা ও তাঁদের পরিবার ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারতেন।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সময়ের দাবি
বেবী নাজনীন
দেশের সামগ্রিক অবস্থার মতো সাংস্কৃতিক অঙ্গনও দিনে দিনে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি নেই, সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি নেই। সংস্কৃতির প্রধান এই দুটি মাধ্যম বিলুপ্তির পথে। এ অবস্থায় নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা কতটা সুযোগ পাবে, তা ভেবে দেখার বিষয়। আর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এ সেক্টরের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বেসরকারি বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে। তাই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এখন সময়ের দাবি। কিছু মাধ্যমে অনুদান থাকলেও তা যথেষ্ট নয়।