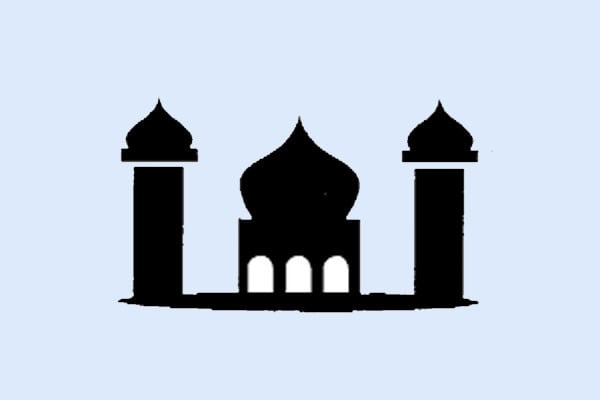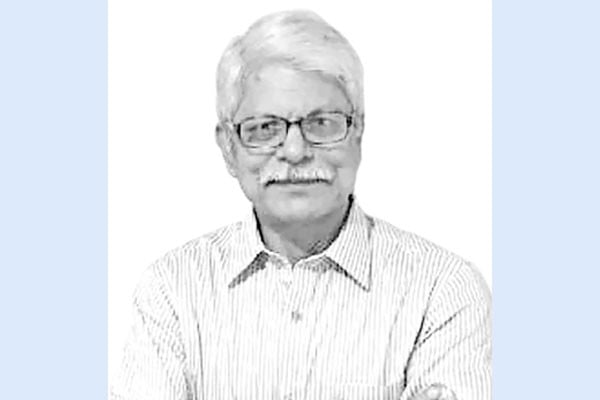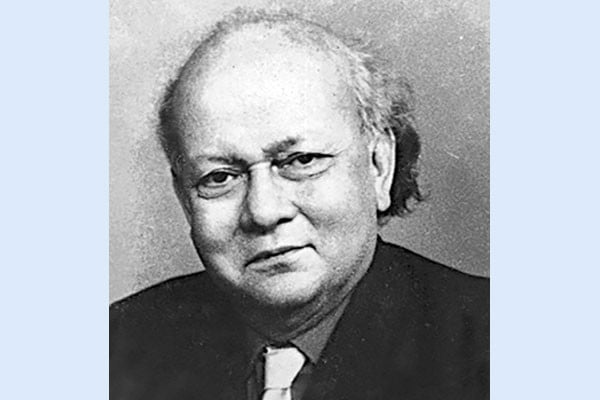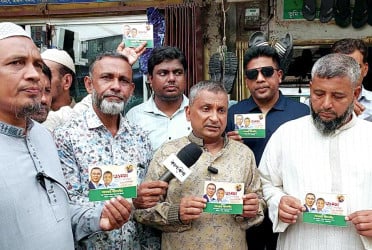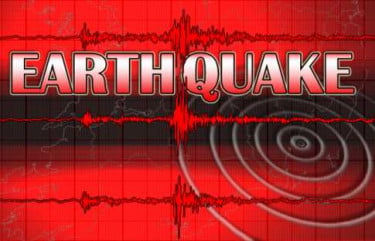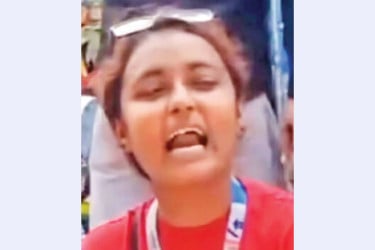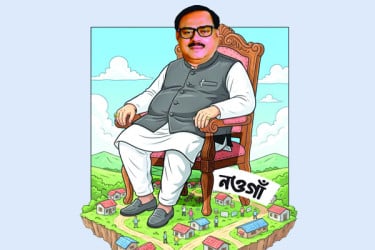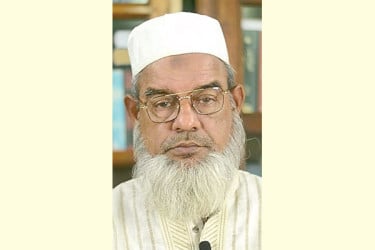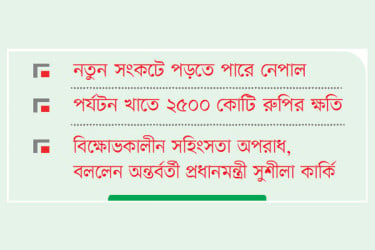বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মুসলিম জন-অধ্যুষিত দেশ, যেখানে অধিকাংশই ধর্মপ্রাণ মুসলমান। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে, যা জনগণের জীবনযাত্রা ও আর্থিক অভ্যাসে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে শরিয়াহ সম্পর্কে সচেতনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শরিয়াহসম্মত আর্থিক পণ্যের প্রতি সংবেদনশীল মুসলমানদের চাহিদা বেড়েছে। বর্তমানে অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ইসলামি ব্যাংকিংকে প্রাধান্য দেয়, কারণ এটি সুদভিত্তিক লেনদেন (রিবা) পরিহার করে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ ছাড়াও ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা এবং ঝুঁকি ভাগাভাগির কারণে ইসলামি অর্থায়ন নীতিগতভাবে অনেক বেশি ন্যায্য ও গ্রহণযোগ্য, যা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের পাশাপাশি ইসলামি নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর্থিক সমাধান খোঁজা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কাছেও জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।
ধর্মীয় কারণ ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ বাংলাদেশে ইসলামি অর্থায়নের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ধর্মীয় কারণে প্রচলিত ব্যাংকিংব্যবস্থা এড়িয়ে চলতে চান এমন ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এসএমই) আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সম্পদভিত্তিক বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি ভাগাভাগির নীতির কারণে অর্থনৈতিক সংকটের সময়ও ইসলামি অর্থায়নব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকে, যা গ্রাহকদের আস্থা বৃদ্ধি করছে। বাংলাদেশ সরকার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো, বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংক, ইসলামি ব্যাংকিং ও সুকুক (ইসলামি বন্ড) ব্যবস্থাকে সমর্থন করছে, যা এ খাতের অগ্রগতিতে সহায়তা করছে। পাশাপাশি হালাল অর্থনীতি, ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ এবং শরিয়াহসম্মত বিনিয়োগের প্রসার বাংলাদেশে ইসলামি অর্থায়নের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করেছে।
বাংলাদেশে ইসলামি অর্থনীতি প্রচলিত ব্যাংকিংব্যবস্থার একটি বিকল্প হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ১৯৮৩ সালে ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (আইবিবিএল) প্রতিষ্ঠার পর, বহু ব্যবসায়ী ও সমাজচিন্তাবিদ ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর ধারাবাহিকতায় বর্তমানে দশটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি ব্যাংক এবং চারটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই) বাংলাদেশে ইসলামি অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর পণ্য ও সেবা ইসলামি অর্থায়নের বিভিন্ন পদ্ধতির অধীনে কাঠামোবদ্ধ, যা সমানুপাতিক ঝুঁকি ও মালিকানা, সম্পদের যথাযথ দখল নিশ্চিতকরণ এবং মুনাফা-ক্ষতির অংশীদারির নীতির অনুসরণ নিশ্চিত করে। ইসলামিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে যারা অর্থায়ন গ্রহণ করেন তারা মূলত বিভিন্ন শরিয়াহসম্মত উৎস থেকে সংগৃহীত তহবিলের ব্যবহারকারী। ইসলামিক অর্থায়ন পদ্ধতিগুলো তিনটি মৌলিক শ্রেণিতে বিভক্ত : ক্রয়বিক্রয়ভিত্তিক অর্থায়ন (বাই মুরাবাহা, বাই মুআজ্জাল, বাই সালাম, ইস্তিসনা ইত্যাদি); লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগিভিত্তিক অর্থায়ন (মুদারাবা, মুশারাকা ইত্যাদি); এবং ইজারাভিত্তিক অর্থায়ন (ইজারা, ইজারা মুনতাহিয়া বিত্তামলিক ইত্যাদি)। ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী চুক্তির মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো পারস্পারিক সম্মতি, সম্পদের মালিকানা, দখল ও ঝুঁকি গ্রহণ। বিক্রেতার অবশ্যই বিক্রির আগে সম্পদের মালিকানা থাকতে হবে। সুতরাং মুরাবাহা বা ইজারা পদ্ধতিতে বিক্রেতা বা লিজদাতা সম্পদটি বিক্রি বা ভাড়ায় দেওয়ার আগে মালিকানা গ্রহণ করতে হবে। বিক্রেতাকে অবশ্যই সম্পদটি প্রকৃতভাবে বা ধারণাগতভাবে নিজের দখলে রাখতে হবে, তারপর তা ক্রেতার কাছে বিক্রি করতে হবে। দখল বলতে ঝুঁকি ও মালিকানার অধিকার বোঝানো হয়। ইসলামিক অর্থায়নে ঝুঁকি ও লাভ একসঙ্গে সংযুক্ত থাকে। যদি সম্পদ বিক্রেতার দখলে না থাকে তবে তিনি সেটি বিক্রি বা ভাড়া দিতে পারবেন না। কারণ তিনি তখন সেই সম্পদের ঝুঁকির মালিক নন। এতে অন্যায়ভাবে ঝুঁকিহীন সুদযুক্ত আর্থিক বৃদ্ধির সুযোগ থাকে না। ইসলামি ব্যাংকিংয়ের বিভিন্ন অর্থায়ন ও বিনিয়োগ পদ্ধতির মধ্যে মুদারাবা আমানত এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে আমানতকারীরা রব-আল-মাল বা বিনিয়োগকারী হিসেবে কাজ করেন আর ব্যাংক মুদারিব বা উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের অর্থকে হালাল ব্যবসায় পরিচালনা করে। ইজারা একটি ইসলামিক ভাড়াচুক্তি, যেখানে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান (ভাড়াদাতা) একটি সম্পদ ক্রয় করে এবং তা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রাহকের (ভাড়াটে) কাছে লিজ প্রদান করে। সম্পদের মালিকানা অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কাছেই থাকে। সম্পদের ক্ষতি বা ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে মালিকের ওপর বর্তায় এবং ঝুঁকি হ্রাসকরণসংক্রান্ত ব্যয়ও মালিককেই বহন করতে হয়। ইজারা চুক্তিতে সম্পদের মালিকানা পুরো ইজারার মেয়াদজুড়ে লিজদাতার (অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের) কাছেই থাকে, তবে গ্রাহক তার উপযোগিতা উপভোগ করতে পারেন। ফলে সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সম্পূর্ণরূপে লিজদাতাকে বহন করতে হয়, যাতে লিজগ্রহীতা (ভাড়াটে) নির্দ্বিধায় সম্পদটি ব্যবহার করতে পারেন। একইভাবে সম্পদের বিমাসংক্রান্ত ব্যয়ও লিজদাতার দায়িত্ব। যদি কোনো কারণে সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং লিজগ্রহীতা সেটি ব্যবহার করতে অক্ষম হন, তবে লিজদাতা (অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান) সম্পদ প্রতিস্থাপন না করা পর্যন্ত কোনো ভাড়া আদায়ের অধিকার রাখেন না। ইজারা চুক্তির আওতায়, সম্পদ ব্যবহারের আগে কোনো ভাড়া প্রযোজ্য নয়, অর্থাৎ সম্পদ যখন ব্যবহারযোগ্য হবে তখন থেকেই ভাড়ার হিসাব শুরু হবে।
লেখক : হেড অব ইসলামিক ফাইন্যান্স, আইডিএলসি