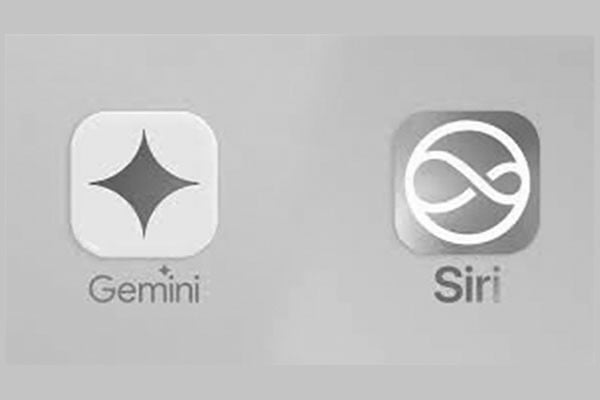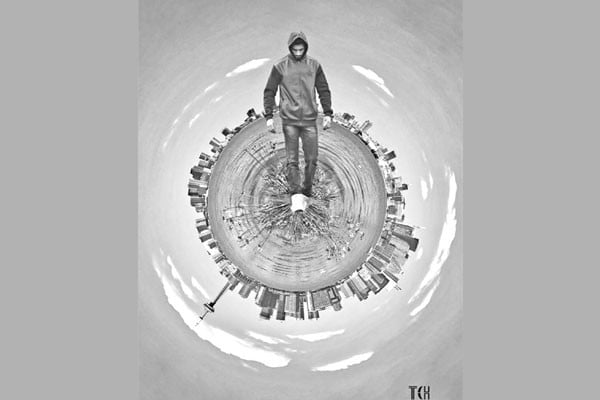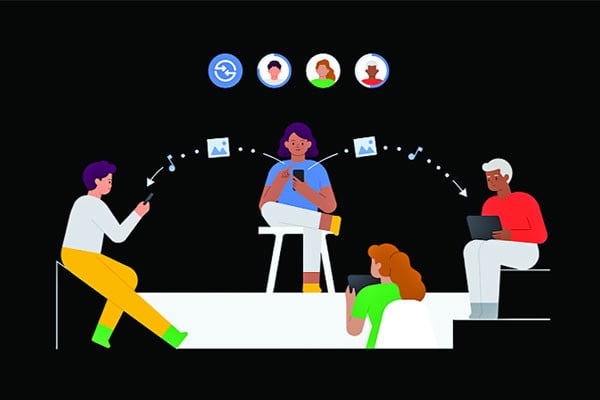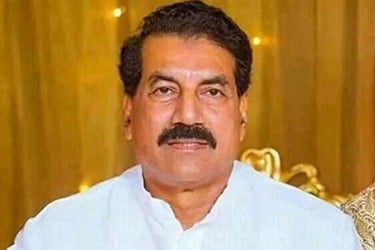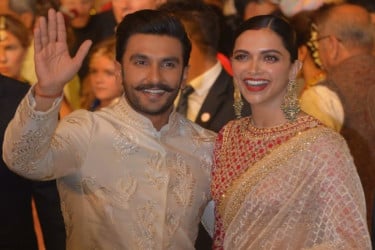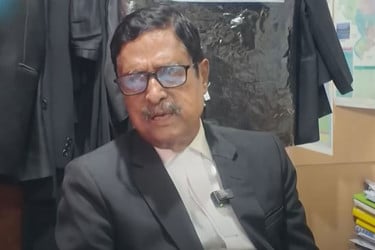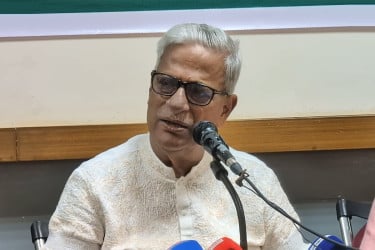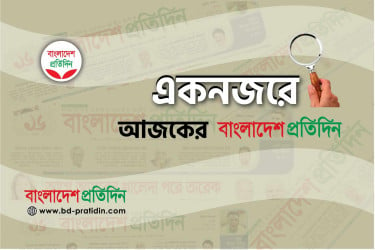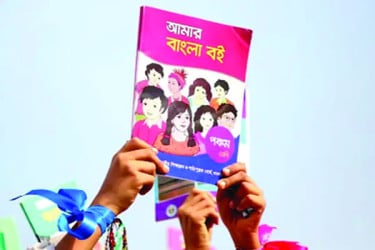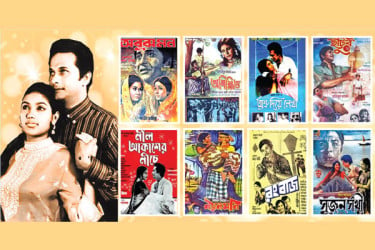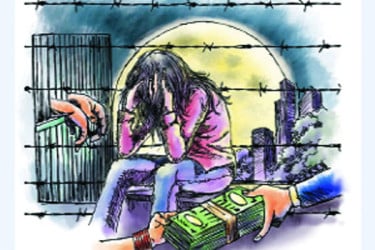উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মের আগমনি বার্তা নিয়ে আসে তীব্র রোদ আর ঘাম ঝরানো গরম। অথচ অবাক করা বিষয় হলো, যখন এই তীব্র গরম অনুভূত হয় তখন আমাদের পৃথিবী সূর্য থেকে তার কক্ষপথের সবচেয়ে দূরে অবস্থান করে। একে জ্যোতির্বিজ্ঞানে অ্যাফেলিয়ন বা ‘অপসূর’ বলা হয়। পূর্বাঞ্চলীয় সময় অনুসারে, গত বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টা ৫৫ মিনিটে পৃথিবী সূর্য থেকে তার কক্ষপথের সর্বোচ্চ দূরত্বে পৌঁছেছিল। যা সূর্য থেকে পৃথিবীর নিকটতম বিন্দুর চেয়ে প্রায় ৩০ লাখ মাইল বেশি দূরে।
মৌসুমি তাপমাত্রার পরিবর্তনের কারণ নিহিত-পৃথিবীর অক্ষীয় ঢালে। আমাদের গ্রহ প্রায় ২৩.৫ ডিগ্রি কোণে হেলে আছে। অর্থাৎ বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ কম বা বেশি সূর্যালোক পায়। জুলাই মাসে, উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে থাকে। ফলে দিনগুলো দীর্ঘ এবং সূর্যের কোণ বাড়ে। ফলে সরাসরি সূর্যালোক পৃথিবীতে বেশি পরিমাণে পৌঁছায়। এগুলোই গ্রীষ্মকালীন উষ্ণতার জন্য দায়ী। অন্যদিকে পৃথিবীর কক্ষপথের আকৃতি ঋতু পরিবর্তনে খুব সামান্যই ভূমিকা পালন করে। এটি পুরোপুরি গোলাকার না, ডিম্বাকার। তবে সূর্য থেকে নিকটতম এবং দূরতম বিন্দুর মধ্যে পার্থক্য তুলনামূলক কম।
সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি ৩০ লাখ মাইল। জানুয়ারির পেরিহেলিয়ন অবস্থার তুলনায় এখন, অর্থাৎ জুলাই মাসে, পৃথিবী সূর্য থেকে প্রায় ৩১ লাখ মাইল বেশি দূরে আছে। যা গড় দূরত্বের তুলনায় মাত্র ৩.৩ শতাংশ বেশি। সহজভাবে বললে, সূর্যের থেকে পৃথিবীর দূরত্বে যে পরিবর্তন হয়, তা খুব সামান্যই। এই সামান্য পরিবর্তনে সূর্যের শক্তি মাত্র ৭ শতাংশ কম আসে পৃথিবীতে। অথচ পৃথিবীর ঢালের প্রভাবে প্রাপ্ত সূর্যালোকের পরিমাণ কয়েকগুণ বেড়ে যায় বা কমে যায়।
তাই সত্যি বলতে গেলে, এখন সূর্য থেকে সামান্য কম শক্তি পেলেও সেই প্রভাব পৃথিবীর ঢালের তুলনায় খুবই নগণ্য। শেষ পর্যন্ত, আমরা সূর্যের কতটা কাছাকাছি আছি তা গ্রীষ্মকে গ্রীষ্মের মতো অনুভব করায় না বরং আমরা সূর্যের দিকে কীভাবে হেলে আছি, সেটাই আসল।