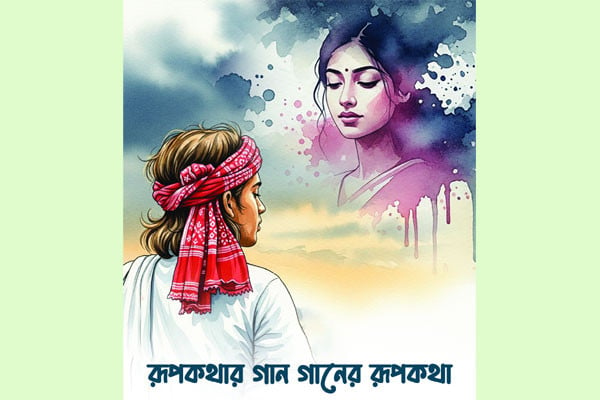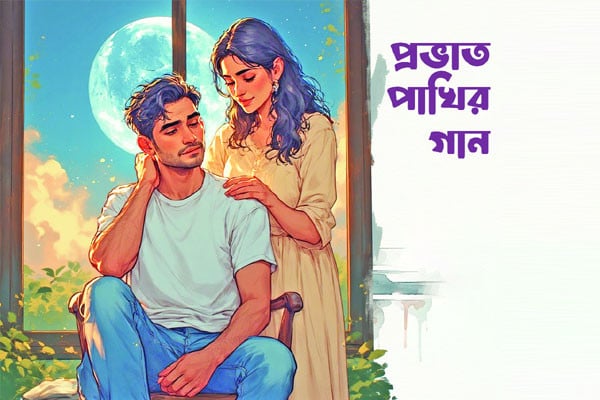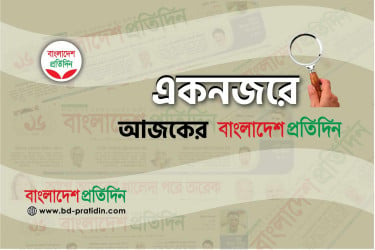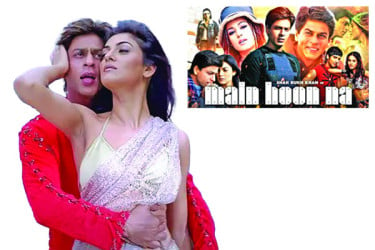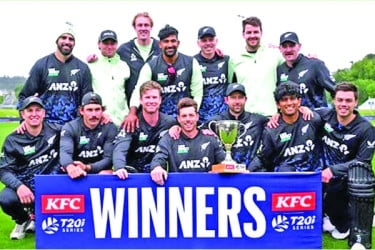প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীজুড়ে মানবিক মূল্যবোধের চরম সংকটময় মুহূর্তে বাংলা কথাসাহিত্যে যে কয়েকজন লেখকের হাতে নতুন এক বৈপ্লবিক ধারা সূচিত হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের অন্যতম। তাঁর রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, নিয়তিবাদ ইত্যাদি। তিনি ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ ও মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, যা তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে। জীবনের নাতিদীর্ঘ পরিসরে তিনি রচনা করেন চল্লিশটি উপন্যাস ও প্রায় তিন শ ছোটো গল্প। তিনি ছিলেন সাহিত্যে জীবননিষ্ঠ, মৃত্তিকা ঘনিষ্ঠ এবং মানবমনের রহস্য সন্ধানী। নিপীড়িত মানুষের প্রতি বিশ্বস্ততার কারণে চলমান সমাজের অসহায় মানুষগুলোকে একত্র করে একটা শোষণহীন সমাজ গড়ার প্রয়াস তাঁর উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে কল্লোল যুগ পর্যন্ত প্রবাহিত বাংলা কথাসাহিত্যের ধারাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু যে স্ফীততর বা অগ্রগামী করেছেন তা নয়, সেখানে তিনি এনেছেন অচেনা আন্দোলন, সৃষ্টি করেছেন অস্থির ঘূর্ণি। পাড় ভেঙেছেন, তল কেটেছেন, দ্বীপ জাগিয়েছেন, ঢেলেছেন প্রচুর লোনাজল। মধ্যবিত্ত জীবনের কৃত্রিমতা, ন্যাকামি ও ভণ্ডামি ত্যাগ করে তিনি চাষি, মজুর, শ্রমিক প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছেন।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতিক্রমী হওয়ার কারণ হলো- বাংলা কথাসাহিত্যের মূল বস্তুবাদী ধারার স্বতন্ত্র স্রষ্টা তিনি। সমকালীন অনেক লেখকের মতো পাঠকনন্দিত বর্ণনাবহুল নয়, বরং তাঁর সাহিত্য জীবনের সত্যকথা নিয়ে পাঠকের আকর্ষণ ধরে রেখে, বলেছেন সত্যের কথা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ‘মানুষই আমার চরিত্র, মানুষই আমার জীবন।’ তাই মানুষের জীবন, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, শ্রমজীবী মানুষের জীবনের বাস্তবতাই হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য।
মানিক সেই লেখক, যিনি শিল্পত্ব ও মনস্তত্ত্বের মোহের নিগূঢ় নির্মম ও বলিষ্ঠ হাতে ছেদন করে, জনগণের জীবন কাহিনিকে সূক্ষ্ম, সুস্থ শ্বাসে গ্রহণ করেছেন। শ্রেণির বাঁধন তাঁর মতো আর কোনো লেখক ছিঁড়তে পারেননি।
নিম্ন ও নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মানুষের প্রতি তাঁর যে আন্তরিক ভালোবাসা, তা নিছক শিল্প বা শিল্পীর নয়, বরং একনিষ্ঠ আত্মীয়ের। তিনি মানুষকে ভালোবেসেছেন মানুষ হিসেবে নয়, বরং মনের জ্বালা দিয়ে। তাঁর ‘পদ্মানদীর মাঝি’তে যে অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষতা ও শ্রেণি চেতনার উচ্চারণ, তা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিরল। এ উপন্যাসে পূর্ববঙ্গে সর্বহারা জেলে সম্প্রদায়ের জীবন চিত্রিত হয়েছে এবং সংলাপে ব্যবহার হয়েছে পূর্ববঙ্গের সেই শ্রেণিরই ভাষা। মুখের ভাষা চারিত্রিক বাস্তবতার অবিবেচ্ছদ্য অংশ, ভাষার এমন নিখাঁদ বাস্তবরূপ মানিকের আগে কারও কলমে উঠে আসেনি। গ্রামীণ জীবনের দৃশ্যচিত্র এবং বাস্তবরূপ আন্তচিত্র নির্মাণে তিনি গ্রামীণ জীবনচিত্রের অন্য রূপকারদের তুলনায় বাস্তবতায় ও চিত্র নির্মাণের অভিনবত্বে যে প্রাগ্রসর চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন, তা বৈপ্লবিক গুণগ্রামে চিহ্নিত। তিনি রোমান্টিক ভাবতালুতার আশ্লেষ থেকে বাংলা কথাসাহিত্যকে মুক্ত করেছেন। তাঁর ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’র গাওদিয়া গ্রাম, ‘পদ্মানদীর মাঝি’র কেতুপুরের জেলেপাড়া তাঁর উপন্যাসের পটভূমি নয়, ভিত্তিভূমিও। তিনি একেবারেই ভাবাবেগবর্জিত। উপন্যাস তাঁর হাত ধরে এগিয়ে এসেছে নিম্নতর ভাবাবেগবর্জিত। মানুষ তাঁর শিল্পের জমিনে মানুষ হয়েই দেখা দিয়েছে, প্রতীক হয়ে ওঠেনি।
একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ হয়ে তিনি নিজের শ্রেণিকে ডিঙিয়ে সমাজের একেবারে নিম্নস্তরের মানুষের শুধু জীবনী নয় বরং তাদের নোংরা অবয়ব, হাস্যকর ক্ষুদ্রতা, অমার্জিত পশুত্ব, ব্যর্থতার পরিচয় অঙ্কন করেছেন। তাঁর শিল্পে বস্তু সত্য, বস্তুর ভিত সত্য নয়। মানিকের দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক, ভাষা আধুনিক। তাতে ফেনিলতা বা উচ্ছ্বসিত বাগবাহুল্য নেই, আড়ম্বরহীন, অনানুষ্ঠানিক- ‘আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোট বাবু।’ কুসুমের এ উক্তিতে অনেক কথা বলা হয়েছে, কিন্তু উচ্ছ্বাস নেই। বারবার প্রশ্ন করেছেন লেখক এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করেছেন, যেন তিনি সত্যকে আবিষ্কার করতে চান।
মানিকের চোখে জীবনটা কল্পনার চেয়ে বড় বলেই জীবন সংগ্রামে তাঁর সৈনিকদের রোমান্টিকতায় আপ্লুত করেননি। তাঁর আগে অনেকের লেখাতেই ভদ্র জীবনের বিরোধ, ভণ্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা, অবিচার, অনাচার, বিকারগ্রস্ত, সংস্কারপ্রিয় যান্ত্রিকতা ইত্যাদি চিত্র ধরা পড়েছে। তবে তিনি এসবের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যে সমাজের অবহেলিত মানুষ ঠাঁই পেয়েছে। তিনি নিজেকে শোষিত সমাজের বিবেক বলে কল্পনা করেছেন। তাই তিনি প্রথা-সংস্কার এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেছেন।
তাঁর সাহিত্যে মাইক্রো-এনালিসিস বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের অবিরল সান্নিধ্য পাঠকচিত্তকে নিমগ্ন রাখে। প্রধান চরিত্রে পক্ষাবলম্বন করে কাহিনি বর্ণনা করার জটিল রীতির উদ্ভাবক তিনি। বাংলা সাহিত্যে তিনি কথাসাহিত্যকে সঞ্চারিত করেছেন নতুন রং, রস দিয়ে। তাঁর আগে কল্লোল গোষ্ঠী গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে আধুনিকতার পতাকা উত্তোলন করলেও তা ছিল রোমান্টিকতায় ভরপুর কিন্তু তিনি সৃষ্টি করলেন মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যা। মানিকের হাতে নর-নারীর প্রেম, যৌন সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে যা আগে প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। তিনি যে চরিত্রগুলো নির্মাণ করেছেন তা এদেশের মানুষের জীবনচিত্র। ‘পদ্মানদীর মাঝি’, ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ ইত্যাদি উপন্যাসে তাঁর দৃষ্টান্ত মেলে। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য প্রবাহের উদঘাটনমূলক উপন্যাস এবং অস্তিত্ববাদী লক্ষণযুক্ত চরিত্রের প্রথম প্রবক্তা তিনি। তাঁর রাজকুমার, শশী ইত্যাদি চরিত্রে চেতনাপ্রবাহ ও অস্তিত্ববাদের সন্ধান মেলে।
বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম মার্কসবাদের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন সচেতনভাবে, সার্থকভাবে।
তিনি কাহিনির নির্মাণ-প্রকরণে এ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। অপূর্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি চরিত্রগুলো সৃষ্টি করেছেন।
নানা মত-পথ-শ্রেণির মানুষ নিয়ে উপন্যাস তখন নতুন নয়। তবে মানিক সেসব মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির গভীর সত্য উন্মোচন করেছেন। চরিত্রগুলোর পেছনের চালচিত্রও তিনি সম্পূর্ণ করেছেন।
মানিক তাঁর শিল্পকর্মের কাহিনি বিন্যাস ও পরিবেশ রচনায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। জীবনের জটিলতায় চামড়া যাদের কুঁচকে গেছে, তারাই তাঁর কাহিনির চরিত্র।
জীবনে যারা বাঁচার জন্য তীব্র পাঞ্জা কষে মৃত্যুর সাথে, যারা প্রতিদিনের দুমুঠো অন্নও পায় না, ঘরে যাদের আলো জ্বলে না, অন্যের ঘরে আলো জ্বালাতে যারা জীবনপাত করে- সেই সব মানুষ মিছিল করেছে মানিকের শিল্পের জমিনে। সে মানুষ ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’র শশী খুঁজেছে, সেই মানুষ তাঁর পদ্মা পাড়ের কেতপুর গ্রাম থেকে উঠে এসে বসতি স্থাপন করেছে ময়না দ্বীপে। সেই ছিন্নমূল, উদ্বাস্তু মানুষগুলো আবার ভিড় করেছে শহরের বস্তিতে।
কলেজপড়ুয়া মানিক যার প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; নির্জনে প্রিয়ার মুখ স্মরণ করে কবিতা লিখতে গেলে তাঁর চোখে ভাসতো সেই সব মুখ, যাদের মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, সেসব স্টেশনের ডেলি প্যাসেনজারের মুখ, খালের ধারে, নদীর ধারে, বনের ধারে বসবাসকারী গ্রাম্য চাষি, জেলে তাঁতিদের কষ্টপীড়িত মুখ। এদের জীবনের যন্ত্রণাই তাঁর সাহিত্যের উপকরণ। তাঁর ‘পদ্মানদীর মাঝি’র কেতুপুর, পুতুল নাচের ইতিকথা’র গাওদিয়া-তাদের নিজ নিজ নামের মতোই সামান্য, শ্রীহীন ও অন্ধকারে প্রপীড়িত। পদ্মানদীর মাঝির জীবন আরও নিম্নগামী। নদীর মতোই ভাটামুখী।
মানিক ভাষা ব্যবহার করেছেন বিষয়ানুগ, সাধারণের নিত্য ব্যবহার্য ভাষা। ঘষামাজা নেই, তবু স্বাস্থ্য আছে, শ্রী আছে। তাঁর সব ঘটনাই সাধারণ মানুষের জীবনের। বীরের জীবনের নয়, শক্ত সামর্থ্য জীবনের নয়। কাদা মাটির মানুষের জীবনের। লেখক হওয়ার আগে পাঠক মানিকের জিজ্ঞাসা ছিল- সাহিত্যে সাধারণ মানুষ উঠে আসে না কেন? এ প্রশ্নের জবাবই তাঁর শিল্পের সারা দেহ। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন- ‘‘বর্তমান, প্রত্যক্ষ ও সমসাময়িকের মধ্যেই তিনি আজীবন শিল্পের উপাদান খুঁজেছেন এবং তাঁর সে অংশটুকুর শিল্পরূপ দিয়ে গেছেন। তাও বিত্তহীন সর্বসাধারণের সর্বাধিক পরিচিত।”
সমাজ ও মানুষের, সামগ্রিকভাবে উন্নতকল্পে কার্ল মার্কস যেভাবে চিন্তা করেছিলেন, মানিকের লেখা থেকে বোঝা যায়, সে চিন্তার দোসর তিনি নিজেও।
দ্বন্দ্ব ও তাঁর থেকে মানব চরিত্রের অপরাভূত শক্তি, দুর্বলতা, রহস্যই তাঁর শিল্পের মূল আঁধার; যা আমাদের শ্রেণি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শোষণহীন, শ্রেণিহীন সমাজের ইঙ্গিত করে। তাঁর শিল্পে ভাঙনের, বদলের, পরিবর্তনের চিত্র দেখা যায়। তিনি তাঁর লেখায় রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রথা, সংস্কার- এ সবের ভিতরে প্রবেশ করে ব্যাধিগ্রস্ত সমাজকে বদলানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর চিন্তা প্রবাহের সাথে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী জীবনের ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধি সর্বত্রই অটুট থেকেছে।
পুরোনো সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার ভিতরে দ্বান্দ্বিক বাস্তবতার বিস্ফোরণের পূর্ণ চিত্র মেলে তাঁর রচনায়। আধা বুর্জোয়া বা আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজজীবনের সাথে শোষিত মানুষের শ্রেণিগত বৈষম্য ও বৈপরীত্য দৃঢ়মূল। তাঁকে সহজ প্রীতির বন্ধনে বেঁধে এক করা যাবে না। সেই বৈষম্যকে সমূলে উৎপাটিত করার একমাত্র উপায় শোষণমূলক ওই সমাজকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলা। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে বিশ্বাসী শিল্পী মানিক সেই কাজটি দুরন্ত শক্তিতে সম্পাদন করার ব্যাপারে সাহায্য করতে সচেষ্ট হয়েছেন।
ক্লেদাক্ত সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্বিষহ অবক্ষয় বাসা বেঁধেছে, সুবিধাবাদী মুষ্টিমেয় একটি শ্রেণি তারই মধ্যে বারবার সুকৌশলে শোষণের সুরক্ষিত দুর্গ গড়ে তুলেছে। সেই দুর্গ ভাঙার সচেতন, সংগঠিত আহ্বানই তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা জোগায়, দিকনির্দেশনা করে।
বাংলা কথাসাহিত্যের স্বরূপ ও তাৎপর্য নির্ণয়ে প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির নব নব প্রয়োগ, জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানায়, শিল্পে তাঁর সত্য রূপায়ণে তীক্ষè সচেতন ও আন্তরিক ব্যাকুলতায় তিনি প্রেরণা হয়ে আছেন।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই লেখক, যিনি বলেন- ‘‘ফুলগুলি সরিয়ে নাও, ফুলকে দিয়ে মানুষ বড় মিথ্যে বলায়, তার চেয়ে আমার পছন্দ আগুনের ফুলকি-যা দিয়ে কোনদিন কারো মুখোশ হয় না।”