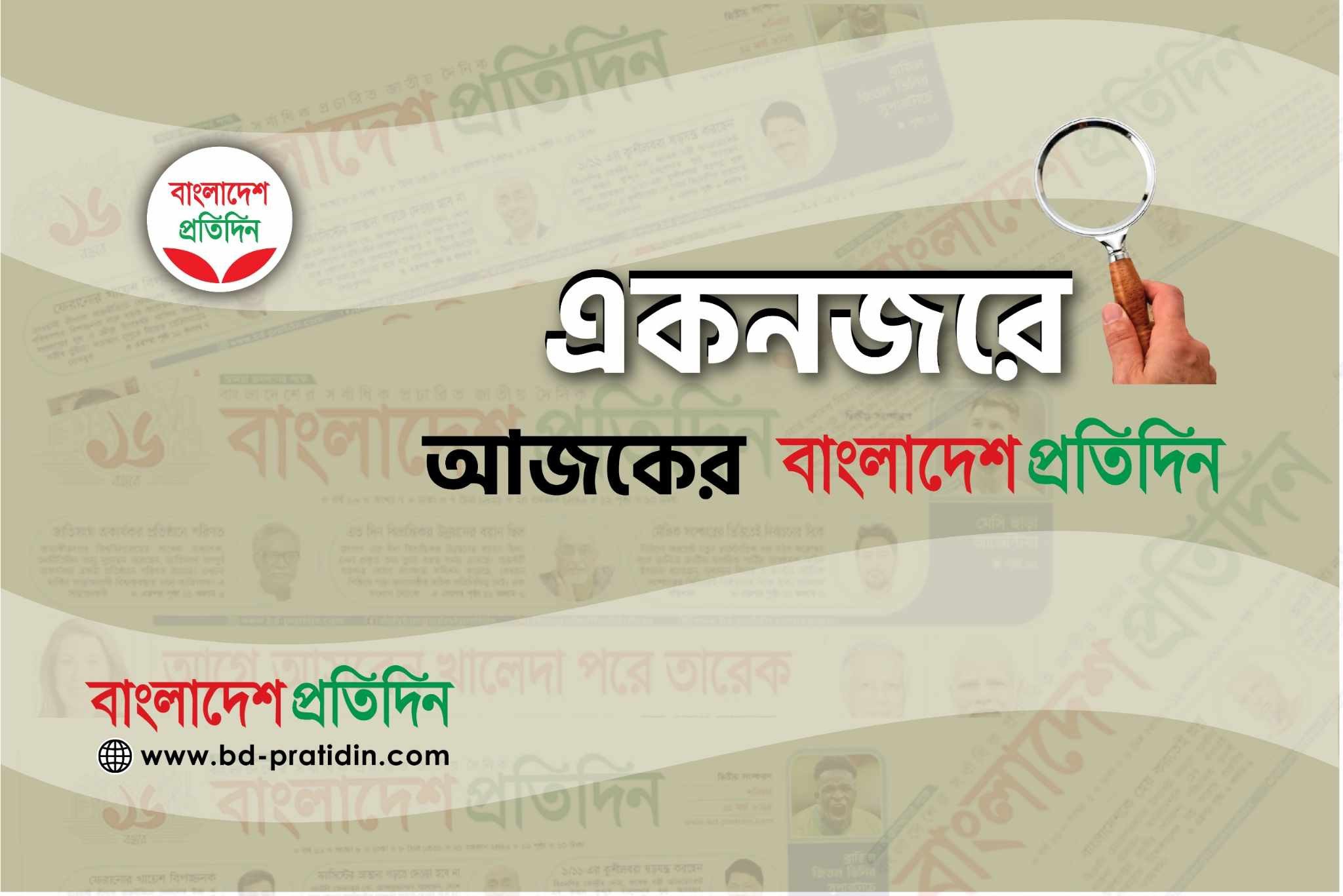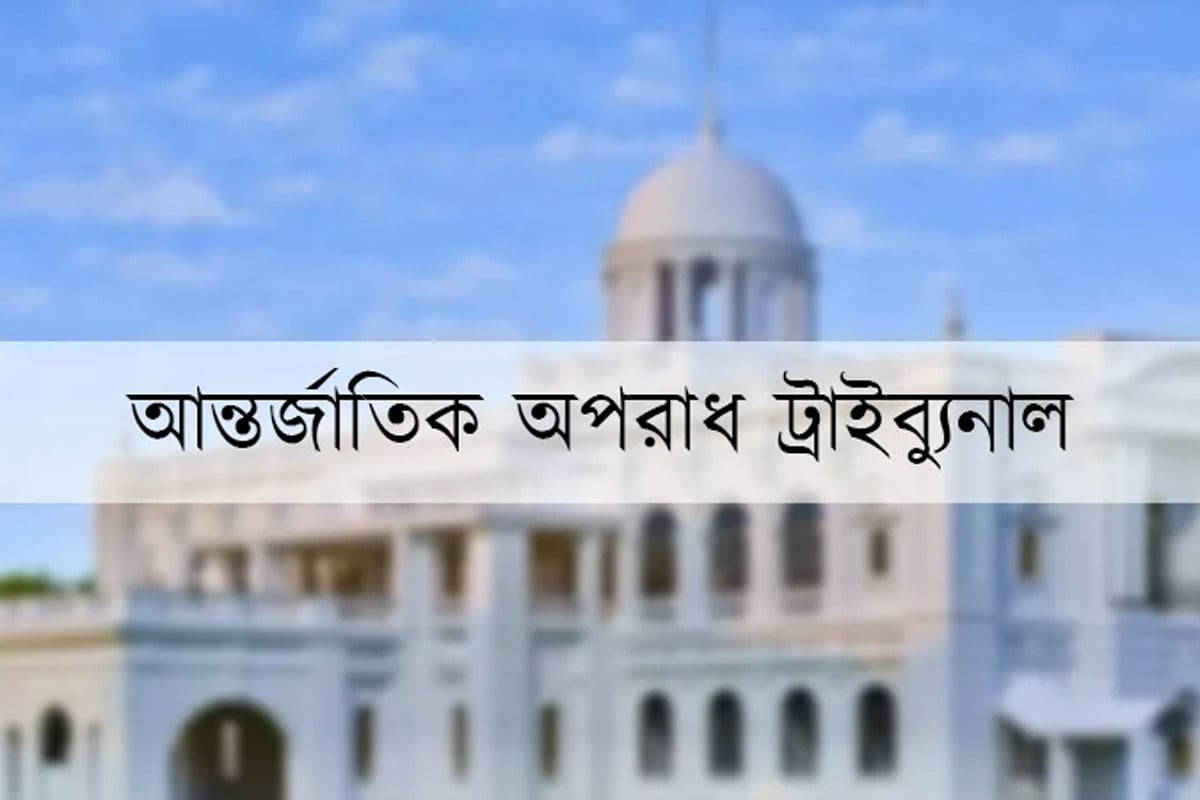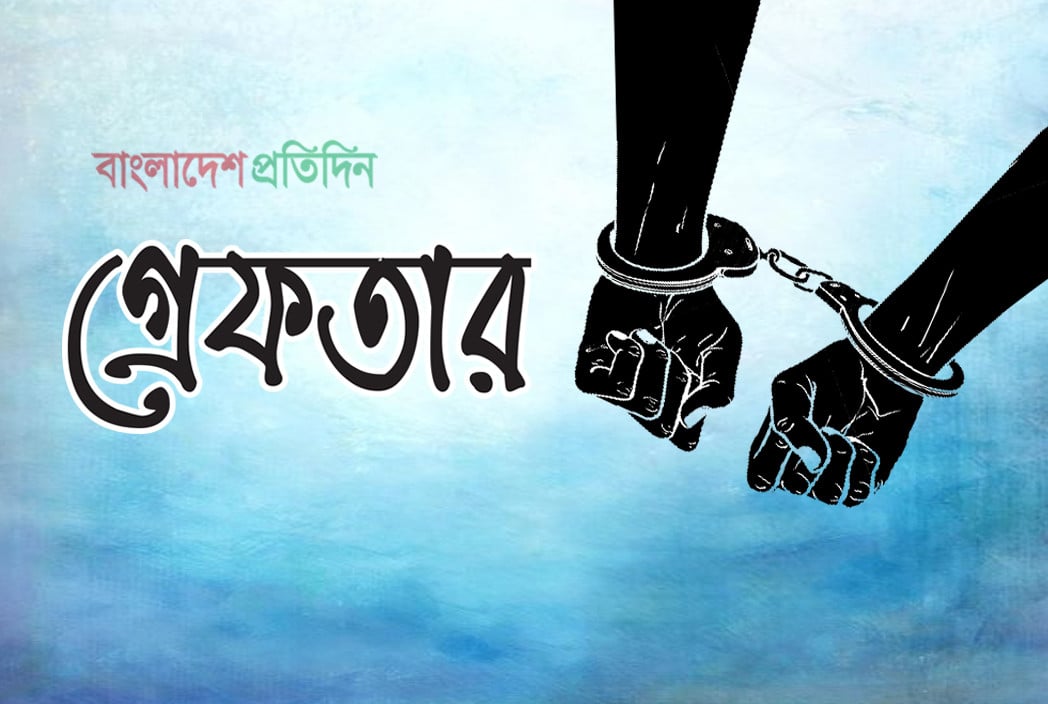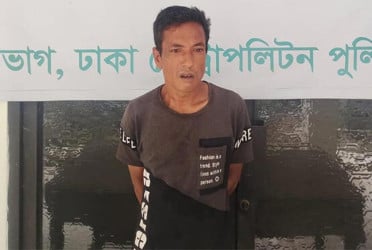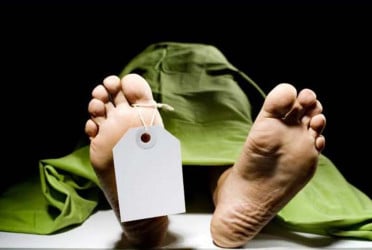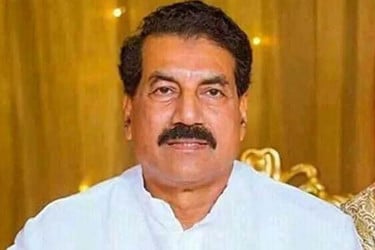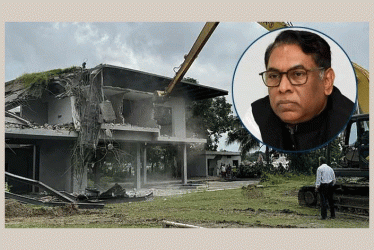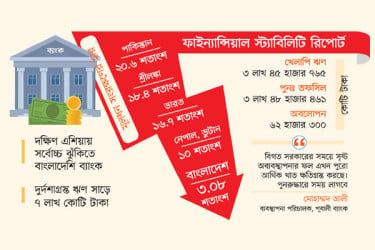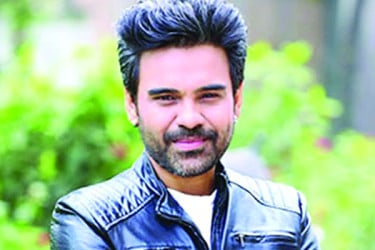নির্বাচন কমিশন (ইসি) দেশে প্রচলিত আসনভিত্তিক ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট (এফপিটিপি) পদ্ধতির পক্ষেই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে।
অন্তর্বর্তী সরকার, সংবিধান ও নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনও বিকল্প সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতির পক্ষে সুপারিশ করেনি। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপের আলোচ্যসূচিতেও সংসদের নিম্নকক্ষে পিআর পদ্ধতির বিষয়টি স্থান পায়নি। তবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এখনো পিআর পদ্ধতির নির্বাচন দাবিতে সোচ্চার।
গত রবিবার রাজধানীর রমনার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এক সেমিনারে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, পিআর (সংখ্যানুপাতিক) পদ্ধতিতে নির্বাচন এবং ভোটের আগে সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে অন্তর্বর্তী সরকারকে বাধ্য করা হবে।
গত মঙ্গলবার ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ শাখার আয়োজনে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল পূর্ব সমাবেশে দলটির পক্ষে বলা হয়, জুলাই সনদের আইনি স্বীকৃতি ও পিআর পদ্ধতি ছাড়া নির্বাচন দেওয়া যাবে না।
বিএনপি ও তাদের সমমনা দলগুলো পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের পক্ষে না। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, ‘পিআর পদ্ধতিতে এ দেশের মানুষ অভ্যস্ত না। তারা বোঝেও না, ঠিকমতো জানেও না। কত দিন চেষ্টা করে ইভিএম বাদ দিতে হয়েছে। পিআর পদ্ধতিতে তো আমরা অভ্যস্ত না- প্রশ্নই উঠতে পারে না। সরাসরি ভোটের যে অধিকার আমার, সেই অধিকার এখানে বিঘ্নিত হয়। আমরা বিশ্বাস করি, পিআর পদ্ধতিতে জনগণের যে অধিকার, সেটা পুরোপুরি প্রয়োগ করা হবে না। জনগণ বুঝবেও না কাকে ভোট দিচ্ছে। সুতরাং এটা গ্রহণযোগ্য না।’
এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলো তাদের অবস্থান থেকে বিভিন্ন ধরনের দাবি জানাতে পারে। কিন্তু আমরা বিদ্যমান আইন অনুসারে আসনভিত্তিক এফপিটিপি পদ্ধতির নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের জানানো হয়েছে, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে রোজার আগেই নির্বাচন। আমরা সেই লক্ষ্যে আমাদের প্রস্তুতি এগিয়ে নিচ্ছি।’
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য ও নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার মনে করেন, পিআর পদ্ধতি চালু করতে হলে প্রথমে দরকার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে দলগুলো তো একমত না। দলগুলো একমত হলে তবেই পিআর পদ্ধতি সম্ভব।
গবেষক নজরুল ইসলাম তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত ‘রাষ্ট্র সংস্কার ও সংবিধান সংশোধন’ বইয়ে উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশের সংবিধানে ৬৫(২) ধারাতে (অনুচ্ছেদ) বলা হয়েছে, ‘একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী তিন শত সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে।’ পিআর পদ্ধতি চালু করতে হলে ‘একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে’ কথাটি ‘আনুপাতিক পদ্ধতি’ কথাটি দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে হবে। এ ছাড়া একাধিক আসন থেকে নির্বাচিত হওয়াসংক্রান্ত ৭১ নম্বর ধারায় (অনুচ্ছেদ) এবং উপনির্বাচন বিষয়ক ধারায় কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন আনতে হবে।
প্রসঙ্গত, দেশে সংসদ নির্বাচনে সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতি চালু হলে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের বাইরে স্বতন্ত্র কেউ প্রার্থী হতে পারবেন না। কারণ এ পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে নয়, ভোট দিতে হবে দলকে। দলের ভোটপ্রাপ্তি অনুপাতে সংসদে আসনসংখ্যা নির্ধারণ হবে। পিআর পদ্ধতিতে সংসদে আসন পাওয়ার জন্য দলগুলোর জন্য সর্বনিম্ন ভোটপ্রাপ্তির সীমা নির্ধারণ করা থাকে। কোনো কোনো দেশে প্রদত্ত ভোটের ১০ শতাংশ ভোট না পেলে সংশ্লিষ্ট দল সংসদে কোনো আসন পায় না। নেপালে এই সীমা বা ন্যূনতম সমর্থনস্তর নির্ধারণ রয়েছে প্রতিনিধি পরিষদের জন্য ৩ শতাংশ আর প্রাদেশিক পরিষদের জন্য ১.৫ শতাংশ।
সম্প্রতি নেপালের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নীলকণ্ঠ উপ্রেতি স্থানীয় সংবাদপত্র কাঠমান্ডু পোস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এই সমর্থনস্তর বা সীমা ৫ শতাংশ করা দরকার। কারণ উন্নত দেশগুলোতে কয়েকটি রাজনৈতিক দল সক্রিয় থাকলেও নেপালের মতো দরিদ্র দেশে এক শর বেশি দল নিবন্ধিত। এত দল অপ্রয়োজনীয়। সমর্থনস্তর ৫ শতাংশ করা হলে দলের সংখ্যা কমে আসবে।
জানা যায়, নেপালে ১৪২টি বর্ণ ও সম্প্রদায় রয়েছে। মাতৃভাষা রয়েছে ১২৫টি এবং ১০টি ধর্মের মানুষ রয়েছে। এ ধরনের একটি বহুজাতিক সমাজের রাষ্ট্রপরিচালনায় সব সম্প্রদায়ে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পিআর পদ্ধতি উপযুক্ত বিবেচনা করা হলেও সেখানে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের ঘটনা ঘটছে এবং এই পিআর পদ্ধতির বিপক্ষেও মতামত আসছে। সেখানে পিআর পদ্ধতির সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের পরিবারের সদস্যদের সংসদে নিয়োগের জন্য সমালোচিত হচ্ছে। নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনেও পিআর পদ্ধতির ভালো ও মন্দ উভয় দিক উল্লেখ করে এ সম্পর্কে কোনো সুপারিশ করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম মনে করা হয়েছে।
কমিশনের প্রতিবেদনে পিআর পদ্ধতির নেতিবাচক দিক সম্পর্কে এই মর্মে বলা হয়েছে যে এর ‘একটি বড় দুর্বলতা হলো সরকারের সম্ভাব্য অস্থিতিশীলতা।’ বাংলাদেশের তুলনামূলকভাবে কম বিতর্কিত পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর ভোটপ্রাপ্তির হার এবং সে অনুসারে পিআর পদ্ধতিতে বণ্টনযোগ্য আসনসংখ্যা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, “এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হলে উল্লিখিত চারটি নির্বাচনে যেহেতু কোনো দলের পক্ষেই এককভাবে সরকার গঠন করা সম্ভব হতো না, তাই বড় দলগুলো ক্ষুদ্র দলগুলোর কাছে জিম্মি হয়ে যেতে পারত এবং ‘টিরানি অব দ্য স্মল মাইনরিটি’ বা ছোটদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারত। এ ছাড়া সরকার গঠনে ভাঙা-গড়ার খেলা প্রকট হয়ে উঠতে পারত। এমনকি সরকার গঠনে লেনদেনের প্রভাবও ঘটতে পারত। এ ছাড়া সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে দলের আধিপত্য বেসামাল পর্যায়ে পৌঁছতে পারে।”
‘ছোটদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা’র নেতিবাচক উদাহরণ হিসেবে ইসরায়েলের কথা উল্লেখ করে কমিশনের প্রতিবেদনের ফুটনোটে বলা হয়েছে, ‘এ প্রসঙ্গে গাজায় ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যকার চলমান যুদ্ধের উদাহরণ টানা যেতে পারে। অনেক বিশ্লেষকের মতে, গাজায় যুদ্ধ এত প্রলম্বিত হওয়ার একটি বড় কারণ হলো আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের কারণে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু কিছু অতিক্ষুদ্র উগ্র ধর্মান্ধ দলের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছিলেন।’
প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়েছে, ‘সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতির আরো অনেক দুর্বলতা রয়েছে, যা অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময়ে উঠে এসেছে। মতবিনিময়ের সময়ে একটি বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল করা গেছে যে অনেক ব্যক্তি ও দল যারা নীতিগতভাবে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতির পক্ষে, তাদের অনেকেই বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটির প্রবর্তনের বিপক্ষে। তাদের আশঙ্কা যে বর্তমান সময়ে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি গৃহীত হলে বিতাড়িত স্বৈরাচারের পুনর্বাসনের আশঙ্কা দেখা দেবে।’
এই কমিশন সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতির নেতিবাচক দিকের উদাহরণ দিতে গিয়ে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের কথাও তুলে ধরে। ওই প্রতিবেদনে এই মর্মে বলা হয়েছে যে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনী ব্যবস্থায় আরো স্বৈরাচারী হবে দল ও দলপ্রধান। কারণ তখন সংসদ সদস্য হতে সম্ভাব্য প্রার্থীরা আর জনগণের কাছে যাবেন না, যাবেন দলের নেতার কাছে। আগে থেকেই টাকা নিয়ে হাজির হবেন। দলের প্রধানরা মোটামুটি নিলামে তুলে প্রতিটি আসনের বিপরীতে টাকা নিয়ে নেবেন। তারপর সংসদ সদস্য নির্ধারণ করা হবে। বিষয়টি ঘটতে পারে বিদ্যমান ব্যবস্থায় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের ক্ষেত্রের মতো।
এছাড়া বর্তমান নির্বাচনী আসনব্যবস্থার সঙ্গে দেশের মানুষ পরিচিত। রাতারাতি সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে তা দেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি প্রচলনের আগে এর ভালো-মন্দ, দেশের প্রেক্ষাপট সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করেই করা দরকার। এ পদ্ধতি চালু করা হলে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত দলগুলো নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করবে। এর মোদ্দাকথা হলো, জনগণ কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থীর পরিবর্তে দলীয় প্রতীকে ভোট দেবে।
একটি দল শতকরা যত শতাংশ ভোট পাবে, সেই অনুসারে সংসদে আসন পাবে। অর্থাৎ ৩০০ আসনের মধ্যে এককভাবে সরকার গঠন করতে একটি দলকে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেতে হবে, যা হবে কঠিন। সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে দেখা দেবে আরেক সমস্যা। যদি কোনো সরকারের শতকরা ৫০ ভাগের বেশি আসন না থাকে তাহলে দেখা যাবে, সরকার বাজেটসহ বিভিন্ন আইন পাস করতে পারছে না। আইন পাসের জন্য অন্য দলের শরণাপন্ন হতে হবে। সেসব দল সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন সুবিধা আদায় করে নেবে। উন্মোচিত হবে নতুন দুর্নীতির ক্ষেত্র।
ছোট দলগুলো কারণে-অকারণে সরকারকে ফেলে দিতে চাইবে এবং কোনো সরকারই সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না। বর্তমানে জনগণের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে ৩০০ সংসদ সদস্য নির্বাচনের যে বিধান রয়েছে, সেটির মাধ্যমে প্রতিটি আসনে মনোনয়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা হয় এবং এর মাধ্যমে স্থানীয় নেতৃত্ব তৈরি হয়। কিছু নেতা তৈরি হয়। জনগণের ভোট পেতে হলে তাঁদের স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মিশতে হয়। কথা বলতে হয়। সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনী পদ্ধতি চালু হলে জনগণের কোনো সংসদ সদস্য থাকবে না। থাকবে দলীয় প্রধানের আনুগত্য, পোষা সংসদ সদস্য, যাঁদের আনুগত্য থাকবে শুধু দলীয় প্রধানের কাছে। সংসদ হবে দলীয় ক্লাব।
সংস্কার কমিশন সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতির সমস্যা হিসেবে আরো উল্লেখ করেছে, ‘সংসদের আসনসংখ্যা ভাগ হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভোটপ্রাপ্তির অনুপাতের হারে। এ ব্যবস্থায় ভোটাররা ভোট প্রদান করেন রাজনৈতিক দলকে, কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থীকে নয় এবং রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আসনসংখ্যা নির্ভর করে দলের প্রাপ্ত ভোটের হারের ওপর। তবে কোনো আসন পেতে হলে দলকে ন্যূনতম হারের ভোট পেতে হয়।
উদাহরণস্বরূপ, কোনো দল যদি সারা দেশে মোট প্রদত্ত ভোটের ৫ শতাংশ ভোট পায়, তাহলে সেই দল সংসদের মোট আসনের ৫ শতাংশ আসন পাবে। তবে সংসদীয় আসনের ভাগ পাওয়ার মানদণ্ড যদি ন্যূনতম ৫ শতাংশ হয়, তাহলে আমাদের দেশের ছোট দলগুলো, যাদের প্রায় সবারই ভোটপ্রাপ্তির হার ৫ শতাংশের কম, তারা কোনো আসন পাবে না।’
সার্বিক এই পরিস্থিতিতে সংস্কার কমিশনের মূল্যায়ন, “এটি সুস্পষ্ট যে বর্তমান আসনভিত্তিক ‘ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট’ এফপিটিপি এবং সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই রয়েছে। দুটি পদ্ধতিই বলতে গেলে ‘মিক্সড ব্লেসিং’ বা মিশ্র আশীর্বাদ। এ বিবেচনায় অনেক দেশেই এখন মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। মিশ্র পদ্ধতিতে সংসদের একাংশ এফপিটিপি পদ্ধতিতে, আরেকাংশ সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে থাকে। সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিও বহু রকমের হয়ে থাকে। এ ছাড়া সংসদের দুই কক্ষে দুই ধরনের পদ্ধতিও থাকতে পারে।”
কমিশনের প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ‘এমনি প্রেক্ষাপটে অংশীজনের পক্ষ থেকে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি প্রচলনের পক্ষে-বিপক্ষে দাবি উঠেছে। তবে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় অনেক অংশীজন একটি মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহারের সুপারিশ করেছে। অনেকে আবার সংসদে উচ্চকক্ষ স্থাপিত হলে সেখানে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি প্রচলনের দাবি তুলেছে। তবে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতির বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চরম মতবিরোধ রয়েছে।’
এ বিষয়ে কমিশন নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করে বলেছে, ‘রাজনৈতিক ঐকমত্যের অভাবের কারণে নির্বাচনপদ্ধতি পরিবর্তনের বিষয়ে কোনোরূপ সুপারিশ করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বিষয়টি সম্পর্কে রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সম্মানিত রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর ছেড়ে দেওয়াই যৌক্তিক বলে আমরা মনে করি।’
সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছে, সরাসরি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট, অর্থাৎ ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট (এফপিটিপি) নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ, জাতীয় সংসদ গঠিত হবে। কমিশন এফপিটিপি নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণের সুপারিশ করছে। কারণ এটি স্থিতিশীলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে, যা আমাদের মতো একটি নাজুক গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব ও বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
এদিকে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন এফপিটিপি পদ্ধতিরও নেতিবাচক দিক সম্পর্কে বলেছে, ‘এর মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের তাঁদের নিজ সংসদীয় আসনে আধিপত্য সৃষ্টির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। তাঁদের পক্ষে স্থানীয় সরকারসহ অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ তৈরি হয়। এ ছাড়া অন্য সব প্রতিষ্ঠানের ওপর অযাচিতভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং বিভিন্ন বিশেষত স্থানীয় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তাদের পদায়ন ও বদলি নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া পুলিশ এসকর্টসহ তাঁরা বিভিন্ন ধরনের অযাচিত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। এসব অযাচিত সুযোগ-সুবিধা এবং একচ্ছত্র আধিপত্যের কারণে আমাদের সংসদ সদস্যদের অনেকেই স্থানীয় পর্যায়ে জমিদারে পরিণত হয়েছেন। এ ব্যবস্থায় মনোনয়ন বাণিজ্যের মতো অপকর্ম, রাজনীতির ব্যবসায়ীকরণ এবং ব্যবসায়ের রাজনৈতিকীকরণ ঘটে। এসব সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক দেশেই পিআর পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।’
সৌজন্যে- কালের কণ্ঠ।