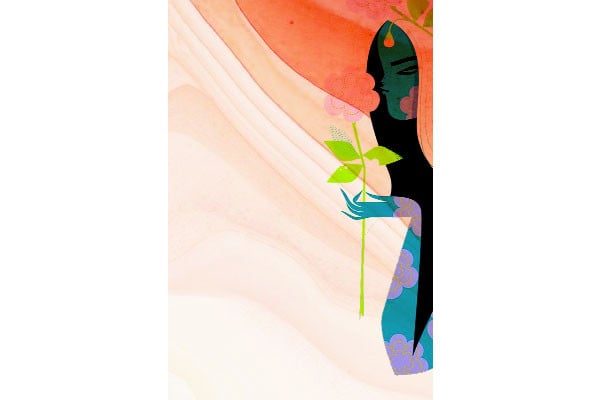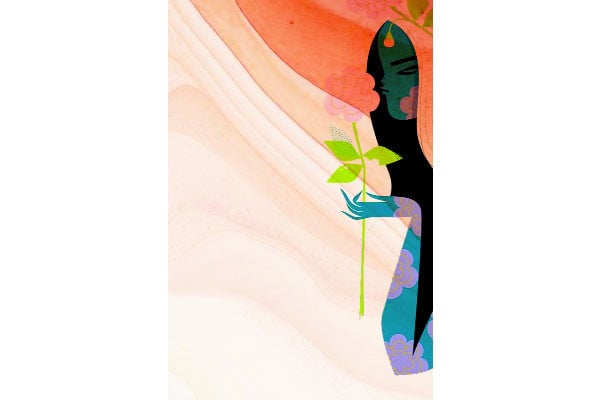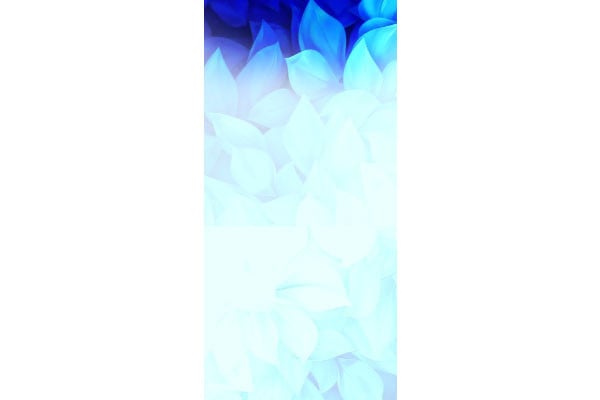ঐতিহ্যানুরাগী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ শুরু করেছেন দেবী বন্দনার মধ্য দিয়ে। দেবী বীণাপাণির বরপ্রার্থনা না করে যেন এত বড় কাজ সম্পন্ন করা অনুচিত। কবিগুরু বাল্মীকির চরণযুগলেও তিনি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন। আসলেই এটা ছিল তৎকালীন প্রথা। কোনো কাব্য বা পুঁথি, লোকগাথা শুরুর আগে বন্দনারীতি বাংলা কাব্যের আদি উৎসের ভিতর নিহিত। যে মধুসূদন মনেপ্রাণে, ভেতর-বাহিরে পুরোপুরি ইউরোপীয়, অথচ ঐতিহ্যের কাছে, প্রথার কাছে তিনি অনুগত। আবার দৃঢ়চিত্তে প্রথা ভেঙেছেন। চুরমার করে দিয়েছেন পুরনো কাব্যরীতি, কাব্যপ্রথাকে। সৃষ্টি করেছেন নবতর কাব্যরীতি, কাব্য-ভাষার। যে মধুসূদন হোমার, ভার্জিল, মিলটন, ট্যাসোর অনুরক্ত; সেই তিনিই আবার বাল্মীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস, জয়দেবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। গ্রিক সাহিত্যের অপরাজেয়তা থেকে মেঘনাদ চরিত্রের নির্ভিকতা, আবার জগদ্রামী রামায়ণ থেকে প্রমীলাকে আত্মীকরণ। মেঘনাদবধ কাব্যের অধিকাংশ চরিত্র রামায়ণ থেকে আহরিত। কিন্তু মেঘনাদপত্নী প্রমীলার কোনো অবস্থান নেই বাল্মীকির রামায়ণ, এমনকি ব্যাসের মহাভারতেও। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই নামটি আছে, কিন্তু চরিত্র-চলনে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন, প্রমীলা মধুসূদনের স্বকল্পিত। তবে ড. বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘প্রমীলার উৎস’ প্রবন্ধে দাবি করেছেন, মেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীলা চরিত্র মধুসূদন নিয়েছেন ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে রচিত জগদ্রামী-রামপ্রসাদী ‘অদ্ভুতরামায়ণ’ থেকে। এই রামায়ণে উল্লিখিত মেঘনাদপত্নী সুলোচনার ছায়াবলম্বনে প্রমীলার সৃষ্টি। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ৩ মার্চ ‘সাপ্তাহিক দেশ’ পত্রিকায় বিশ্বনাথ বাবুর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই বিতর্কের অবতারণা করেন শ্রীমতি গার্গী দত্ত। আমেরিকা থেকে গবেষক ক্লিনটন সিলিও বিতর্কে অংশ নেন। জগদ্রামী রামায়ণের সুলোচনা মেঘনাদের প্রমীলা নয়, এটির পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন গার্গী দত্ত। আর সিলির সম্ভাবনাকে একদম উড়িয়ে দেননি।
সে যাই হোক, পুরো ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ রামায়ণ থেকে উৎসারিত, বাল্মীকি যেখানে মূর্তমাণ কিন্তু তার প্যাটার্ন, চরিত্র-সৃজন ইউরোপীয়। মধুসূদনের ভেতর এই দ্বৈতসত্তা সর্বদা সক্রিয় ছিল। একের ভেতরে দুই। মধুসূদনের ভেতরে মাইকেল, অথবা মাইকেলের ভেতরে মধুসূদন। তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টি পর্যালোচনা করলে, তাঁর জীবন বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব, একজন অসামান্য প্রতিভাধর ব্যক্তির ভেতর দুটি সত্তা বিরাজমান; একটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে মধুসূদন, অন্যটি মাইকেল।
মধুসূদনের জন্ম হয়েছিল একটি গোঁড়া হিন্দু পরিবারে। যেখানে সনাতন সব ধরনের সংস্কার চালু ছিল। পৌত্তলিক পূজা থেকে সব পূজা-পার্বণ দত্তবাড়িতে অনুষ্ঠিত হতো। বাড়িতে পঠিত হতো রামায়ণ, মহাভারতসহ বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থ। শিশু মধুসূদনের মনে এর প্রভাব পড়েছে ব্যাপকভাবে। কৈশোরে ফারসি শিখেছেন মৌলভি সাহেবের কাছে। পুরাণপ্রীতি, ফরাসি শিক্ষা, ধনী পরিবারের বিলাস-ব্যসন, আর গ্রামের ধুলোমাটি, কপোতাক্ষ তীরের সুষমা সব মিলিয়ে গঠিত হয়েছিল মধুমানস। ছাত্রজীবন থেকেই ইংরেজিপ্রীতি, ইংরেজি সাহিত্যে বড় কবি হওয়ার বাসনা তাঁকে করেছিল ইউরোপীয় সংস্কৃতির সমঝদার। তাঁর উচ্চাশা এমন স্তরে পৌঁছেছিল, যার সঙ্গে বাস্তবতা ছিল অনেক দূরে। আশা আর প্রাপ্তির টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রে দানা বেঁধেছিল সুদৃঢ় আমিত্ব; যেখানে অন্য সবই মূল্যহীন। যা তাঁকে নিয়ে গেছে স্বপ্নের শিখরে, আবার পৌঁছে দিয়েছে চরম স্বপ্নহীনতার পাদদেশে। আশা ও প্রাপ্তির মধ্যে যে তফাত, সে তফাতটিকে তিনি বরণ করেছেন বুকের ক্ষরণ দিয়ে, নিজেকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে।
অবিভক্ত বাংলার এক অজগ্রাম সাগরদাঁড়ির ধুলোমাখা মধুসূদন নিজেকে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন খাঁটি ইংরেজের মতো। গ্রাম ছেড়ে যখন শহর কলকাতায় গমন করেছেন, তখনও কথাবার্তা, আচার-আচরণে গ্রামের প্রভাব ঘোচেনি, তার আগেই ইংরেজি শিখতে এসে নিজেকে ইংরেজ বলে ভেবেছেন। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে ভর্তি করা হয় আধুনিক শিক্ষার এক অনন্য পীঠস্থান হিন্দু কলেজে। অনেকের মতো বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করতে শিখে গেছেন। ভেবেছেন, বাংলা ভাষা জেলে ও মেছুনীদের ভাষা ছাড়া আর কিছু নয়। আর এ ভাষায় উন্নত সাহিত্য সৃষ্টি; সে তো অসম্ভব! হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) না থাকলেও তাঁর মুক্তচিন্তা, যুক্তিবাদ, উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব কলেজের ছাত্রদের মধ্য থেকে বিলুপ্ত হয়নি। ডিরোজিওর প্রভাব অন্যদের মধ্যে প্রতিফলিত হলেও মধুসূদনের মধ্যে ছিল কম। ডিরোজিয়ানরা ছিলেন যুক্তিশাসিত, কিন্তু মধুসূদন যুক্তির ধার ধারেননি। হিন্দু কলেজে মধুসূদন শিক্ষক হিসেবে পেলেন আরেক কৃতিজন, কবি ক্যাপ্টেন ডেভিট লেস্টার রিচার্ডসনকে (১৮০১-১৮৬৫)। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর ব্যুৎপত্তি, শিক্ষাদানের আন্তরিক মানসিকতা মধুসূদনের মতো অনুসন্ধিৎসু ছাত্রকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করেছিল। প্রিয় শিক্ষকের শেকসপিয়র পাঠদানে মধুসূদন যেমন মুগ্ধ হয়েছেন, তেমনি ঋদ্ধ হয়েছেন তাঁর লিখিত কাব্যপাঠে। রিচার্ডসনের প্রকাশিত কাব্য Miscellaneous Poems, Sonnets and Other Poems, Literary Leaves মধুসূদনের মনে রেখাপাত করেছে বৈকি! রিচার্ডসন ইংরেজি সাহিত্যের কবিদের নিয়ে একটি বৃহৎ সংকলন সম্পাদনা করেন এ সময়। সংকলনের নামটি ছিল Selections from the British Poets from the time of Chaucer To the present dey with Biographical and critical notices. কলকাতার ব্রিটিশ মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত এই সংকলন মধুসূদনকে একান্তভাবে অনুপ্রাণিত ও আলোড়িত করেছিল। ইংরেজি সাহিত্যে বড় কবি হওয়ার বাসনা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছিল এই সংকলন পাঠের ফলে। স্বপ্নের কবি বায়রনের দেশ যেন তাঁর দেশ হয়ে ওঠে। তিনি ভুলে যান, তাঁর জন্ম এই বাংলায়। এ সময় থেকে তিনি ইংরেজি ভাষায় কবিতা রচনা শুরু করেন এবং তা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ‘Extemporary Song’ শীর্ষক কবিতায় লিখেন :
(১)
“দূর শ্বেতদ্বীপ তরে, পড়ে মোর আকুল নিশ্বাস,
যেথা শ্যাম উপত্যকা, উঠে গিরি ভেদিয়া আকাশ;
নাহি সেথা আত্মজন; তবু লঙ্ঘি অপার জলধি
সাধ যায় লভিবারে যশঃ কিম্বা অনামা সমাধি।
(২)
জনক-জননী-ভগ্নী আছে মোর; স্নেহ পরকাশি,
তারা মোরে ভালোবাসে; আমিও তাদের ভালোবাসি;
তবু ঝরে অশ্রু বেগে, হেমন্তের শিশিরের সম,
কাঁদি শ্বেতদ্বীপ তরে, যেন সেই জন্মভূমি মম!”
এতখানি উন্মাদনা যে, কবি শ্বেতদ্বীপকে নিজের জন্মভূমি বলে ভেবেছেন। ডিরোজিও ইংরেজ হয়েও ভারতভূমিকে ভেবেছিলেন মাতৃভূমি, সেখানে মধুসূদন ডিরোজিওর জন্মভূমিকে ভেবেছেন নিজের জন্মভূমি! লন্ডনের ‘ব্ল্যাকআউট’ ম্যাগাজিনে কবিতা পাঠিয়েছেন কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থকে উৎসর্গ করে। যদিও ছাপা হয়নি সেসব কবিতা। তিনি ইংল্যান্ড যাবেন, বড় কবি হবেন, বন্ধু গৌরদাস বসাককে বলছেন, সে যেন তাঁর জীবনী লেখে। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর মধ্যরাতে বন্ধুকে তিনি লিখছেন, “তুমি জান, দেশ ত্যাগ করবার ইচ্ছে আমার হৃদয়ে এতখানি বদ্ধমূল, যা নাকি মুছে ফেলা যাবে না। সূর্য উদিত নাও হতে পারে। কিন্তু আমার এ ইচ্ছে মন থেকে কখনো বিদূরিত হবে না। নিশ্চিত জেনে রাখ- দু-এক বছরের ভিতর আমি ইংল্যান্ডে যাব, না হয় আমি আত্মহত্যা করব। এ দুটোর একটা ঘটবেই।”
১৮৪২ থেকে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কেটে গেছে কুড়িটি বছর। তাঁর বিলেত যাওয়া হয়নি। তিনি আত্মহত্যাও করেননি। আত্মহত্যা না করলেও আত্মক্ষরণে বিক্ষত হয়েছেন প্রতিদিন, এটা সহজেই অনুমেয়। কীভাবে বিদেশ যাওয়া যায়, এটা ভাবতেই এসে গেল মোক্ষম সময়। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত তাঁর বিয়ে ঠিক করলেন স্থানীয় এক সুন্দরী জমিদার-কন্যার সঙ্গে। তিনি অমত প্রকাশ করলেন, দেখা করলেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জির সঙ্গে। জানালেন- ইংরেজরা যদি তাঁকে বিলেত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন, তাহলে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবেন। কৃষ্ণমোহন তেমন আশ্বাস না দিলেও তিনি আলোচনা করলেন অ্যাংলিকান চার্চের একজন কর্তাব্যক্তি আর্চডিকন ডিয়ালট্রির সঙ্গে। আশ্বাস পেয়ে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি মধুসূদন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন। মধুসূদন নামের সঙ্গে যোগ হলো মাইকেল শব্দটি। ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে যে মাইকেল ভেতরে ভেতরে বেড়ে উঠছিল, সেই-ই পাখা মেলল; কিন্তু উড়তে পারল না। হলো না তাঁর বিলেত যাওয়া। ইংরেজ কর্তৃক প্রবঞ্চিত হলেন তিনি। ধর্ম ত্যাগের কারণে হিন্দু কলেজে পড়াশোনার সুযোগ হারিয়ে তিনি পিতার অর্থ সাহায্যে ভর্তি হলেন বিশপস কলেজে। পিতা ভেবেছিলেন পুত্রকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। কিন্তু যার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে আছে ইংরেজ কবি আলেকজান্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪)-এর সেই অব্যর্থ উক্তি- “কবিতার জন্য প্রয়োজনে বাবা-মা উভয়কেই ত্যাগ করতে হবে।” তাঁর পক্ষে কি সম্ভব ঘর ছেড়ে ঘরে ফিরে আসা! তিনি ফিরলেন না। একপর্যায়ে রাজনারায়ণ দত্ত আশা ছেড়ে দিয়ে পুত্রকে অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দিলেন।
এরপর ভাগ্যান্বেষণে মধুসূদন মাদ্রাজ গমন করেছেন। সেখানে শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা করেছেন। পত্রিকায় ইংরেজদের বর্ণবৈষম্য, শিক্ষাবৈষম্য, জোরপূর্বক ধর্মান্তর, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের প্রতিবাদে, বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় লিখেছেন।
বিয়ে করেছেন ইংরেজ কন্যাকে। ইংরেজদের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে শিক্ষকতায় যথার্থ পদোন্নতি ঘটেনি; যদিও ‘The Anglo Saxon and the Hindu’ দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। অথচ ইংরেজরা তাঁর প্রতি সদয় হতে পারেনি। মধুসূদনের ভেতরে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা মাইকেল আশাহত হয়েছেন বারবার।
মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে শ্রীহর্ষের সংস্কৃত নাটক ‘রত্নাবলী’র রামনারায়ণ তর্করত্নকৃত বাংলা অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকের দুর্দশা দেখে মাতৃভাষায় নাটক রচনা করে সবাইকে হতবাক করে দিলেন। যে মধুসূদন বাংলা ভাষাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন, তিনি একের পর এক সৃষ্টি করলেন পাশ্চাত্য ধারার প্রথম নাটক ‘শর্ম্মিষ্ঠা নাটক’; ‘পদ্মাবতী নাটক’; সমাজশোধনী প্রহসন- ‘একেই কি বলে সভ্যতা’; ‘বুড়সালিকের ঘাড়ে রোঁ’; বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’; নব্যপ্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম কাব্য- ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’; নবতর ধারার গীতিকাব্য ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’; সার্থক মহাকাব্য ‘মেঘনাদবধ কাব্য’; বাংলা সাহিত্যে প্রথম ও একমাত্র পত্রকাব্য ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’।
কাব্য সাহিত্যের প্রচলিত রীতিকে উপেক্ষা করে প্রবর্তন করলেন নবতর ভাবধারার। একের পর এক সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ হলো বাংলা সাহিত্য। প্রতীচ্যের সঙ্গে প্রাচ্যের সাহিত্যের সংযোগ ঘটিয়ে দিলেন তিনি। আকাশছোঁয়া সম্মান- জনপ্রিয়তা অর্জন করেও থামেনি তাঁর অন্তরাত্মার হাহাকার। তিনি লিখলেন :
“আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,-
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? একি দায়!”
আশাহত মধুসূদন শেষ পর্যন্ত বিলেত গেলেন, নিজের খরচে। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে নিজের সম্পত্তি পত্তনি দিয়ে ব্যারিস্টারি শিক্ষার জন্য তিনি লন্ডনের উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ করলেন। বিদেশবিভুঁইয়ে চরম অর্থকষ্ট, পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম দুরবস্থায় দিন কেটেছে। বিদ্যাসাগরের সহায়তায় প্রাণে বেঁচেছেন। শেষ করেছেন ব্যারিস্টারি শিক্ষা। চরম অসহায় অবস্থার মধ্য দিয়ে একের এর এক বিদেশি ভাষা শিখেছেন, নিজের ভাষা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য। একদা কলকাতায় বসে বাংলা ভাষায় যে চতুর্দ্দশপদী কবিতা বা সনেটের সূচনা ঘটিয়েছিলেন, ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে বসে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটল। তিনি রচনা করলেন শতাধিক সনেট সংবলিত ‘চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী’। সেখানে উদ্ভাসিত হলো তাঁর জন্মভূমি। কবিতায় উঁকি দিল বাংলার মুখ। হ্যাট কোট পরিহিত, পুরোদস্তুর সাহেব বনে যাওয়া মাইকেলের মধ্য থেকে সহাস্যে বেরিয়ে এলো এক খাঁটি বাঙালি মধুসূদন। কবিতাগুলো কতখানি ধুলো-মাটির কাছাকাছি, পুরাণপ্রাণিত, কতখানি বাঙালিত্বে ভরপুর, তা কবিতার কিছু নামকরণের মধ্য দিয়ে প্রকটিত হয়েছে।
যেমন : বঙ্গভাষা, কমলে কামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, জয়দেব, কালিদাস, মেঘদূত, বউ কথা কও, পরিচয়, কবি, দেব-দোল, শ্রীপঞ্চমী, কবিতা, আশ্বিন মাস, নিশা, নিশাকালে নদী-তীরে বট-বৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির, বটবৃক্ষ, সীতাদেবী, মহাভারত, নন্দন-কানন, সরস্বতী, কপোতাক্ষ নদ, ঈশ্বর পাটিনী, বসন্তে একটি পাখির প্রতি, রাশি-চক্র, সুভদ্রা-হরণ, নদী-তীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির, কিরাত-অর্জুনীয়ম, সীতা-বনবাসে, বিজয়া-দশমী, কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা, বীর-রস, গদা-যুদ্ধ, গোগৃহ-রণে, কুরুক্ষেত্রে, শৃঙ্গার-রস, সুভদ্রা, উর্বশী, রৌদ্র-রস, দুঃশাসন, হিড়িম্বা, উদ্যানে পুষ্করিণী, নূতন বৎসর, কেউটিয়া সাপ, ভাষা, পুরারবা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশুপাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সংস্কৃত, রামায়ণ, হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু, ভারত-ভূমি, শকুন্তলা, বাল্মীকি, শ্রীমন্তের টোপর প্রভৃতি। নিজের জীবনের না পাওয়া, আশা-নিরাশার হাহাকার বর্ণিত হয়েছে- যশের মন্দির, সায়ংকাল, সায়ংকালের তারা, কুসুমে কীট, প্রাণ, কল্পনা, পরলোক, শ্মশান, শ্যামা-পক্ষী, দ্বেষ, যশঃ, শনি, সাগরে তরী, তারা, অর্থ, ভূত কাল, আশা, সমাপ্তে প্রভৃতি কবিতায়। পরাধীনতার শৃঙ্খলে জাতির মর্মবেদনা ফুটে উঠেছে ‘আমরা’-এর মতো সনেটে। এই কবিতায় কবির খেদোক্তি উল্লেখযোগ্য :
“আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে?-
আমরা, - দুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে?-”
মধুসূদনের কাব্যে চতুর্দ্দশপদী কবিতার আগেই পরাধীন ভারতের ক্রন্দনধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর অমর সৃষ্টি ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-এ কাব্যে সর্বত্র পরাধীনতার প্রতি ঘৃণা, পরাধীন জাতির প্রতি সমবেদনা, পাশাপাশি পররাজ্যলোভীদের প্রতি সুতীব্র ধিক্কার অনুরণিত হয়েছে। উনিশ শতকের আধুনিক জীবন-চেতনায় ঋদ্ধ মধুসূদন অন্ধকার, পাপাচ্ছন্ন যুগকে অস্বীকার করেছেন নির্দ্বিধায়। জাতির মুক্তি কামনায় উদ্বেলিত কবি পৌরাণিক চরিত্রসমূহে দেশপ্রেম, মানবিকতাবোধ, স্বাজাত্যবোধের দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছেন। দেবতাশ্রয়ীদের থেকে স্বদেশপ্রেমী যোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ফুটে উঠেছে। কবির কাছে শ্রদ্ধেয় তাঁরাই, যারা জন্মভূমির জন্য জীবন দেন, মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনেও মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রাক্ষসজাতি হলেও রাবণ-সম্প্রদায় আক্রান্ত। তাঁদের শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বকে বড় করে দেখেছেন কবি। রাক্ষসদের মানবতাবাদী মানুষের মর্যাদা দান করেছেন। কেননা যারা লোভী, হিংস্র, ষড়যন্ত্রকারী, মিথ্যুক এবং দেবতাদের করুণাপ্রার্থী, তাঁরা মানুষ হলেও নিকৃষ্ট। স্বজাতি-স্বদেশের প্রেম থেকে বিমুক্ত বিভীষণ রাষ্ট্রদ্রোহী। পোশাকি ধর্মের চেয়ে মানবধর্ম যে বড়, উদারচেতা মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে তা দেখিয়েছেন।
স্বদেশপ্রেমের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মধুসূদন তাঁর কাব্যে উপস্থাপন করেছেন, তা বাংলা কাব্যে সর্বপ্রথম এবং অদ্যাবধিও বিরল। স্বদেশপ্রেমের এক অবিনাশী পঙ্ক্তিমালা-
“জন্মভূমি-রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে!”
মধুসূদন রামায়ণের চিরাচরিত বিশ্বাসকে ভেঙেচুরে রচনা করেছেন ‘মেঘনাদবধ কাব্য’। রামায়ণে যে রাম পূজিত, মেঘনাদবধ কাব্যে সে রাম পররাজ্যলোভী তস্কর, ভিখারি রাঘব। আর রামায়ণের চিরঘৃণিত রাবণ মেঘনাদবধ কাব্যে মানবমহিমায় অধিষ্ঠিত। মধুসূদনের সময়ে ধর্ম ছিল, ধার্মিক ছিল; ছিল না ধর্মান্ধতা। ধর্মের প্রচলিত বিশ্বাসে মধুসূদন যে কুঠারাঘাত করেছিলেন, তৎকালীন সমাজ তা নিয়ে খুব বেশি হইচই করেনি। তারা মধুসূদনের এই দুঃসাহসকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। আজকের ভারতের রামরাজত্বে এ ঘটনা ঘটলে, মধুসূদনের কপালে কী দুর্দশাই না ঘটত!
প্রচণ্ড আমিত্বে ভরা, আত্মদম্ভী, জেদি, সংসার জীবনে অবিবেচক, অমিতব্যয়ী এই মধুসূদন না হতে পেরেছেন হিন্দু, না হতে পেরেছেন খ্রিস্টান। কিন্তু যথার্থভাবে হয়ে উঠতে পেরেছিলেন অসাম্প্রদায়িক, একজন দেশপ্রেমিক কবি। ইউরোপ যে সংকীর্ণতাকে পরিহার করে একজন শিক্ষিতজনকে করে তোলে যথার্থ মানুষ; ব্যক্তি মধুসূদনে তার ব্যত্যয় ঘটলেও কবি ও নাট্যকার মধুসূদনে তার ব্যত্যয় ঘটেনি। তিনি মাইকেল হতে পেরেছিলেন বলেই এত বড় কবি হতে পেরেছিলেন। মাইকেল হতে পেরেছিলেন বলেই তিনি অকাতরে বিদেশি সাহিত্য আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন; বিদেশি সাহিত্যের মণি-মুক্তা আহরণ করে সাজাতে পেরেছিলেন স্বদেশের সাহিত্যকে। যারা মধুসূদনকে মাইকেল হিসেবে দেখতে চান না, মধুসূদন যে মনেপ্রাণে হিন্দু ছিলেন এটা যারা প্রমাণ করতে চান, প্রকৃতপক্ষে তারা মধুসূদনকে খণ্ডিত করতে চান। তেমনি যারা মধুসূদনকে শুধু মাইকেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর, তারাও কবির প্রতি সুবিচার করেন না। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম মধুসূদনকে ‘শ্রীমধুসূদন’ বলে অভিহিত করেছিলেন। কবির মৃত্যুর পর তিনি ‘বঙ্গদর্শন’-এ লিখেছিলেন- “কাল প্রসন্ন- ইউরোপ সহায়- সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও- তাহাতে নাম লেখ ‘শ্রীমধুসূদন’।” বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে অবমূল্যায়নই করেছেন। বঙ্কিম কথিত ‘জাতীয় পতাকা’ ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের ‘জাতীয় পতাকা’।
মধুসূদন কখনো হিন্দু জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন দেখেননি। পরবর্তীকালে সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখলেন, তাঁর গ্রন্থ ‘শ্রীমধুসূদন’। এ গ্রন্থে তিনি মধুসূদন যে হিন্দু বাঙালিয়ানাকে ত্যাগ করতে পারেননি, সেটা প্রমাণ করতে অকাট্য যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন যে, মধুসূদন তাঁর ‘সমাধি-লিপি’ কবিতায় লিখেছেন ‘শ্রীমধুসূদন’। কবিতায় মাত্রাগত সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য মধুসূদনকে লিখতে হয়েছিল-
“দাঁড়াও পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!”
মোহিতলাল এটা বুঝতে পারেননি। মধুসূদন নিজের নাম লিখতেন ‘শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত’। ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন, - “মধুসূদন যুগন্ধর, কিন্তু যুগাতিশয়ী শক্তির অধিকারী। এই শক্তির উৎস নিশ্চয়ই কেবল যুগের সত্যে নয়, ব্যক্তির সত্যেও।” এই উক্তিকে সামনে রেখে বলতে চাই, মধুসূদন ও মাইকেল এই দ্বৈত সত্তার ব্যক্তিসত্য- শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অর্থহীন হয়ে ওঠে। মধুসূদন শেষ জীবনে এসে লিখলেন কিছু নীতিগর্ভ কবিতা, নাটক- ‘মায়া-কানন’। অনুবাদ করলেন হোমারের ‘ইলিয়ড’ কাব্য- ‘হেক্টর-বধ’। রেখে গেলেন অনেকগুলো অসম্পূর্ণ কাব্য, নাটক। এসবই তাঁর মধুসূদন থেকে মাইকেল হয়ে ওঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।