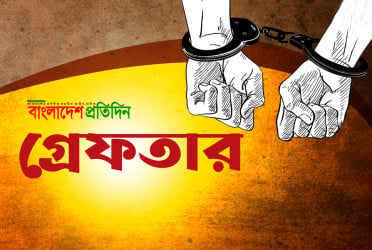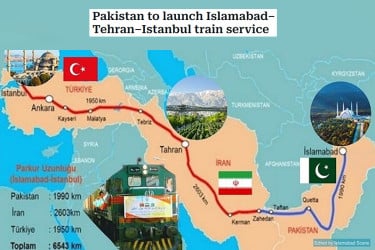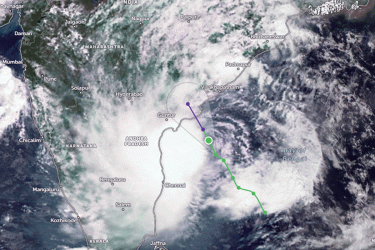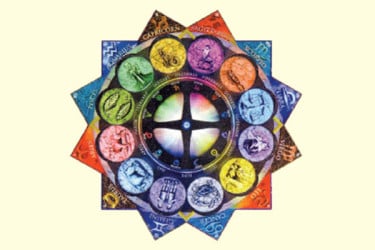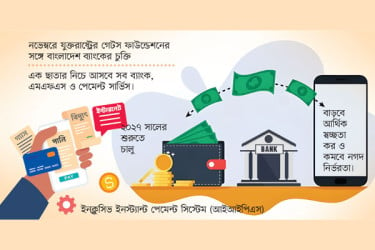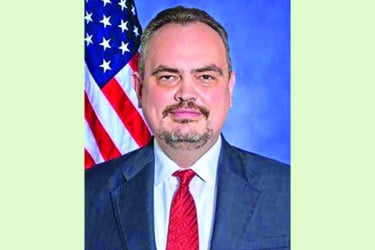দেশের চিকিৎসাসেবার মানোন্নয়ন এবং রোগীদের বিদেশ যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা কমাতে নানামুখী উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। ক্যানসার, কিডনি, বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট, হৃদ্রোগের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিতে বিশ্বমানের সেবা দেওয়ার পরিকল্পনায় সরকারের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে এগোচ্ছে বেসরকারি হাসপাতাল। হাসপাতালের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সেবার মান নিশ্চিতে তদারকি জোরদারের পরামর্শ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।
এ ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান বলেন, ‘চিকিৎসাব্যবস্থার মানোন্নয়নে ব্রিটিশ স্বাস্থ্য প্রশাসনের আদলে দেশের স্বাস্থ্য প্রশাসন সাজানো হচ্ছে। এ লক্ষ্যে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে ব্রিটিশ এমএইচআরএর (মেডিসিন্স অ্যান্ড হেলথকেয়ার প্রোডাক্টস রেগুলেটরি এজেন্সি) আদলে পরিবর্তন করা হবে। এ ছাড়া এনএইচএস (ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস) এবং এনআইসিইর (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ অ্যান্ড কেয়ার এক্সিলেন্স) আদলে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘বর্তমান সরকার দেশের স্বাস্থ্যসেবায় আমূল পরিবর্তনে সব ধরনের চেষ্টা করছে। ওষুধের অত্যাবশ্যকীয় তালিকা প্রণয়নের পাশাপাশি রোগীদের জরুরি পরীক্ষানিরীক্ষার তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। তালিকা করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞরা ঢাকায় অবস্থান করছেন। রোগ নির্ণয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা, যৌক্তিকতা ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করা হবে। এগুলো বাস্তবায়ন হলে দেশের সাধারণ মানুষের পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যয় নিয়ে ক্ষোভ প্রশমিত হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েব পেজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সনির্ভর করা হচ্ছে। যেখানে প্রতি সপ্তাহে একটি বিষয়ে জনসাধারণের মতামত চাওয়া হবে এবং মতামতের ভিত্তিতে সরকার পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করবে।’
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, রোগীর সংখ্যা বাড়ায় পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। কিন্তু এর অনেকটিই মানসম্মত নয়। একদিকে যেমন পাঁচ তারকাবিশিষ্ট বিলাসবহুল হাসপাতাল রয়েছে, তেমনই রয়েছে মেয়াদোত্তীর্ণ নিম্নমানের ক্লিনিক। দেশে সরকারি হাসপাতাল রয়েছে ৬৫৪টি। এ ছাড়া সরকারি সহযোগিতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আরও ২ হাজার ২৭৭টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র রয়েছে। এসব হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে শয্যা রয়েছে প্রায় ৭২ হাজার। প্রায় সাড়ে ৫ হাজার বেসরকারি হাসপাতালে ১ লাখ ১০ হাজার শয্যা রয়েছে। এর বাইরে সারা দেশে নিবন্ধিত বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টার আছে ১০ হাজার ৭২৭টি ও ব্লাডব্যাংক আছে ১৪০টি। তবে বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিকে চিকিৎসার মান নিয়ে এখনো রয়েছে নানান অভিযোগ। কিডনি, লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টের মতো জরুরি চিকিৎসায় রয়েছে আইনি জটিলতা। ক্যানসার চিকিৎসায় এখনো রয়েছে প্রযুক্তি এবং দক্ষ জনবলের সংকট। স্বাস্থ্যবিমা না থাকায় চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে অসহায় অবস্থায় পড়তে হচ্ছে মানুষকে।
স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্টরা বলেন, সরকারি হাসপাতালে রোগীর চাপ বেশি। সেবা নিতে বেশ সময় লাগে। কিন্তু বেসরকারি হাসপাতালে গেলেই স্বাস্থ্যসেবা মেলে। এসব ঝামেলা এড়াতে কষ্ট হলেও টাকার বিনিময়ে দ্রুত স্বাস্থ্যসেবা পেতে বেসরকারি হাসপাতালে যাচ্ছে রোগীরা। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার পাশাপাশি তাদের অবকাঠামোগত উন্নতি ও ব্যবস্থাপনায়ও মানুষ প্রভাবিত হয়। সরকারি হাসপাতালে ভালো চিকিৎসকরা সেবা দিচ্ছেন। কিন্তু সেখানকার বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা ও সুযোগসুবিধা মানুষকে টানতে পারছে না। সরকারি হাসপাতালে রোগীর অনুপাতে চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক, টেকনোলজিস্টের সংখ্যাও কম। এসব কারণেই বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার প্রতি মানুষ বেশি ঝুঁকছে। স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আবদুল হামিদ বলেন, ‘বাংলাদেশে বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো দেশের ক্রমবর্ধমান চিকিৎসা চাহিদা পূরণে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। গ্রাম থেকে শহরে সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি একটি শক্তিশালী সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। তবে এ খাতের সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং নৈতিক মান নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যা এটিকে জর্জরিত করে রেখেছে। অনিয়ম, অতিরিক্ত মুনাফার লোভ, দালালনির্ভরতা এবং রোগীদের প্রতি অবহেলার মতো ঘটনা প্রায়ই শিরোনামে উঠে আসে। এ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে জনস্বার্থের সঙ্গে সমন্বয় করতে সরকারকে একটি বিস্তৃত, সুচিন্তিত এবং সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘গুণগত মান নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ হেলথ কমিশন (বিএইচসি) বা একটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রেডিং পদ্ধতির আওতায় আনতে হবে। এ গ্রেড নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন মানদণ্ড বিবেচনা করা যেতে পারে। ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর ক্ষেত্রে পরীক্ষার নির্ভুলতা, যন্ত্রপাতির সুরক্ষা এবং রিপোর্টিংয়ের মান বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।’
স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের সাবেক পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. নুরুল আমিনের ‘রোগীর নিজ পকেট থেকে চিকিৎসার জন্য উচ্চ ব্যয়ের নেপথ্যের কারণ অনুসন্ধান’ শীর্ষক গবেষণায় সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে সেবাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য উঠে এসেছে। তাঁর গবেষণায় দেখা যায়, সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা খরচ কম। কিন্তু মাত্র ১৪ দশমিক ৪১ শতাংশ মানুষ সরকারি প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা নিতে যায়। ৮৫ দশমিক ১ শতাংশ পরীক্ষানিরীক্ষাই রোগীকে করতে হয় বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। চিকিৎসাসেবায় বড় অবদান রেখে চলেছে বেসরকারি খাত। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তিন ধরনের। ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসায়িক হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার। বেসরকারি দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং দেশি বা বিদেশি এনজিওচালিত প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানই বেশি। চিকিৎসার পাশাপাশি মেডিকেল শিক্ষায়ও তারা বড় ভূমিকা রাখছে। এখন সরকারি মেডিকেল কলেজ যত রয়েছে, তার দ্বিগুণ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ।
বাংলাদেশ প্রাইভেট হসপিটাল, ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এবং ল্যাবএইড হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এম শামীম বলেন, ‘দেশে ৬০-৭০ ভাগ সেবা আমরাই দিই। তাই আমাদের সঙ্গে নিয়েই কাজ করতে হবে। সরকার আমাদের সুবিধা দিলে অনেক ক্ষেত্রে আমরাই যথেষ্ট। সরকার অডিট করুক, সবাইকে এক কাঠামোয় আনুক।’
জানা যায়, উন্নত বিশ্বের প্রায় সব আধুনিক চিকিৎসাসেবা বাংলাদেশে রয়েছে। হৃদ্রোগ চিকিৎসায় বাংলাদেশ এখন গর্ব করে। একসময় একটা এনজিওগ্রাম করার জন্য রোগীকে বিদেশে যেতে হতো। ভারতে গিয়ে এনজিওগ্রাম করাতে ভিড় করত বাংলাদেশের রোগীরা। বর্তমানে দেশে ৫০টির বেশি কার্ডিয়াক সেন্টার রয়েছে। প্রতি বছর কয়েক লাখ রোগী হৃদ্রোগের উন্নত ও সর্বাধুনিক চিকিৎসা দেশেই পাচ্ছে। গত এক যুগে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে যুগান্তকারী উন্নতি হয়েছে। সরকারি হাসপাতাল স্থাপন, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ, রোগ নির্ণয়কারী প্রতিষ্ঠান ও আধুনিক হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. আশীষ কুমার চক্রবর্ত্তী বলেন, ‘দেশে স্বাস্থ্যবিমা চালু থাকলে মানুষ দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করতে গেলে অধিকাংশ টাকা সেখান থেকে পাবে। ফলে চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে গিয়ে কোনো পরিবারকে আর পথে বসতে হবে না।’ তাই দেশে অবিলম্বে এ ব্যবস্থা চালু করার জোর দাবি করেন তিনি।