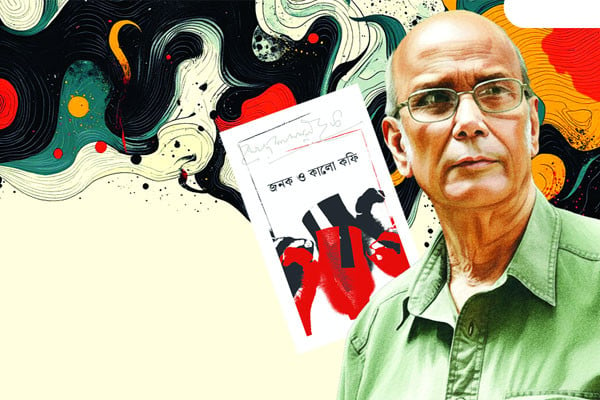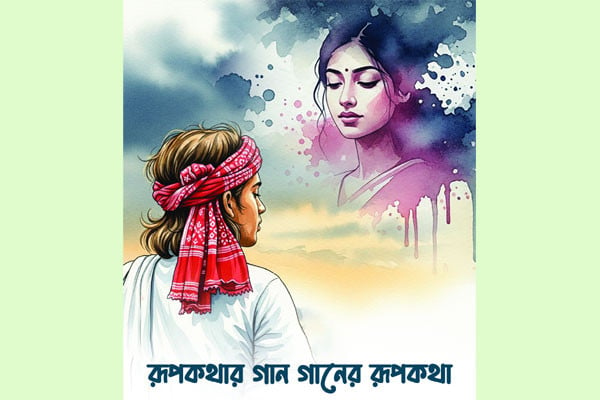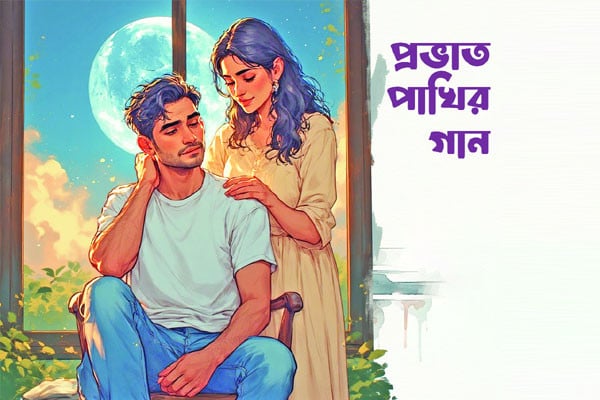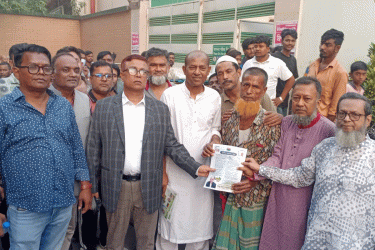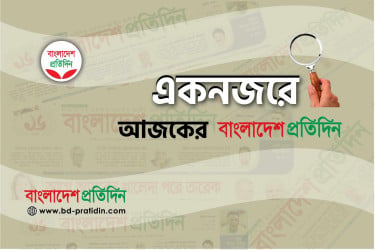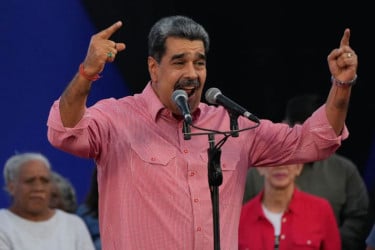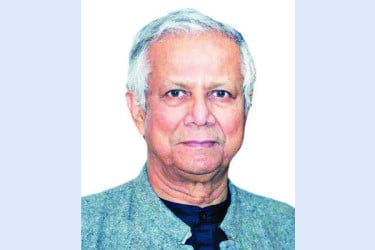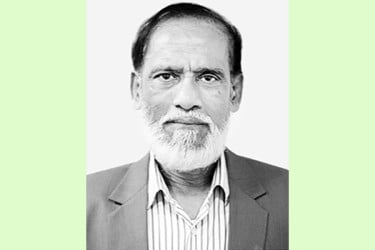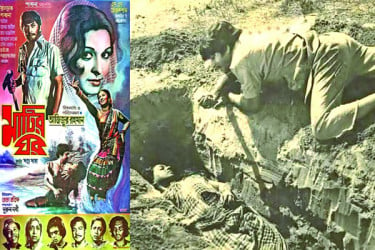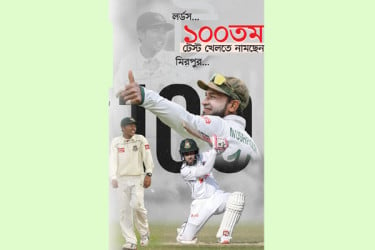সৈয়দ শামসুল হক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি এবং প্রাগ্রসর লেখক। ছয় দশকের অধিককাল ধরে তিনি বিচিত্র বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সায়েন্স ফিকশন, শিশুতোষ রচনা, চলচ্চিত্রের কাহিনি, গান, আত্মজৈবনিক রচনা, অনুবাদ ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ
বিভাগোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে দেশভাগের যন্ত্রণা, ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ, আবহমান বাংলার সমাজ মানস, ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিক্ষুব্ধ জনজীবন ও ব্যক্তির ভাঙাগড়া লেখকদের কলমে মুখ্য হয়ে উঠেছে। সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) সমকালীন জীবন-বাস্তবতা, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম ও লোকসংস্কৃতির আড়ালে মানুষের অন্তরাত্মা বা ব্যক্তিমানসকে রূপায়িত করেছেন বিভিন্ন ঢঙে। তাঁর অঙ্কিত চরিত্রের পাত্রপাত্রীরা সাধারণের প্রতীক হয়ে আমাদের সামনে প্রতিবিম্বিত হয়। সৈয়দ হকের কথাসাহিত্যে গ্রাম ও নগরজীবন, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবর্গ মানস, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ’৭১-র মুক্তিযুদ্ধ এবং আরও বৈচিত্র্যময় বিষয় চিত্রিত হয়েছে।
সৈয়দ শামসুল হক ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি এবং একজন প্রাগ্রসর লেখক। ছয় দশকের অধিককাল তিনি বাংলা ভাষায় বিচিত্র বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর রচিত কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সায়েন্স ফিকশন, শিশুতোষ রচনা, চলচ্চিত্রের কাহিনি, গান, আত্মজৈবনিক রচনা, অনুবাদ ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে আমৃত্যু তিনি ছিলেন গণমানুষের কণ্ঠস্বর। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই শিল্পীর নানারৈখিক সৃজনশীল কাজ সমকালে বিরল ও বিস্ময়। শিল্প-সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় উচ্চমার্গের সৃজনপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখে তিনি বাংলা ভাষার পাঠক মহলে ‘সব্যসাচী’ লেখক অভিধায় অভিষিক্ত হয়েছেন।
১৯৪৭-এর দেশভাগের পর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে জটিল ও দ্বন্দ্বময় পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, সমাজের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের-মনে তার প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের নিরেট বাস্তবতা, আবেগ ও প্রেমের অন্তঃসারশূন্যতা, মূল্যবোধের ভাঙন, নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রথাগত বৈশিষ্ট্যে অবিশ্বাস-এ সময়ে বাঙালি জীবনের অনিবার্য উপাদানে পরিণত হয়। বাঙালি জনজীবনের এই নির্মমতাকে নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করার মতো অনেক কথাশিল্পী ষাট ও সত্তরের দশক থেকেই বাংলাদেশের সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা ষাটের দশক থেকে শুরু করে আমৃত্যু বাংলা সাহিত্যে দ্যুতি ছড়িয়েছেন। কেউ কেউ এখনো লেখার মাধ্যমে আলো ছড়াচ্ছেন। একদিকে সামরিক শাসনের নিষ্পেষণে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে পুঁজিবাদের বিকৃত বিকাশ, অন্যদিকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত বাঙালি জাতি। ফলে সমাজ ও রাজনীতিতে তখন অশান্ত পরিবেশ বিরাজ করছিল। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বাংলার রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ’৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি আত্ম-উন্মোচন করতে সক্ষম হয়। আর একাত্তরের রক্তাক্ত মুক্তির সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা পাই স্বাধীন-সার্বভৌম একটি দেশ; বাংলাদেশ। তাই শিল্প-সাহিত্যেও ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়।
আমাদের অন্বিষ্ট লেখক সৈয়দ শামসুল হকের জনক ও কালোকফি (১৯৬৩) উপন্যাস অবলম্বনে নিম্নবর্গ মানুষের স্বরূপ উন্মোচন করা।
যে সব মানুষ আবহমান সমাজে ও সভ্যতায় পেছনের সারিতে অবস্থান করছে তারাই ‘নিম্নবর্গ’। এই পর্যায়ের মানুষের চিহ্নিতকরণ, স্বরূপ-সন্ধান ও পরিচয় দান প্রসঙ্গে বিভিন্ন চিন্তাবিদ, দার্শনিক নানা রকম পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। আমাদের বিচারে ব্রাত্য, অন্ত্যজ, সর্বহারা, প্রলেতারিয়েত ও সাবঅলটার্ন শব্দগুলোর সম্মিলিত প্রতীতিজাত বিস্তৃত যে অর্থ তা-ই নিম্নবর্গ।
এরই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্গের ভিত্তি গড়ে ওঠে আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মানদণ্ডের ওপর ভর করে। সেখানে বর্গ, শ্রেণি, বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স, অর্থ, সমাজনীতি কিংবা অন্য যে কোনো বিচারেই সমাজস্তরে অবনীয়মান, মর্যাদাহীন মানুষই নিম্নবর্গ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দরিদ্র চাষি, শ্রমিক, খেতমজুর, আদিবাসী, নারী, নিম্ন জাতি-বর্ণের মানুষ, গৃহভৃত্য, নিরক্ষর ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, অভিবাসী, শিশু এবং প্রান্তিক ক্ষমতাহীন মানুষকে নিম্নবর্গ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন গবেষকরা।
সাহিত্যের বিবিধ শাখা-প্রশাখার মধ্যে উপন্যাস সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও জীবনঘনিষ্ঠ। সৈয়দ শামসুল হক বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অতিপরিচিত এবং জনপ্রিয় একটি নাম। এ দেশের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনের বহুমুখী সংকট তিনি কথাসাহিত্যে শিল্পসফলভাবে উপস্থাপন করছেন। মানুষের সার্বিক জীবনপ্রবণতা কিংবা যা আপাতভাবে সমাজে অপ্রচলিত অথচ জীবনের অনিবার্য অংশকে তিনি গল্প অথবা উপন্যাসের বিষয় করে তুলেছেন। ‘জনক ও কালোকফি’ বিভাগোত্তর সময়ে লেখা সৈয়দ শামসুল হকের একটি অনবদ্য সামাজিক উপন্যাস। সমাজের সাধারণ মানুষের জীবন এবং তাদের বেঁচে থাকার বিবিধ সংগ্রাম এ উপন্যাসের উপজীব্য।
স্বাধীনতা-পূর্বে বাংলার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে মুশতাক নামের এক শিক্ষিত যুবকের স্বপ্ন ও সংগ্রামের চিত্র এ উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে। নিশাত নামের একটি মেয়েকে তার ভালো লাগত, এই ভালোলাগা থেকেই ভালোবাসা। কিন্তু ছন্নছাড়া জীবনের সঙ্গে নিশাতকে জড়ানোর সৎ সাহস মুশতাকের ছিল না। সে ঢাকা জজ কোর্টের সিনিয়র উকিল কাজী সাহেবের অধীনে মাসকাবারি চারশ টাকা বেতনের একজন জুনিয়র সহকারী হিসেবে কাজ করত। মুশতাকের বাবা-মা নেই। মাত্র চার বছর বয়সে সে বাবাকে হারিয়েছিল। স্বামী বিয়োগের পর তার মা তাকে নিয়ে থাকেনি- মুশতাককে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে নতুন করে আবার সংসার পেতেছে। মুশতাক চাচা-চাচির কাছে মানুষ। কিন্তু এম এ পাস করেও উপযুক্ত চাকরি জোগাড় করতে না পারায় চাচা-চাচিও একসময় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পথের মানুষের মতো সবাই তাকে পর করে দিয়েছে। সহায়-সম্পদ, আত্মীয়-পরিজনহীন যুবক মুশতাককে নিম্নবর্গ চরিত্র হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সবাই মুশতাককে দূরে ঠেলে দিলে শুরু হয় তার জীবন-সংগ্রামের দ্বিতীয় ধাপ। একদিকে দারিদ্র্র্যের গ্রাস, অন্যদিকে অস্তিত্ব সংকটের প্রবল দোলাচালে মুশতাক শেষ পর্যন্ত নিশাতকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিয়ের খবর মাকে দিয়ে আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য ছাব্বিশ বছর পর সে মায়ের মুখোমুখি দাঁড়ায়। মায়ের দ্বিতীয় সংসারে গিয়ে নাটকীয়ভাবে সে নিজেকে আবিষ্কার করে বাবার খুনি হিসেবে। তখন থেকে পাল্টে যায় তার নৈমিত্তিক জীবন। বদলে যায় জীবনের রং। তাস, জুয়া, মদ আর মেয়ে মানুষের নেশায় আকৃষ্ট মুশতাক কেবল নিশাতকে ভুলে থাকার জন্য জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ায়। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক লিখেছেন :
সেদিন রেস্তোরাঁয় আমি বসেছিলাম সোয়া পাঁচটায়। সাতটায় দেখা করবার সময় ছিল নিশাতের সঙ্গে। কিন্তু তার আগে ঘটল অঘটন, আমার চশমার কাচ আচ্ছন্ন হয়ে গেল কালোকফির ধোঁয়ায় এবং আমি বিকৃত হতে লাগলাম হত্যাকারী হিসেবে।
‘জনক ও কালোকফি’ উপন্যাসের খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি চরিত্র রয়েছে-তারা হলেন, মুশতাকের বন্ধু জালাল ও তার স্ত্রী। মুশতাকের ভবঘুরে জীবনের সঙ্গী ছিল জালাল। একই বাসায় পাশাপাশি রুম ভাগাভাগি করে তারা বসবাস করত। জালাল ও তার স্ত্রী এ উপন্যাসের আরও দুটি নিম্নবর্গ চরিত্র। তারা মুশতাককে ভালোবাসত। তাই তারা তাকে পরিবারের সদস্য হিসেবে ঠাঁই দিয়েছিল। কিন্তু জীবন বাস্তবতার রূঢ় প্রতিঘাতে মুশতাক বন্ধু জালাল ও তার পরিবারের প্রতি যোগ্য প্রতিদান দিতে পারেনি। বরং লিবিডো তাড়নায় জারিত হলে বিশ্রীভাবে সেখান থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। মুশতাকের খামখেয়ালিপনায় একসময় তাদের বন্ধুত্বের চিড় ধরে। পিতার মৃত্যুর ছাব্বিশ বছর পর অন্যত্র বিবাহিত মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সে এক বিরাট সত্য আবিষ্কার করে। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা পিতাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দিয়েছিল মুশতাক। সে মানুষটা সাঁতার জানত না। তীব্র স্রোতের টানে অকূলে হারিয়ে যাওয়া বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী মুশতাক। তখন সে নতুন এক জীবনের সন্ধান পায়। তিন বছর বয়সের সেই অপরাধ মুশতাককে এখন কুরে কুরে খায়। তারপর থেকে মুশতাক আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে না।
জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানো মুশতাক তখন; পিতৃহত্যার দায় স্বরূপ নিজেকেও ভাসিয়ে দেয় অজানা অন্ধকারে। কথা দিয়ে প্রথমবার নিশাতের সঙ্গে দেখা না করে ধীরে ধীরে সে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। বেখেয়ালে আগের জমানো ৪ হাজার টাকা থেকে পাঁচশ’ টাকা দিয়ে নিশাতের জন্য কেনা পারফিউম সেন্ট, শাড়ি, চপ্পল- এসব বন্ধু জালালের স্ত্রীকে দিতে গেলে বন্ধুর সঙ্গে মুশতাকের সম্পর্কের অবনতি হয়। ফলে সাবলেট বাসা ছেড়ে দিতে হয় তাকে। তারপর থেকেই সে ভবঘুরে জীবনের দিকে ধাবিত হয়। তিন বছর বয়সের ছেলেকে চাচাদের কাছে রেখে দারিদ্র্যের কথা বলে মায়ের খোরশেদ সাহেবের সঙ্গে দ্বিতীয় পরিণয় যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি মুশতাক। তাই ছাব্বিশ বছরের মধ্যে সে একবারও মায়ের সন্ধান করেনি। মা-ও তার নিজের সন্তানের কোনো খোঁজখবর রাখেনি। মায়ের প্রতি জমে থাকা অভিমান একটু একটু করে ক্ষোভে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বিয়ের মতো এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর মুশতাক তার মাকে বিষয়টি জানানো দরকার মনে করে। দীর্ঘদিনের অসাক্ষাতে মাকে মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেও বিয়ের ব্যাপারে মায়ের উপস্থিতি ও আশীর্বাদ তার কাছে অনিবার্য হয়ে পড়ে। বহু বছর পর মাকে এক নজর দেখার জন্য সে ঢাকা থেকে দূরবর্তী গ্রাম; মায়ের দ্বিতীয় স্বামী খোরশেদ সাহেবের বাড়িতে উপস্থিত হয়। খোরশেদ সাহেব মুশতাকের সঙ্গে সহজভাবেই কথা বলেন। কিন্তু মনে মনে তিনি মুশতাককে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন না।
খোরশেদ সাহেব গ্রামের একজন নিম্নবিত্ত মানুষ। অভাব তার নিত্যসঙ্গী। সংসারে আগের পক্ষের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর; তিনি মুশতাকের মাকে বিয়ে করেছেন। তাই দীর্ঘসময় পর প্রথমবার মুশতাক এ বাড়িতে এলেও তাকে খোরশেদ সাহেবের কাছে বোঝা বলে মনে হয়। খোরশেদ সাহেবের ধারণা মুশতাক হয়তো টাকা-পয়সার জন্য মায়ের কাছে এসেছে।
মুশতাক ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে পরের সংসারে মায়ের সীমাবদ্ধতা। নিজের সন্তানকে কাছ থেকে দেখার অধিকার যে এখন অন্যের হাতে। ছাব্বিশ বছর পর প্রথম দেখায় মায়ের অনুভূতিহীন অন্তঃসারশূন্যতা; মাতৃস্নেহের কাঙাল মুশতাককে যেমন দগ্ধ করে, তেমনি মাকেও তার আরও দূরের অপরিচিত কেউ মনে হয়। কিন্তু জীবন বাস্তবতার নিরিখে ধোঁয়াশা ক্রমেই কাটতে থাকে। শীতের গভীর অন্ধকার রাতে সন্তানের সঙ্গে মায়ের দেখা হয়। চোর যেমন চুরি করতে আসে চুপিচুপি, মাকেও তেমনি আসতে হয় অপত্য স্নেহ বিনিময় করতে। মা চোরের মতো লুকিয়ে ঘরে ঢুকে সন্তানকে জিজ্ঞাসা করে, ‘গ্যাদা আইছস ক্যান? টাকা-পয়সা দরকার? কয় টাকা? ফিরোজার বাপ কত রাগ কইরল। কয়, ছাওয়াল আইছে ক্যান? কী চায় তারে জিজ্ঞাস করো নাই? পরের সংসারে আগের পক্ষের সন্তানের সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতে আসার মধ্যে সমকালীন নারীদের সামাজিক অবস্থা ফুটে উঠেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পরের বাড়িতে মেয়েরা বড্ড অসহায়। মায়ের আবেগ, বুকফাটা কান্না মুশতাকের মাতৃহীন জীবনের কাছে মেকি বলে মনে হলেও- সমাজ বাস্তবতার নিরিখে এটাই চরম সত্য। কিন্তু সন্তান হিসেবে মুশতাক মায়ের কাছে অপত্য স্নেহ প্রত্যাশা করে। অপার্থিব, অকৃত্রিম ভালোবাসা দাবি করে। মায়ের পক্ষ থেকে যা সন্তানের জন্য আর কোনোভাবেই পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই রাতের আঁধারে মাকে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে সন্তানের কাছে আসতে হয়। মুশতাক মায়ের এই পালিয়ে দেখা করতে আসাকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে না। ফলে মায়ের বুকফাটা আর্তনাদ খেদোক্তি আকারে প্রকাশ পায় আর তখনই উন্মোচিত হয় মুশতাকের জীবনের নিষ্ঠুর সত্য।
মুশতাক যখন উপলব্ধি করে তিন বছর বয়সের সেই অপরাধের জন্য তার এবং মায়ের জীবন এমন তছনছ হয়ে গেছে। তখন থেকেই সে প্রায়শ্চিত্তের পথ বেছে নেয়। নিজের মধ্যে পিতৃহত্যার দায় এবং অপরাধবোধ তাকে সারাক্ষণ তাড়া করে বেড়ায়। জীবন থেকে পালিয়ে সে কেবলই ছুটতে থাকে অজানার উদ্দেশে। বন্ধু জালালের ভাড়া করা বাড়ি, কাজী সাহেবের চেম্বার- সব ছেড়েছুড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসে সে। মুশতাক তখন ঠিকানাবিহীন এক ছিন্নমূল মানুষ। পরিচিত সবার কাছ থেকে; এমনকি প্রেমিকা নিশাতের কাছ থেকেও সে নিজেকে আড়াল করে রাখে। বহুদিনের পুরোনো বন্ধুদের খোঁজে ফিরে যায় ফরাশগঞ্জের গোবিন্দর চায়ের দোকানে।
ফরাশগঞ্জের চায়ের দোকানে ঢুকে মুশতাক মানুষের জীবনের নয়া অধ্যায় আবিষ্কার করে। সংসার-সমরে হেরে যাওয়া মানুষগুলো এখানে এসে ধ্বংসাত্মক জীবনের সমারোহ রচনা করতে ব্যস্ত। ভিতরে যেতেই দেখা হয়ে যায় অনেক দিনের পরিচিত লোকমান, আসাদসহ আরও কয়েকজনের সঙ্গে। তিন বছর পর সবার সঙ্গে দেখা হলে মুশতাক জমিয়ে আড্ডা দেয়। এই প্রথম বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মুশতাক মদ খায়। খাওয়াদাওয়া শেষে সবাই একসঙ্গে বের হয়। এরপর থেকে প্রত্যহ সারা রাত ফ্লাস খেলে, মদ খেয়ে, হইচই করে কাটিয়ে দিনভর ঘুমানো যেন মুশতাকের রুটিনে পরিণত হয়। ব্যাংকে গচ্ছিত চার হাজার টাকা; যা দিয়ে মুশতাক একসময় নিশাতকে বিয়ে করে সংসার সাজাতে চেয়েছিল; সব ব্যয় করে জুয়া, মদ আর মেয়েমানুষের পিছনে। নিশাতের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়ার পর মুশতাক এক নতুন সত্যের সন্ধান পায়। লেখকের ভাষায় : ‘আজ আমার সাফল্যে এই ধারণা হয়েছে, মানুষ আবিষ্কার করতে পারে মহাদেশ, পর্বত, নক্ষত্র। জয় করতে পারে যুদ্ধ; সৃষ্টি করতে পারে সংগীত; কিন্তু যা চিরচেনা এবং অজেয়- তা নিজের মন।’
উপন্যাসে কালো কফির প্রসঙ্গটি বিশেষ অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মুশতাকের ব্যক্তিজীবন, বিবেকবোধ; কালো কফির ধোঁয়া আর চশমার কাচের লুকোচুরি খেলার মধ্যে অনবদ্য হয়ে উঠছে। লেখক কালো কফির সঙ্গে মুশতাকের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার চমৎকার মিল-বিন্যাস রচনা করেছেন। ঔপন্যাসিকের ভাষায়, কফির ধোঁয়ায় চশমার কাচ যখন কুয়াশা হয়ে গেল, তখন ইন্দ্রাজালে অবচেতনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে গেল। ছড়িয়ে ছিটকে পড়ল আমার গ্লানি, আমার পাপ, আমার ক্ষমাহীন অস্তিত্ব। আমার কাছে লুপ্ত হলো আশা, বাস্তব এবং বর্তমান, দুলে উঠল অতীতের ভারী পর্দা- যা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল আমার স্মৃতিকে।
সৈয়দ শামসুল হক মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব বাংলাদেশের ঢাকা অঞ্চলে বসবাসকারী মুশতাককে নাগরিক নিম্নবিত্ত শ্রেণিচরিত্র হিসেবে সার্থক করে তুলেছেন। উপন্যাসে তৎকালীন জনজীবন ও ঢাকার চালচিত্র ফুটে উঠেছে। সে সময় মানুষ রিকশা, টেম্পো, স্কুটার যাতায়াতের বাহন হিসেবে ব্যবহার করত। লোকাল বাসের কথাও উপন্যাসে বলা হয়েছে। দূরের রাস্তায় ট্রেনে মানুষ যাতায়াত করত। তখন বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে ছিল সপ্তাহান্তে সিনেমা দেখা। পথে সিনেমার পোস্টার লাগানো থাকত। তবে খেটে খাওয়া নিম্নবর্গের মানুষের জীবন চিরকালই ছিল কষ্টের। উপন্যাসে ভাষার ব্যবহারে লেখক অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।
আগামীকাল এই সব্যসাচী লেখকের নবম মৃত্যুবার্ষিকী। এ উপলক্ষে তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।