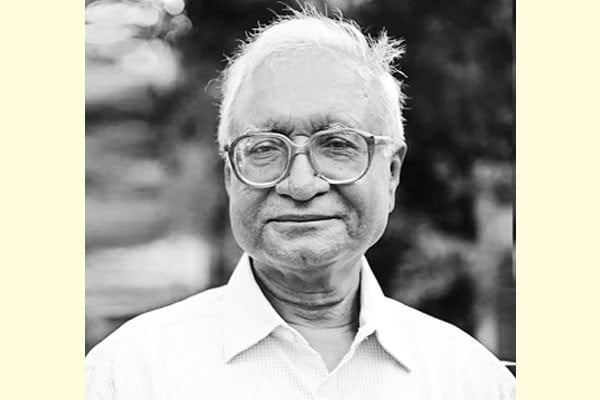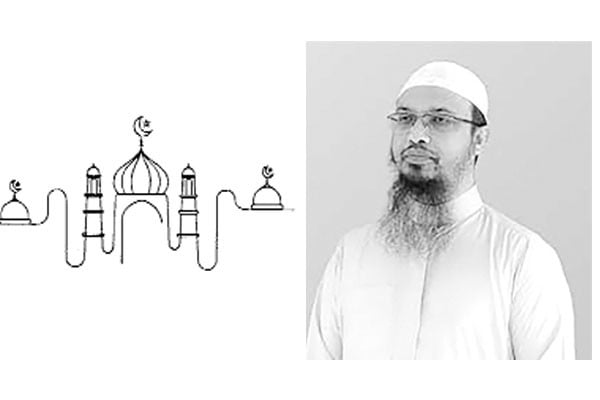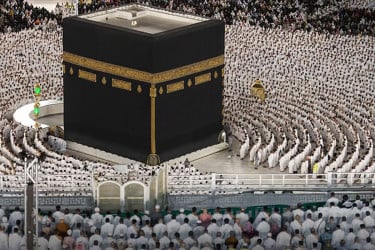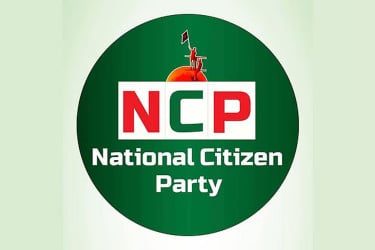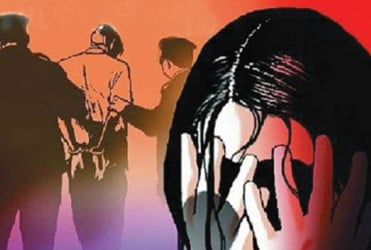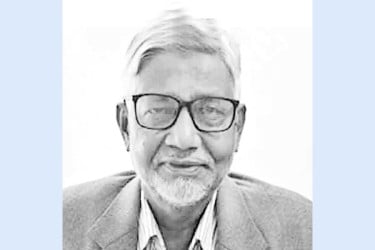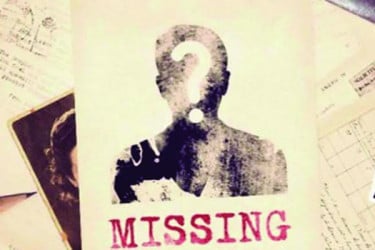বাংলাদেশে ক্ষমতার প্রশ্নে বিত্তবানদের সঙ্গে বিত্তহীন কৃষকদের বিভাজনটি খাড়াখাড়ি। বিভাজন আরও রয়েছে, যেগুলো আড়াআড়ি। এদের একটি হচ্ছে নারী-পুরুষে পার্থক্য। আমরা মায়ের কথা খুব করে বলি, মাতৃভাষা, মায়ের মর্যাদা, মাতৃভূমি, এসব ধ্বনি ও বোধ আমাদের উদ্বেলিত করে থাকে। কিন্তু নারীর হাতে ক্ষমতা নেই, সমাজ পুরোপুরি পুরুষতান্ত্রিক, কেবল পুরুষতান্ত্রিক নয়, পিতৃতান্ত্রিকও বটে। যে কারণে নানা ক্ষেত্রে পিতানুন্ধান চলতে থাকে, মাতার খোঁজ নেই। বিদুষী এক মহিলা, নিজেকে যিনি মোটামুটি নারীবাদী বলেই জেনে এসেছেন এতকাল, সেদিন প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়েছেন, জানালেন আমাকে। ঘুমের মধ্যে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন। সেই স্বপ্নের সবটাই তার পিতাকে নিয়ে, মা একবারও আসেননি, উঁকি পর্যন্ত দেননি। এসব ক্ষেত্রে স্বপ্ন অনেক বেশি বাস্তব, বাস্তবের তুলনায়। স্বপ্নে ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণ নেই। জীবনে যা সত্য, স্বপ্নেও তাই প্রতিফলিত হয়েছে, পূর্ণ মাত্রাতে। আমি নিজেও দেখি একটি বই লিখেছি ‘আমার মাতার মুখ’ বিষয়ে অথচ আমার মাতার মুখের আলোছায়া অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও হৃদয়স্পর্শী ছিল পিতার মুখের কুঞ্চন-প্রশান্তির চেয়ে। আয়টা পিতারই, কিন্তু সেই আয় প্রচুর নয়, সামান্যই। তা দিয়ে সংসার চালানো, অতিথি আপ্যায়ন, সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষা- এসব দায়িত্ব পালনে অত্যাশ্চর্য দক্ষতা ও ধৈর্য মাতা দেখিয়েছেন। তিনি সবাইকে খাইয়েছেন, তিনি নিজে কী খাচ্ছেন তার খবর কেউ করেনি। নিজেও করতে পারেননি। নিজের ব্যাপারে সহনশীলতা এবং অপরের ব্যাপারে বিবেচনা ও সংবেদনশীলতার কোনো শিক্ষা যদি আমি পেয়ে থাকি, তা তো আমার মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছি। কিন্তু এটা তো কেবল আমার একার ব্যাপার নয়। অধিকাংশেরই অভিজ্ঞতা। বোঝা যাবে খবর নিলে। কিন্তু খবরটা নেবে কে? বাঙালি সমাজে বীরপুরুষ পুত্র সন্তানেরা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টায় যেভাবে মাকে জড়িয়ে গাল পাড়ে, তাতে মাতার সম্মান সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করার কোনো কারণই নেই।
মুক্তিযুদ্ধে মেয়েরা সরাসরি লড়তে পারেনি এটা ঠিক। কিন্তু ওই যুদ্ধের ঝড়ঝাপটা তাদের ওপর দিয়েই গেছে সর্বাধিক। সে ইতিহাস কেউ লেখেনি। কোনো দিন লিখবেও না। কেননা ইতোমধ্যে তার অধিকাংশই হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অন্ধকারে। কে দেয় তার মূল্য? মূল্যই যদি দেওয়া হবে, তাহলে আমাদের এত বেশি দুর্দশা কেন? নারীকে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার ফল নানাদিকে বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। সেই যে রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন মাতাকে উদ্দেশ করে, সন্তানকে তিনি বাঙালি করেছেন ঠিকই তবে মানুষ করেননি, সেই অভিযোগ যে পরিমাণে সত্য, ঠিক সেই পরিমাণেই এটাও সত্যি যে এর প্রধান কারণ অন্য কিছু নয়, নারীকে ক্ষমতাবঞ্চিত করা ভিন্ন। এ হচ্ছে অন্তঃপুরচারী প্রতিহিংসা। বাংলাদেশের জন্য বড় বড় সমস্যা হলো এর জনসংখ্যা। এ সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি পেত না, যদি সন্তান প্রজননের ব্যাপারে মায়ের হাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকত। কিন্তু হায়, তা তো ছিল না। সিদ্ধান্ত পিতাই নিয়েছে, যার নিজের জীবনে সন্তান উৎপাদনের বাইরে বিনোদনের সুযোগ ছিল নিতান্ত সীমিত। তা ছাড়া এ রকমের দৃষ্টান্ত বিরল নয় যেখানে দেখা গেছে যে একের পর এক কন্যাসন্তান জন্ম দিয়ে ক্লান্ত মাতা পুত্রসন্তানের জন্মদানের আগে অব্যাহতি পাননি। আমাদের সীমাবদ্ধ সমাজে মেয়েদের বিনোদনের একটি হচ্ছে পরস্পরের মাথা পরীক্ষা করে উকুন বাছা- সে বিনোদন যে ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে মাতা থেকে সন্তানের সংক্রমিত হয়নি, এমন কথাই বা কী করে বলি। অনর্থক তর্ক করা, গৌণ সমস্যাকে প্রধান করে তোলা, চুলচেরা বিশ্লেষণ করা থেকে বাঙালি কবে মুক্তি পাবে কে জানে।
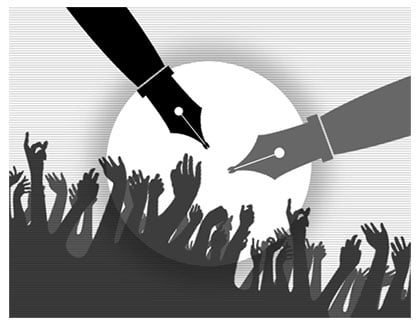 এ ভূখণ্ডে ক্ষমতার অভাব নারী-পুরুষনির্বিশেষেই সত্য; নারীবঞ্চিত অধিক পরিমাণে এটা সত্য, কিন্তু পুরুষের হাতে যে প্রভূত ক্ষমতা রয়েছে তান্ডও নয়। প্রধান কারণ দারিদ্র্য। অথচ এ এলাকায় সম্পদ ছিল, বস্ত্র ও রেশমশিল্প তো ছিলই, কৃষিতে যেমন ছিল অপার সম্ভাবনা, মাটির নিচেও সম্পদ কম ছিল না। এখন যে গ্যাস, কয়লা ও তেলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে ইউরেনিয়ামও পাওয়া যেতে পারে, সেগুলো তো আগেও ছিল, কিন্তু অনুসন্ধানের সুযোগ ছিল না। কারণ হলো পরাধীনতা। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো এটা যে বাংলার সম্পদই বাংলার দারিদ্র্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই সম্পদের ঘ্রাণ পেয়েই ঔপনিবেশিক ইংরেজ এ দেশে এসেছিল। এখন যে সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে তাও মনে হয় দ্বিতীয়বার আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বড় বড় সিদ্ধান্ত এখন বিদেশেই গৃহীত হয়, সামনের দিনগুলোতে এ ব্যাপারে আরও ‘উন্নতি’ ঘটার আশঙ্কা।
এ ভূখণ্ডে ক্ষমতার অভাব নারী-পুরুষনির্বিশেষেই সত্য; নারীবঞ্চিত অধিক পরিমাণে এটা সত্য, কিন্তু পুরুষের হাতে যে প্রভূত ক্ষমতা রয়েছে তান্ডও নয়। প্রধান কারণ দারিদ্র্য। অথচ এ এলাকায় সম্পদ ছিল, বস্ত্র ও রেশমশিল্প তো ছিলই, কৃষিতে যেমন ছিল অপার সম্ভাবনা, মাটির নিচেও সম্পদ কম ছিল না। এখন যে গ্যাস, কয়লা ও তেলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে ইউরেনিয়ামও পাওয়া যেতে পারে, সেগুলো তো আগেও ছিল, কিন্তু অনুসন্ধানের সুযোগ ছিল না। কারণ হলো পরাধীনতা। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো এটা যে বাংলার সম্পদই বাংলার দারিদ্র্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই সম্পদের ঘ্রাণ পেয়েই ঔপনিবেশিক ইংরেজ এ দেশে এসেছিল। এখন যে সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে তাও মনে হয় দ্বিতীয়বার আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বড় বড় সিদ্ধান্ত এখন বিদেশেই গৃহীত হয়, সামনের দিনগুলোতে এ ব্যাপারে আরও ‘উন্নতি’ ঘটার আশঙ্কা।
সমস্যাটা হলো ক্ষমতা বৃদ্ধি করার। সমষ্টিগত ক্ষমতা বৃদ্ধি ব্যক্তিগতভাবে সম্ভব নয়। সমষ্টিগতভাবেই তা করতে হবে। ক্ষমতা এখন কুক্ষিগত হয়েছে কতিপয় ব্যক্তির হাতে। আমাদের নদীগুলো যেমন কোথাও শুকিয়ে যাচ্ছে, কোথাওবা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হচ্ছে, ক্ষমতাও তেমনি ব্যক্তিগত হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে, স্বাভাবিক নদীর মতো প্রবহমান থাকছে না, সমৃদ্ধ করতে পারছে না সমগ্র দেশকে, অর্থাৎ দেশবাসীকে। দেশের সম্পদ যেভাবে পাচার হয়ে যাচ্ছে এবং তুলে দেওয়া হচ্ছে বিদেশিদের হাতে তা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন ও যুদ্ধজয়ের দিনগুলোর কথা এবং তখনকার মীর জাফরদের ভূমিকাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বাধীনতার সৈনিকরা অমর বটে, কিন্তু মীর জাফর যে মরণশীল তান্ডও তো বলা যাচ্ছে না।
আমরা ক্ষমতাবান হব এ সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল একাত্তর সালের দুর্যোগের দিনগুলোতে। মানুষ তখন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল একটি সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে। সেই ঐক্যে নানা ধরনের দুর্বলতা ছিল। যাদের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা সেই আওয়ামী লীগ একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, এবং তাদের উদ্বেগের মধ্যে প্রধান ছিল নেতৃত্ব, যাতে বামপন্থিদের হাতে চলে না যায় সে ব্যাপারটা নিশ্চিত করা। সামনে ছিল যে মধ্যবিত্ত তাদের সঙ্গে মূলশক্তি যে কৃষিজীবী সমাজ তার যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত সামান্য। যে বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন গ্রামের রাজনৈতিক কর্মীরা তা না বুঝে এ বিপজ্জনক সন্দেহ প্রকাশ করেছে যে এরা ছদ্মবেশী পাকিস্তানি চর, গ্রামে এসেছে অন্তর্ঘাতের উদ্দেশ্যে। তবু একটা স্রোত তৈরি হয়েছিল বৈকি, যাতে অনৈক্যের উপাদানগুলো আবর্জনার মতো ভেসে চলে যাবে বলে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ থেমে গেছে ৯ মাসেই এবং সঙ্গে সঙ্গে স্রোতটিও পড়েছে স্তব্ধ হয়ে। এখন প্রবাহের তুলনায় আবর্জনাই প্রধান হয়ে উঠছে। কথা ছিল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও সুষম বণ্টন ঘটবে; তা হলো না, রক্ষকরা ভক্ষক হয়ে দাঁড়াল অথবা বলা যায়, আকাক্সক্ষার দিক থেকে তারা ভক্ষকই ছিল, সাময়িকভাবে ভূমিকা নিয়েছিল রক্ষকের।
মুক্তিযুদ্ধ ঐক্য, আত্মসম্মানবোধ, আত্মবিশ্বাসের সম্প্রসারণ ও দৃঢ়করণ ঘটিয়েছিল। অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ঘোষণা দিয়েছিলে, কোনো অবস্থাতেই বাংলাদেশ মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করবে না; যুদ্ধকালে এ বক্তব্য তাঁর একার ছিল না, ছিল সমগ্র জনগণের। মেজাজটা ছিল ওই রকমেরই। পরবর্তীকালে হাওয়া উল্টে গেছে, কেবল সাহায্য নেওয়া নয়, কোন সরকার কতটা তথাকথিত মার্কিন সাহায্য ও সমর্থন আদায় করতে পারছে সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই সরকারের একটি বিশেষ কৃতিত্ব। স্বাধীনতার পর তাজউদ্দীন এ-ও বলেছিলেন যে দেশ চালানোর ব্যাপারে এ দেশের মানুষের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সেটাও সত্য। অভিজ্ঞতা ছিল না, তবে শেখার যে আগ্রহ ছিল তান্ডও বলা যাবে না। তা ছাড়া শাসনক্ষমতা যারা পেল তাদের প্রধান আগ্রহটা হয়ে দাঁড়াল ক্ষমতা কুক্ষিগত করার। জনগণের ক্ষমতা ব্যক্তিগত ও দলীয় হয়ে গেল।
ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অর্জিত ক্ষমতা জনগণের মধ্যে বিতরণ করা দরকার ছিল। করলে অর্থনৈতিক জীবনে সবাই অংশ নিতে পারত, যার ফলে ক্ষমতা বৃদ্ধি পেত এবং জনগণ যেহেতু রক্ষকের ভূমিকা নিত তাই তা জনগণের সম্পত্তি রয়ে যেত, পাচার হতো না, অব্যবহৃত অবস্থায় যে পচে যাবে তেমন ঘটনাও ঘটত না।
ব্যাপারটি সে পথে এগোয়নি। ফলে ক্ষমতাহীনতার অভিশাপটা কাটল না এবং বাংলা ভাষাও ক্ষমতাবানদের ভাষায় পরিণত হলো না। আমরা চলে গেলাম নব্য ঔপনিবেশিকতার অধীনে। দারিদ্র্য ঘুচল না। বাংলা ভাষা দরিদ্রের ভাষাই রয়ে গেল। এ পরিচয় ঘোচাতে হলে ক্ষমতার নতুন বিন্যাস ঘটানো চাই, প্রতিষ্ঠা চাই প্রকৃত গণতন্ত্রের; অর্থাৎ অধিকার ও সুযোগের সাম্য, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং নাগরিকদের মানবিক অধিকারের কার্যকর স্বীকৃতির। মুক্তিযুদ্ধের সমষ্টিগত লক্ষ্যেও এটাই ছিল। আত্মরক্ষা তো বটেই, কিন্তু সেই সঙ্গে আত্মসম্মান ও আত্মশক্তি বৃদ্ধিও।
লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়