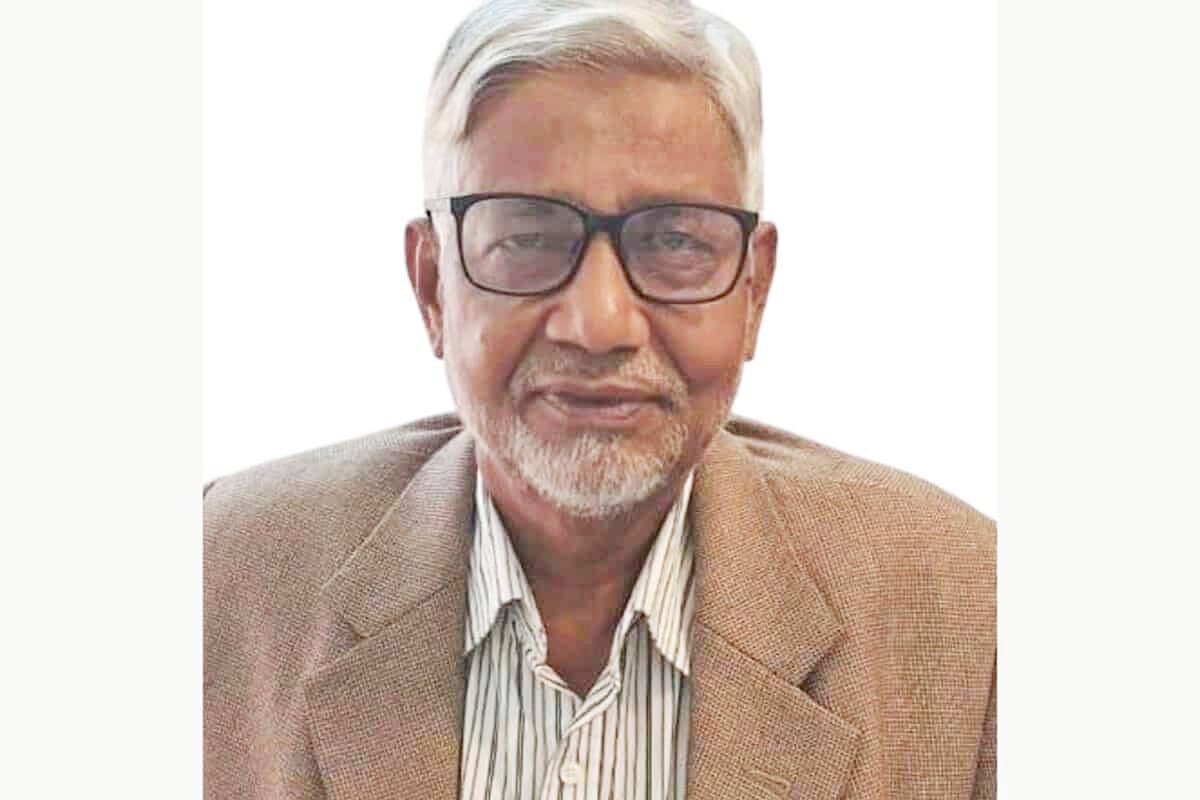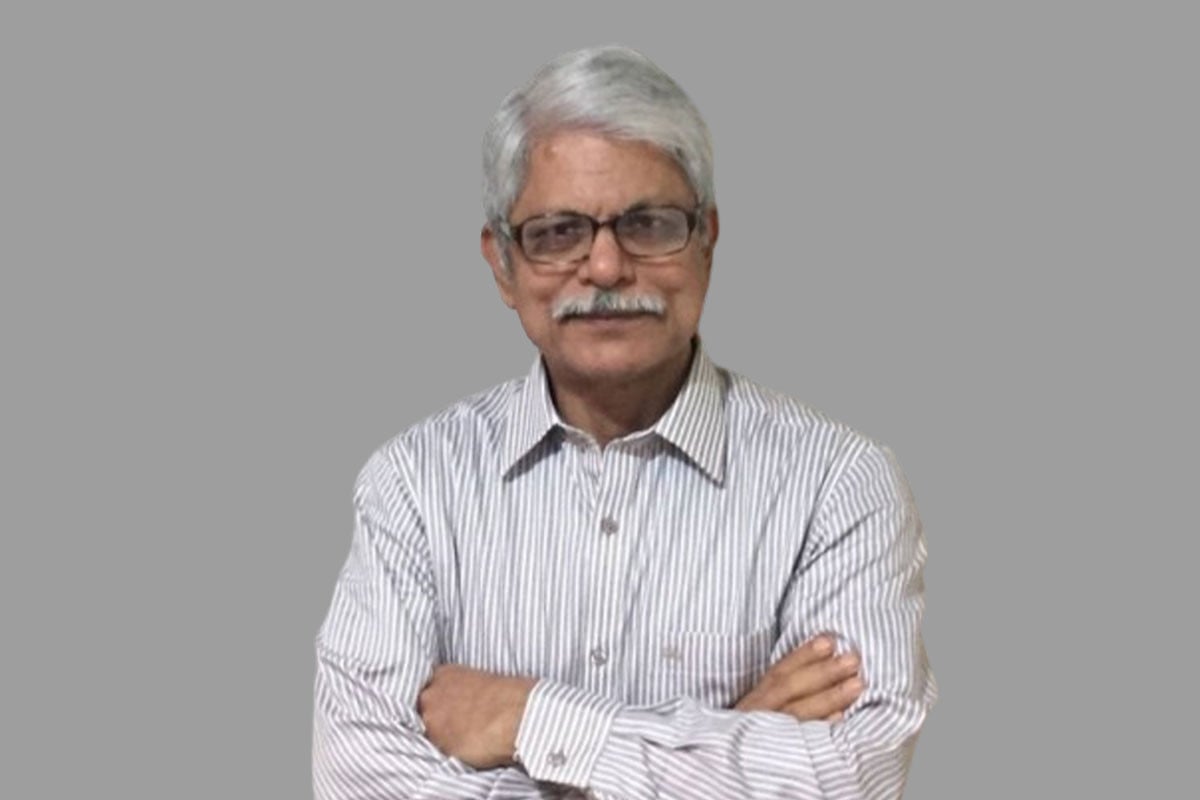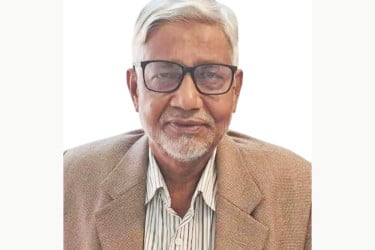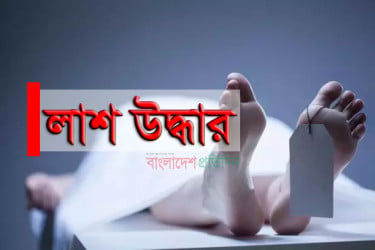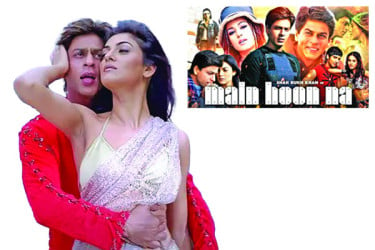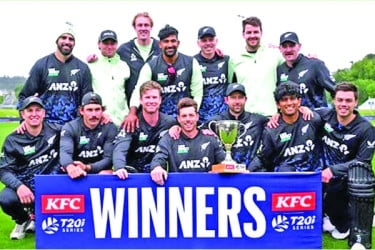দেশ এখন এক সংকট ও সম্ভাবনার সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে নির্বাচনী হাওয়া সারা দেশেই বইছে, অন্যদিকে রাজনৈতিক সংস্কার, জনবিশ্বাস পুনঃস্থাপনের চ্যালেঞ্জ লক্ষ করা যাচ্ছে। এবারের নির্বাচন নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলকে পুনরায় ফিরে পাওয়ার এক বড় পরীক্ষা। নির্বাচন ঘিরে যে উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা শুধুই ক্ষমতায় যাওয়ার লড়াই বা ভোটার উৎসাহের বিষয় নয়, এখানে রয়েছে ‘ভোট কি কার্যকর হবে?’, ‘সক্রিয় অংশগ্রহণ কি সম্ভব হবে?’ এবং ‘নির্বাচন-পরবর্তী সময় কী রূপ ধারণ করবে?’—এসব বেশি গভীরে ভাবার বিষয় সামনে এসেছে।
বিগত কয়েকটি নির্বাচনে আমরা দেখেছি ভোটার অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল, গ্রহণযোগ্যতার ঘাটতি ছিল। বিরোধী দলগুলোর বড় অংশ নির্বাচনে ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে খুব ন্যায্যভাবেই আলোচনা সামনে আসে যে শুধুই নির্বাচন আয়োজন বা ঘোষণা বড় কথা নয়, সমস্যা হলো নির্বাচন-পরবর্তী সময়, তার স্বীকৃতি, অংশগ্রহণ ও জন-আস্থার পরিবেশ। এবারের নির্বাচনকে তাই শুধু ‘আগামী নির্বাচন’ বলা যাবে না, এটি হবে একটি রূপান্তরপ্রক্রিয়ার অংশ, যেখানে নির্বাচন নিজেই একটি উদ্দেশ্য নয়, বরং একটি ‘মাধ্যম’ হয়ে উঠবে।
এ ক্ষেত্রে বিষয়টি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে বেশ কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে।
প্রথমত, রাজনৈতিক প্রস্তুতির দিক থেকে দেখা যাচ্ছে যে দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি এরই মধ্যে ২৩৭টি আসনের প্রার্থিতা ঘোষণা করেছে। জামায়াতও প্রায় সব আসনেই তাদের প্রার্থিতা ঘোষণা করেছে আরো আগেই। এটি একটি সক্রিয় পদক্ষেপ, যেখানে দল বিশ্বাসযোগ্যভাবে সামনে এগোচ্ছে।
আবার সম্প্রতি আমরা লক্ষ করলাম বিএনপি থেকে যাঁরা প্রার্থিতার গ্রিন সিগন্যাল পাননি, তাঁরা বিদ্রোহ করে বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। আশা করছি, এই সংকট তারা কাটিয়ে উঠবে। কিন্তু মোটাদাগে যে বিষয়টি না বললেই নয়, তা হলো শুধু প্রার্থী ঘোষণা করলেই সবকিছু শেষ হয় না—প্রত্যক্ষ নির্বাচনী পরিবেশ, অংশগ্রহণকারীর মনোবল, নিরাপত্তা ও তথ্য প্রচারণার স্বচ্ছতা এবং নিয়ন্ত্রণ—এসব একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এ ছাড়া বাংলাদেশে এই মুহূর্তে নির্বাচনের সংবিধান-বিধি ও প্রতিষ্ঠানগত প্রেক্ষাপটের দিক থেকেও বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যেমন—Representation of the People Order, 1972 (RPO) সংশোধনের কারণে বড় দলের প্রতীকে অংশ নেওয়ার বিষয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে।
এ ছাড়া জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, গণভোট পরিকল্পনা ও সংশোধিত সংবিধান প্রস্তাব—এসব প্রশ্ন ঝুলে আছে। আর এগুলো ভোটের পরিবেশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে বলে মনে হচ্ছে।
দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষ নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা মনে করছে নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুটি দিক সামনে রয়েছে। একদিকে রয়েছে ‘নির্বাচন ভালো হবে’ এমন আশাবাদ। অন্যদিকে রয়েছে ‘যদি অংশগ্রহণ না হয় বা প্রতিযোগিতা না হয়’-এর ভয় বা শঙ্কাও। অংশগ্রহণ মানে শুধু ভোট দেওয়াই নয়, অংশগ্রহণ মানে ভোটের পর ফলাফল গ্রহণ, সিদ্ধান্তকে স্বীকার এবং অংশগ্রহণকারীর মনোবলকে সম্মান করা।
তৃতীয়ত, রাজনৈতিক মেরুকরণের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জ লক্ষ করা গেছে। বিশেষ করে ইসলামিক দলগুলোর রাজনৈতিক উত্তরণ ও পথচলা নতুন মাত্রা পাচ্ছে। এই শক্তিগুলো শুধুই নির্বাচনের লড়াই নিয়ে নয়, তারা নিজেদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকেও নতুনভাবে সাজাচ্ছে, যা আগামী দিনের সংসদীয় প্রতিযোগিতায় প্রভাব ফেলতে পারে।
এ ছাড়া তথ্য ও মিডিয়া পরিবেশও এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট এবং এর পূর্ববর্তী সময়ে ঘটে যাওয়া আন্দোলন ও তার ডিজিটাল পরিণতি দেখিয়ে দিয়েছে যে সোশ্যাল মিডিয়া ভিত্তিক আন্দোলন ও তথ্য প্রচারণা আমাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে দ্রুত পরিবর্তন করছে। এই পরিবর্তন শুধু নির্বাচনের দিনেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি নির্বাচনপ্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাজ করবে—ভোটার সিদ্ধান্তে, প্রচারণায়, ফলাফল গ্রহণে। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, এসব প্রস্তুতি, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ মিলিয়ে আসন্ন নির্বাচনের ‘বড় অর্থ কী হতে পারে’?
প্রথমত, এটি হতে পারে একটি নতুন রাজনৈতিক যাত্রার সূচনা। যদি নির্বাচন হয় অংশগ্রহণমূলক, অংশগ্রহণমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে, তাহলে এমন একটি রূপ তৈরি হতে পারে, যেখানে ভোট শুধু জেতার লড়াই নয়, ভোট হবে নির্বাচিত প্রতিনিধির প্রতি দায়বদ্ধতা ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রতীক। সরকারের দায়িত্ব শুধু নির্বাচনের আয়োজন করে কোনো দলকে বিজয়ী করে দেওয়া নয়, বরং আগামী দিনে মানুষের জীবনে পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক কৃষ্টি ও গতিতে পরিবর্তন আনার প্রসঙ্গ।
দ্বিতীয়ত, বিগত সময়ের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাঠামোগত সমস্যা ছিল। আজ সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নির্বাচন কমিশন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী, রাজনৈতিক দল, মিডিয়া ও নাগরিক সমাজ যেন মিলিত হয়ে একটি নতুন মানদণ্ড গড়তে পারে।
তৃতীয়ত, যদি দায়িত্বশীলভাবে সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহলে এটি হবে বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের পরিচয়ের পুনর্গঠন। নির্বাচনের ফলাফল শুধু দেশীয় প্রতিফলন নয়, এটি আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিফলিত হবে নির্বাচন অবাধ, অংশগ্রহণ ও সার্বভৌমতার দৃষ্টিকোণ থেকে। আজ বিশ্বকে দেখানোর সময় এসেছে যে বাংলাদেশের ভোটব্যবস্থা শুধু ত্রুটিপূর্ণ নয়, বরং আশাবাদও সৃষ্টি করতে পারে।
বিপরীতভাবে যদি ভোট হয় উদ্বেগ পরিপূর্ণ পরিবেশে, যদি অংশগ্রহণ কম হয়, তাহলে এই নির্বাচন হয়ে উঠতে পারে বিভাজনের উৎস, বিশ্বাসের সংকট এবং গণতান্ত্রিক ধারণার ক্ষয়ের কারণ। যেমন ‘একতরফা ভোট’, ‘আংশিক প্রতিযোগিতা’—এসব ঘটনা জাতীয় ভাবমূর্তিতে নেতিবাচক প্রতিফলন ছুড়ে দিতে পারে।
নির্বাচন কমিশন ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে এখন আর অপেক্ষা করার সুযোগ নেই, সময় এসেছে তাদের দায়িত্ব সচলভাবে নেওয়ার। বিচারিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক প্রস্তুতি যেন দ্রুতগতিতে এগিয়ে নেওয়া হয়। নাগরিক সমাজের পক্ষে এখন দায়িত্বের সময় এসেছে। ভোটারদের শুধু শেয়ার-লাইকে থাকলে চলবে না। নির্বাচনের সত্যিকারের শক্তি শুধু ভোট হয়েছে কি না, কারা জয় পেয়েছে সেগুলোই নয়, এর সঙ্গে আরো অনেক বিষয় জড়িত রয়েছে।
পরিশেষে বলতে পারি, এই নির্বাচন আমাদের সময়-সন্ধিক্ষণের একটি চিহ্ন হতে পারে। আমরা যদি আজ দায়িত্বশীলভাবে এগিয়ে যাই, যথাযথভাবে প্রস্তুত হই, তাহলে আসন্ন নির্বাচন শুধু একটি ভোটের আয়োজন হবে না, বরং সেটি হবে একটি ‘মুহূর্ত’, একটি ‘ধাপ’ এবং একটি ‘সম্ভাবনা’, যা আমাদের রাজনীতিতে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পরিবেশ তৈরি করতে পারে। রাজনীতির সম্ভাবনা শুধু নির্বাচনে জয়ের জন্য নয়, সম্ভাবনা ভবিষ্যতের বাংলাদেশের রূপায়ণ। এই বাস্তবতার নাম গণতন্ত্রের টেকসই টিকে থাকা। কাজেই বলা যায়, যদি সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে না গিয়ে দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে চিন্তা করতে পারে, তাহলে হয়তো আগামী নির্বাচনই হবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পুনর্জন্মের সূচনা।
লেখক : অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়