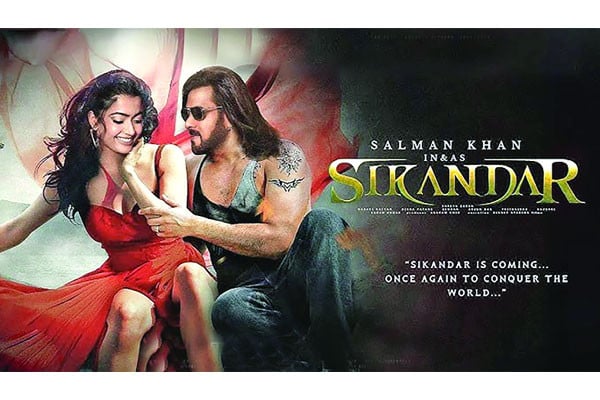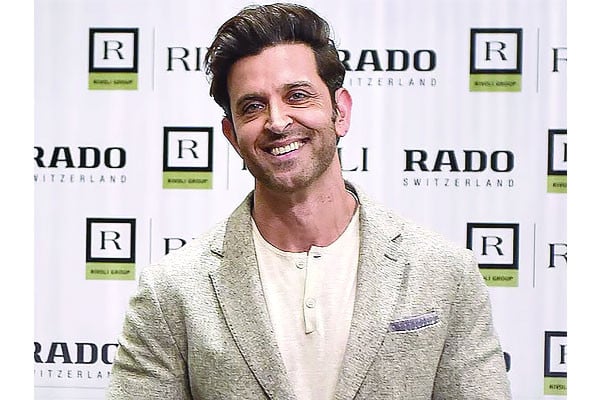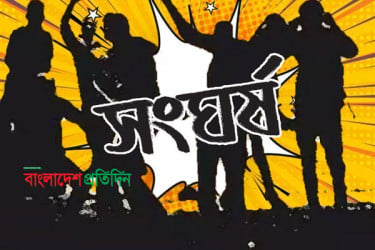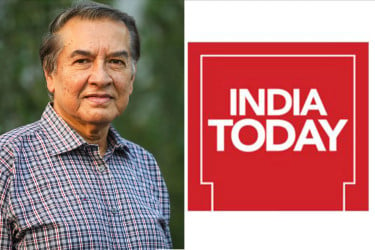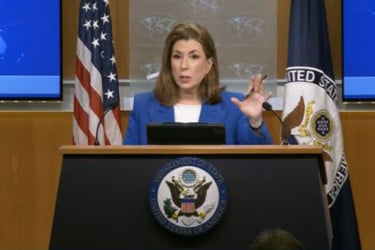‘আরে ওই...পুত, কই যাইতাছোস’ এমন বাজে বাক্য এখনকার সিনেমার সংলাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ একসময় এ বাক্যটা এভাবে ব্যবহার হতো-‘আরে ভাই কোথায় যাচ্ছেন’। এমন অবক্ষয়যুক্ত শব্দ আর বাক্য যেন এখনকার চলচ্চিত্রে অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেছে। এ নিয়ে বোদ্ধাশ্রেণি কী বলেন- ‘চলচ্চিত্র হচ্ছে জীবনের প্রতিচ্ছবি। তাই এর ভাষা হতে হবে জীবনঘনিষ্ঠ। আশির দশক পর্যন্ত আমাদের চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত ভাষা ছিল যথার্থ এবং শব্দ ও উচ্চারণে সমৃদ্ধ। তাই ওই সময়ের চলচ্চিত্রগুলো এখনো দর্শকের মনে চিরগাঁথা হয়ে আছে’, বললেন সিনিয়র চলচ্চিত্র সাংবাদিক আবদুর রহমান। চলচ্চিত্রে প্রচলিত বাংলা ভাষার দৈন্যের জন্য তিনি দায়ী করলেন স্ক্রিপ্ট রাইটার ও ডিরেক্টরকে। তাঁর কথায়- বর্তমানে আহমদ জামান চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, আমজাদ হোসেন প্রমুখের মতো স্ক্রিপ্ট রাইটারের যথেষ্ট অভাব রয়েছে, ফলে চলচ্চিত্রে শব্দ ও উচ্চারণ প্রক্ষেপণে ব্যত্যয় ঘটছে মারাত্মকভাবে। আগে একটি স্ক্রিপ্ট যথেষ্ট সময় নিয়ে লেখা ও পরিমার্জন করা হতো। এখন তা হয় না বললেই চলে। এ সিনিয়র সাংবাদিক আক্ষেপ করে আরও বলেন, চলচ্চিত্র হচ্ছে একটি দেশের প্রধান গণমাধ্যম। তাই চলচ্চিত্রে কোন চরিত্রের মুখে কেমন শব্দ ও উচ্চারণ প্রয়োগ করা হবে সেটি সম্পর্কে একজন ডিরেক্টরের যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে। যেমন চলচ্চিত্রে অভিনয় করা একজন বিচারক বা আইনজীবীর মুখ থেকে যদি আঞ্চলিক ভাষা বের হয় তাহলে তা দর্শক মেনে নেবে না। তবে তার চাপরাশি বা একজন আসামি যদি আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ প্রক্ষেপণ করে তবে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আঞ্চলিক ভাষাও কিন্তু শব্দ ও উচ্চারণে যথার্থ হতে হবে। বর্তমানে দর্শক চলচ্চিত্রে দৈনন্দিন জীবনের প্রমিত শব্দ ও উচ্চারণ খুঁজে না পেয়ে চরম হতাশ হচ্ছে। আবদুর রহমান বলেন, এরপর ডিরেক্টরকে দায়ী করতে হয় এ জন্য যে, তার নির্দেশনায়ই একটি চলচ্চিত্রের সবকিছুই গড়ে ওঠে। তাই এ অবক্ষয়ের দায় একজন ডিরেক্টর কোনোভাবেই এড়াতে পারেন না। চলচ্চিত্রে জীবনের চিরচেনা প্রচলিত শব্দ ও উচ্চারণের উপস্থাপনাকে যথাযথ করতে পারলেই আবার তা দর্শক-মনে সাড়া জাগাবে বলে আমার বিশ্বাস।
সিনিয়র চলচ্চিত্র সাংবাদিক ও গবেষক অনুপম হায়াৎ বলেন, চরিত্র অনুযায়ী হবে মুখের ভাষা। এ অজুহাতে বাংলাদেশের সিনেমায় পরিপূর্ণ প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার ধীরে ধীরে কমছে। এসব ক্ষেত্রে মূলত এখন প্রাধান্য পাচ্ছে আঞ্চলিক ভাষা। অনেকের মতে, একটি ছবি কিংবা নাটক সব ভাষার সব সমাজের প্রতিনিধিত্ব করবে। সৃষ্ট চরিত্রটি তার চরিত্রের উপযোগী ভাষা ও শব্দেই কথা বলবে। সেখানে ভাষা চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু গেল দুই দশকে ঢাকাই ফিল্ম অদ্ভুত এক ভাষায় মত্ত হয়ে আছে। যে ভাষার আসল নাম কী তা জানা নেই কারও। অনুপম হায়াৎ আরও বলেন, যে কোনো সংস্কৃতি চর্চার জন্য ভাষা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ভাষার অপপ্রয়োগে অধঃপতন হতে পারে অনেক শক্ত ও মজবুত শিল্পেরও। সেই অধঃপতনের দিকেই যেন হাঁটছে এ দেশের সিনেমা। ষাট থেকে কমপক্ষে নব্বই দশকে ঢাকাই ছবিতে ভাষার যে শানিত উচ্চারণ ও আবেদন ছিল, কালক্রমে তা হারিয়ে গেছে। সেখানে দখল নিয়েছে আঞ্চলিক ভাষাগুলো। সেগুলোও উঠে আসছে ভুল উচ্চারণ ও অর্থ নিয়ে। নানা দোহাই ও অজুহাতে ঠাঁই পাচ্ছে অশ্লীল সংলাপও। আজকাল বাস্তবতার দোহাই দিয়ে জাঁকজমক আয়োজনে মানহীন গল্প ও সংলাপে সিনেমা নির্মিত হচ্ছে। সেখানে বিকৃত ভাষা স্থান পাচ্ছে। ফলে তা আর দর্শক গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। আরও একটি বেদনার বিষয় হলো- ভাষাকে বিনোদনের মসলাদার হাতিয়ার বানিয়ে অনেক সময় বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণ ঘটানো হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা ও নির্মাতা তৌকীর আহমেদ বলেন, ‘এ অশুদ্ধ চর্চা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সিনেমায় বাংলা ভাষাটাকে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। স্ক্রিপ্টে আঞ্চলিকতার ব্যবহার দোষের কিছু নয়। এটা একটা নির্দিষ্ট গল্পের জন্য থাকে। তবে সেখানেও খেয়াল রাখতে হবে অশ্লীল বা অশুদ্ধ সংলাপ যেন না থাকে। শেষ কথা- সেন্সর বোর্ড, স্ক্রিপ্ট রাইটার ও নির্মাতারা একটু সচেতন থাকলে হয়তো এর সমাধান হলেও হতে পারে।’ চিত্রপরিচালক কাজী হায়াত বলেন, সিনেমা কখনো শুদ্ধ ভাষায় চলতে পারে না। যেমনটা হচ্ছে- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা শরৎচন্দ্রের সাহিত্য দিয়ে সিনেমার ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন না। ‘আমি এখন ওপারে কী করিয়া পার হইব’ এটা সম্পূর্ণ সাধু ভাষা। এটা হয়তো ছবিতে চরিত্রের স্বার্থে কিছু দৃশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু পুরো সিনেমায় এ শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার যোগ হতে পারে না। চরিত্রের জন্য সঠিক ভাষার ব্যবহার ঠিক রাখতে হবে এবং যথাসময়ে পরিবর্তন করতে হবে। সিনেমার ভাষাটা একদমই আলাদা। এখানে দর্শকদের সিনেমা হলে ধরে রাখতে হলে যে কোনো ভাষার ব্যবহার রাখতে হবে। কিন্তু তার মানে এই নয়, অশ্লীল ভাষা বা অশুদ্ধ কোনো সংলাপ যোগ করতে হবে। এ বিষয়ে গল্পকার, নির্মাতা, অভিনেতা অভিনেত্রী ও সেন্সর বোর্ডকে একটু সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যে, ভাষার ব্যবহার সঠিক হচ্ছে কি না?