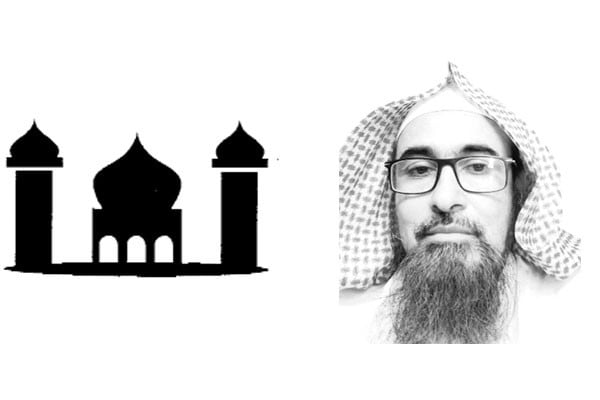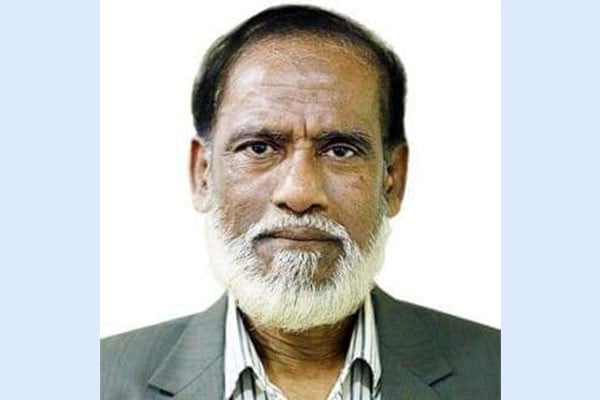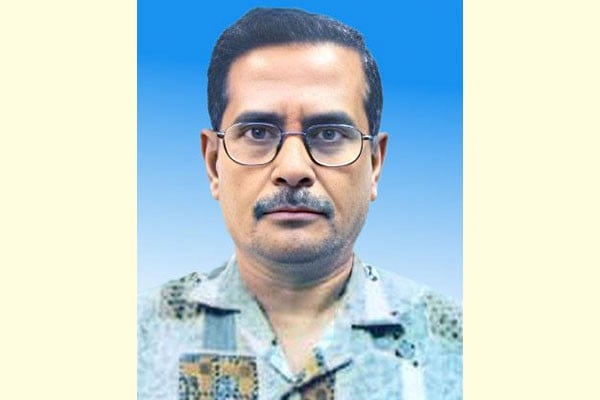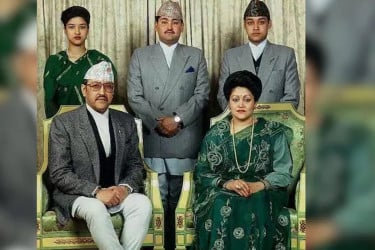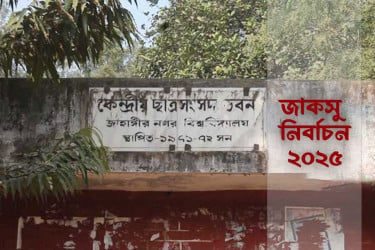হঠাৎ করেই নির্বাচনের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম গতকাল রাতে সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানিয়েছেন। গতকালের এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে নির্বাচন নিয়ে ধোঁয়াশা অনেকটা কেটে গেছে। আশা করা যায় প্রধান উপদেষ্টার প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যেই নির্বাচন অনুুষ্ঠিত হবে। ভোটে অংশগ্রহণের জন্য দেশের জনগণও মুখিয়ে আছে। বলা যায় জনগণ প্রস্তুত। তবে নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এখনো ঐকমত্য তৈরি হয়নি।
.jpg) আমাদের সংবিধানের প্রথম ভাগে ৭ (১)-এ বলা হয়েছে, ‘প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।’ এ জনগণই রাজনীতি ব্যবসার কাঁচামাল। বিগত ৫৪ বছরই জনগণের কল্যাণে, জনগণকে সামনে রেখে সবাই যার যার কাজ করে গেছে। জুলাই অভ্যুত্থানের পর এবার শুরু হয়েছে নতুন বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রাম। এখনো সবাই জনগণের চিন্তায় অস্থির। জনগণ কীভাবে ভালো থাকবে, কীভাবে জনগণের নিরাপত্তা, মানবাধিকার নিশ্চিত করা যাবে এ নিয়ে ১১ মাস ধরে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনগণের সর্বময় ক্ষমতা খর্ব করে বিনা ভোটে নেতা হওয়ার দাবি করছে জনগণের হিতাকাক্সক্ষী অনেক দল। আমাদের নির্বাচনব্যবস্থায় সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদ সদস্য হওয়ার সুযোগ আছে। বিগত সংসদে ৫০ জন নারী বিনা ভোটে অর্থাৎ সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির (পিআর) ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল ও জোটের সংরক্ষিত মহিলা আসনে এমপি হয়েছিলেন। তাহলে এখন যারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে সংসদে নিজেদের অবস্থান ভোটের আগেই নিশ্চিত করতে চান তারা জনগণের অধিকারকে কতটা মূল্য দিচ্ছেন? যদি শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত মহিলা আসনের মতো পিআর পদ্ধতি চালু হয়, তাহলে দেশের মালিক জনগণ কী পাবে? এমনিতেই জনগণের ওপর নানানরকম চাপ। তারপর আবার নতুন করে বিশ্ববাণিজ্যে ট্রাম্পের শুল্কনীতির চাপও গিয়ে পড়বে জনগণের ওপরই।
আমাদের সংবিধানের প্রথম ভাগে ৭ (১)-এ বলা হয়েছে, ‘প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।’ এ জনগণই রাজনীতি ব্যবসার কাঁচামাল। বিগত ৫৪ বছরই জনগণের কল্যাণে, জনগণকে সামনে রেখে সবাই যার যার কাজ করে গেছে। জুলাই অভ্যুত্থানের পর এবার শুরু হয়েছে নতুন বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রাম। এখনো সবাই জনগণের চিন্তায় অস্থির। জনগণ কীভাবে ভালো থাকবে, কীভাবে জনগণের নিরাপত্তা, মানবাধিকার নিশ্চিত করা যাবে এ নিয়ে ১১ মাস ধরে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনগণের সর্বময় ক্ষমতা খর্ব করে বিনা ভোটে নেতা হওয়ার দাবি করছে জনগণের হিতাকাক্সক্ষী অনেক দল। আমাদের নির্বাচনব্যবস্থায় সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদ সদস্য হওয়ার সুযোগ আছে। বিগত সংসদে ৫০ জন নারী বিনা ভোটে অর্থাৎ সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির (পিআর) ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল ও জোটের সংরক্ষিত মহিলা আসনে এমপি হয়েছিলেন। তাহলে এখন যারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে সংসদে নিজেদের অবস্থান ভোটের আগেই নিশ্চিত করতে চান তারা জনগণের অধিকারকে কতটা মূল্য দিচ্ছেন? যদি শেষ পর্যন্ত সংরক্ষিত মহিলা আসনের মতো পিআর পদ্ধতি চালু হয়, তাহলে দেশের মালিক জনগণ কী পাবে? এমনিতেই জনগণের ওপর নানানরকম চাপ। তারপর আবার নতুন করে বিশ্ববাণিজ্যে ট্রাম্পের শুল্কনীতির চাপও গিয়ে পড়বে জনগণের ওপরই।
আমাদের দেশে শাসনব্যবস্থা ওয়েস্টমিনস্টার পদ্ধতির। বর্তমানে যে ব্যবস্থাটি দেশে প্রচলিত। ওয়েস্টমিনস্টার বিষয়টি লন্ডনের প্যালেস অব ওয়েস্টমিনস্টার থেকে এসেছে। যেখানে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অবস্থিত। ব্রিটেনের নির্বাচনব্যবস্থাকেই ওয়েস্টমিনস্টার সিস্টেম বলা হয়। কমনওয়েলথভুক্ত দেশ বা ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল যে দেশগুলো, মূলত সেসব দেশে এ ব্যবস্থায় নির্বাচন হয়। অর্থাৎ আমরা ব্রিটিশ ব্যবস্থা অনুসরণ করছি। কারণ গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে এখনো ব্রিটিশ ব্যবস্থা পৃথিবীতে অনন্য। ওয়েস্টমিনস্টার ব্যবস্থায় আসনভিত্তিক নির্বাচন হয়। এতে দলের এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকেন। যে দলের প্রার্থী বা যে প্রার্থী সর্বোচ্চ ভোট পান তিনিই ওই আসন থেকে সংসদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।
এদিকে দেশে বর্তমান পদ্ধতির বাইরে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি নিয়ে এখন রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা চলছে। পৃথিবীর ১৭০টি দেশের নির্বাচনব্যবস্থায় ইসরায়েলসহ প্রায় ৮০টি দেশে নির্বাচন হয় সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে। যেটিকে বলা হয় প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন বা পিআর। এ পদ্ধতিতে একটি দল যত ভোট পায়, সে অনুপাতে জাতীয় সংসদে আসন পায়। এতে একটি নির্বাচনের পর সংসদে সব দলের ও মানুষের প্রতিনিধি থাকে।
নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত ৫০টি দলের মধ্যে বেশ কটি দল পিআর ব্যবস্থার পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছে। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের পক্ষে এখন পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ও বাংলাদেশ ইসলামিক ফ্রন্ট, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি), তৃণমূল বিএনপি, আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি, গণঅধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি (বিএমজেপি) ও বাংলাদেশ কংগ্রেস রয়েছে। বিপ্লবীদের নতুন দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন দাবি করছে।
অন্যদিকে বিদ্যমান নির্বাচনব্যবস্থার পক্ষে রয়েছে দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিএনপি, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, গণফোরাম, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (বাংলাদেশ ন্যাপ), বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি (নিম্নকক্ষ বিদ্যমান ব্যবস্থায় এবং উচ্চকক্ষ পিআর), বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (বিএমএল), জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম (নিম্নকক্ষ বিদ্যমান ব্যবস্থায় এবং উচ্চকক্ষ পিআর), বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (বাংলাদেশ জাসদ), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম), বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বিএসপি), নাগরিক ঐক্য (নিম্নকক্ষ বিদ্যমান ব্যবস্থায় এবং উচ্চকক্ষ পিআর), গণসংহতি আন্দোলন (নিম্নকক্ষ বিদ্যমান ব্যবস্থায় এবং উচ্চকক্ষ পিআর)। এ ছাড়া আরও কিছু দল এখনো কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি।
প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনগণ শুধু দলকে ভোট দেয় না, পছন্দের প্রার্থীকেও ভোট দেয়। প্রত্যেক প্রার্থী যার যার নির্বাচনি এলাকায় পরিচিত। সেই সঙ্গে সভাসমাবেশ, পোস্টার-ব্যানার ছাপিয়ে নিজের পরিচিতি আরও বিস্তৃত করেন। নির্বাচনের দিন প্রার্থীর কর্মীরা কেন্দ্রে ভোটারদের আসতে সহায়তা করেন। দল বা মার্কার পাশাপাশি প্রার্থীর ব্যক্তিপরিচয় নির্বাচনে অনেকটা ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে। যদিও বিগত ১৬ বছরে মার্কার পরিচয়েই নির্বাচন হয়েছে। এখন অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে নির্বাচনব্যবস্থা নিয়ে যে বিভাজন তৈরি হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। অনেকেই মনে করছেন, পিআর পদ্ধতি যতটা না জনগণের মঙ্গলের জন্য দাবি করা হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে নির্বাচনের আগেই দলগুলোর ক্ষমতা নিশ্চিত করা। এমন অনেক দল আছে সেসব দল হয়তো সরাসরি ভোটের মাধ্যমে সংসদে একটি আসনেও নির্বাচিত হতে পারবে না। কিন্তু পিআর পদ্ধতিতে ভোটের সংখ্যানুপাতিক হারে হয়তো একাধিক আসন পেয়ে যাবে। অন্যদিকে পিআর পদ্ধতি দাবিদার দলগুলো মনে করছে, এর ফলে দেশে গণতন্ত্র সুসংহত হবে। ভোটে টাকা ও পেশিশক্তির প্রভাব বন্ধ হবে।
প্রশ্ন হচ্ছে-পিআর পদ্ধতিতে দেশের জনগণ কী পাবে? তারা কি তাদের পছন্দমতো জনপ্রতিনিধি পাবে? জনগণের অধিকার কি শতভাগ নিশ্চিত হবে? ভোটে টাকার প্রভাব কি বন্ধ হবে? জনপ্রতিনিধি যদি দল নির্ধারণ করে তাহলে দলের পকেটে বা দলের প্রভাবশালী নেতার পকেটে যে টাকা ঢুকবে না, এর কোনো নিশ্চয়তা আছে কি? এসব প্রশ্নে এখন থেকেই জনগণের ভাবনায় নতুন করে চাপ পড়ছে।
এমনিতেই গত ১১ মাসে জনগণের ওপর নানান চাপ পড়েছে। কেউ শান্তিতে নেই। চরদিকে অস্থিরতা। আইনশৃঙ্খলার অবস্থা খুবই ভয়াবহ। মব সংস্কৃতিতে সবাই আতঙ্কিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে মসজিদের ইমাম পর্যন্ত মবের শিকার হচ্ছেন। কিশোর-তরুণরা এখন পাড়ামহল্লা নিয়ন্ত্রণ করছে। সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠরা মানসম্মানের ভয়ে কোনো কথা বলছেন না। দেশের অর্থনীতিতে যে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তারা এখন অসহায়ের মতো বসে আছেন। সিরাজউদ্দৌলা নাটকের ডায়ালগের মতো বলতে হয়- ‘ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের কে দেবে আশা, কে দেবে ভরসা।’ সব মিলিয়ে দেশের জনগণ এখন নানামুখী চাপে আছে। জুলাই অভ্যুত্থানের পর যে স্বপ্ন- আকাঙ্খায় সবাই অধীর আগ্রহে দিন গুনছিল, সেই স্বপ্ন কবে বাস্তবে রূপ লাভ করবে কেউ জানে না।
১৮ কোটি মানুষের ওপর আরেকটি নতুন চাপ হলো ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধ। বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা সব ধরনের পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী মাস থেকে এ বাড়তি শুল্ক কার্যকর হবে। সোমবার ট্রাম্প তার নিজস্ব সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে প্রকাশিত চিঠিতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে জানান, ‘২০২৫ সালের ১ আগস্ট থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো সব বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে, যা খাতভিত্তিক বিদ্যমান শুল্কের পাশাপাশি প্রযোজ্য হবে। উচ্চ শুল্ক এড়াতে যদি কোনো পণ্য ঘুরপথে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে, সেগুলোর ওপরও একই হারে শুল্ক আরোপ করা হবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনকারী বাংলাদেশি কোম্পানিগুলোকে শুল্কছাড় দেওয়া হবে এবং দ্রুত অনুমোদনপ্রক্রিয়া নিশ্চিত করা হবে। বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি দীর্ঘমেয়াদি ও একতরফা এবং এ শুল্ক তা সংশোধনেরই একটি পদক্ষেপ। এ সিদ্ধান্ত পুরোপুরি চূড়ান্ত নয়। যদি কেউ বিকল্প প্রস্তাব দেয় এবং সেটি আমাদের ভালো লাগে, তাহলে তা বিবেচনায় নেওয়া হবে।’
অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ এ শুল্ক আরোপকে অপ্রত্যাশিত উল্লেখ করে বলেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি মাত্র ৫ বিলিয়ন ডলারের। সেখানে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ অনুপাতহীন ও অনৈতিক। তবে আমরা বিশ্বাস করি সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে এ হার কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।’ সরকার হয়তো চেষ্টা করবে। তবে এর প্রভাব পড়বে দেশের প্রতিটি নাগরিকের ওপর। দেশের অন্যতম রপ্তানি খাত গার্মেন্ট ভয়াবহ ঝুঁকিতে পড়বে।
দেশের জনগণ এখন সাংঘাতিক বেকায়দায় আছে। একদিকে রাজনীতির চাপ, অন্যদিকে ট্রাম্পের শুল্ক বাণিজ্য চাপ। এ দুই চাপে জনগণের অবস্থা রীতিমতো চিড়েচ্যাপটা। বাংলাদেশের মানুষ বরাবরই রাজনীতি একটু বেশি বোঝে। ড. মুহাম্মদ ইউনূস সঠিক সময়ে নির্বাচন দেবেন কি না, লন্ডন বৈঠকে কী আলাপ হয়েছে, এনসিপির প্রতি প্রধান উপদেষ্টা পক্ষপাতদুষ্ট কি না, দেশ ঠিকমতো চলছে কি না এসব আলোচনা-সমালোচনা গ্রামের চায়ের দোকানেও শোনা যায়। সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে যে কোনো সত্য-অসত্য তথ্য মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশে। নানানরকম অপতথ্যও জনমনে নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করছে। জনগণকে চাপমুক্ত রাখতে দরকার শক্ত হাতে মব নিয়ন্ত্রণ, অর্থনীতি স্বাভাবিক রাখতে ব্যবসায়ীদের সহায়তা দেওয়া এবং বৈদেশিক সম্পর্ক ও বাণিজ্য ঠিক রাখা। তা করতে না পারলে জনগণেরই কষ্ট বাড়বে।
লেখক : নির্বাহী সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন