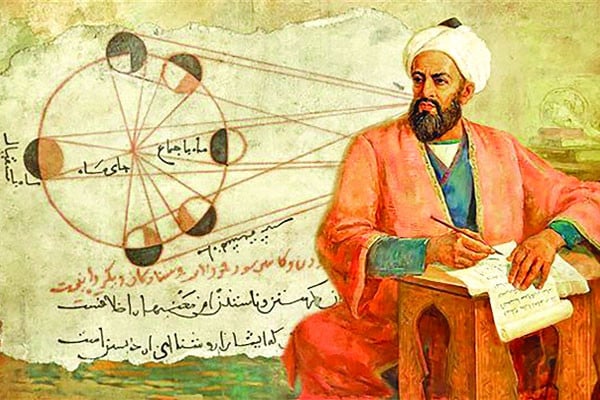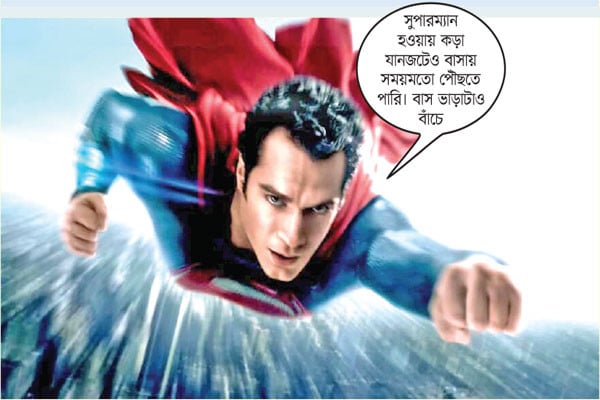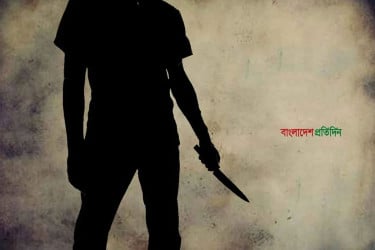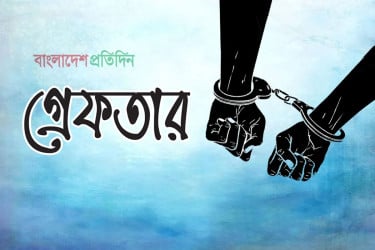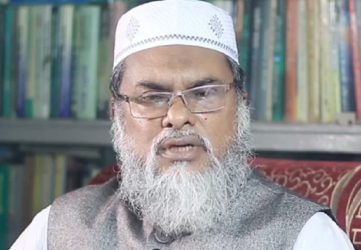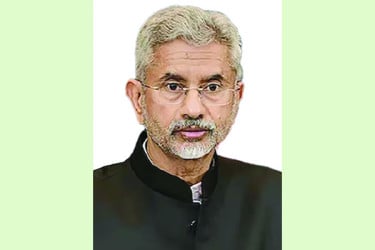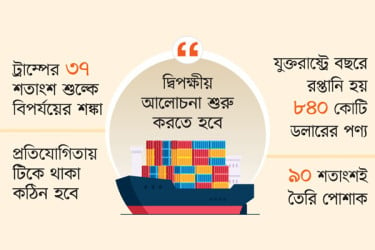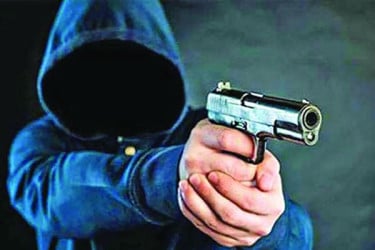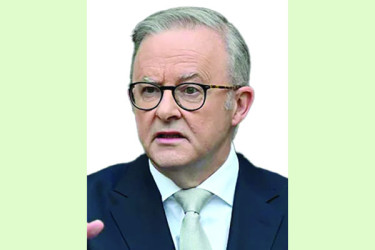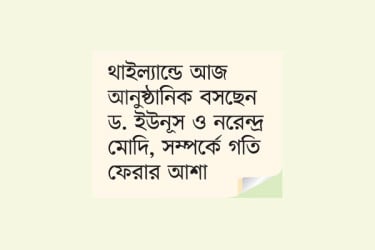স্বাধিকার আন্দোলন ও সংগ্রামের তীর্থস্থল : ’৬৬-এর ছাত্র আন্দোলন থেকে ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ’৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন থেকে ’২৪-এর গণ অভ্যুত্থানসহ সব আন্দোলন-সংগ্রামে উত্তাল হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ’৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশের মতো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও রাজপথে নেমে আসেন। সেদিন পাক হানাদার বাহিনীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বন্দুকের সামনে বুক পেতে শহীদ হন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর জনসাধারণের প্রবল প্রতিরোধে রাজশাহীতে সক্রিয় পাকবাহিনী অল্প কয়েক দিনের মধ্যে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়। এই সংগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। মনসুর রহমান খান সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী গ্রন্থ সূত্রে জানা যায়, মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. হবিবুর রহমান, ড. সুখরঞ্জন সমাদ্দর, মীর আবদুল কাইয়ুমসহ অন্তত ৩০ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্র শহীদ হন। নব্বইয়ের দশকে স্বৈরাচারী এরশাদবিরোধী আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। স্বৈরাচার হটাতে সেদিন রাজপথে জীবন দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও জাসদ নেতা শাজাহান সিরাজ।
চব্বিশের জুলাই বিপ্লবে প্রথম ছাত্রলীগমুক্ত ক্যাম্পাস : কোটা সংস্কার আন্দোলনে উত্তাল সময়ে ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগ। এ ঘটনায় প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ মুহূর্তেই অন্য ক্যাম্পাসগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৬ জুলাই দুপুর পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ভয়ভীতি দেখাতে থাকে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা। শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে টিকতে না পেরে কৌশলে বিনোদপুর এলাকায় জড়ো হন। তারা দুপুর সোয়া ২টার দিকে বিক্ষোভ নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন। মুহূর্তেই শত শত শিক্ষার্থীতে পূর্ণ হয় প্যারিস রোড। ছাত্রীরা হলগেটের তালা ভেঙে আন্দোলনে যুক্ত হন। শিক্ষার্থীরা বিশাল বিক্ষোভ নিয়ে অবস্থান নিলে ছাত্রলীগ সভাপতিসহ সব নেতা-কর্মী ক্যাম্পাস থেকে পালিয়ে যান। সে দিনই ছাত্রলীগের দখলকৃত হল-কক্ষ ভাঙচুর করে এবং ছাত্রলীগমুক্ত ক্যাম্পাস ঘোষণা করে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক মেহেদী সজিব বলেন, ১৬ জুলাই একটি ঐতিহাসিক দিন। এ দিনই দেশের প্রথম ক্যাম্পাস হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ বিতাড়িত হয় এবং আন্দোলন ভিন্ন মাত্রা পায়।
শাবাশ বাংলাদেশ ভাস্কর্য : ১৯৯১ সালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উজ্জীবিত রাখতে ক্যাম্পাসে নির্মিত হয় শাবাশ বাংলাদেশ ভাস্কর্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকতে বাম পাশে দৃষ্টিনন্দন স্থাপনাটি অবস্থিত। প্রকাশভঙ্গির সরলতা, গতিময়তা ও নন্দনতাত্ত্বিক দিক দিয়ে ভাস্কর্যটি অনবদ্য। চিত্রশিল্পী নিতুন কুণ্ডের কালজয়ী এই স্থাপনা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সর্বদা সংগ্রাম ও বিজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ছয় ফুট বেদির ওপর লাল বেলেমাটির তৈরি এই ভাস্কর্যে রাইফেল হাতে দুজন মুক্তিযোদ্ধাকে দেখা যায়। দুজনকেই খালি গায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। একজন লুঙ্গি পরিহিত এবং মাথায় গামছা বাঁধা গ্রামীণ যুবা কৃষক-সমাজের প্রতিনিধি। তার এক হাতে আছে রাইফেল এবং মুষ্টিবদ্ধ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অন্য হাতটি ওপরে উত্থিত। প্যান্ট পরিহিত অন্য যুবকটি শহুরে যুবকের প্রতিনিধিত্ব করছে। সে দুই হাত দিয়ে ধরে রেখেছে রাইফেল। কোমরে তার গামছা বাঁধা। বাতাসের ঝাপটায় চুলগুলো পেছনের দিকে সরে যাচ্ছে। সিঁড়ির ওপর মঞ্চের পেছনের দেয়ালগাত্রে নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ-সমাজের সব বয়সি মানুষের মিছিলের দৃশ্য। রাইফেল হাতে যুবক-যুবতী, একতারা হাতে বাউল, গেঞ্জি পরা এক কিশোর তাকিয়ে আছে পতাকার দিকে। মূল ভাস্কর্যের পেছনে রয়েছে ৩৬ ফুট উঁচু একটি স্তম্ভ ও ভিতরে রয়েছে পাঁচ ফুট ব্যাসের গোলাকার শূন্যতা, যা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকার প্রতীক। সব মিলিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে গণমানুষের সম্পৃক্ততার চিত্র ফুটে তোলা হয়েছে। ভাস্কর্যে তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার কয়েকটি লাইন স্থান পেয়েছে-
‘সাবাস, বাংলাদেশ,
এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়;
জ্বলে, পুড়ে-মরে ছারখার,
তবু মাথা নোয়াবার নয়।’
বধ্যভূমি স্মৃতিস্তম্ভ : শহীদ শামসুজ্জোহা হলের পূর্বদিকে সমতল থেকে ৪২ ফুট উঁচু সিমেন্টের গোলাকার বেদির ওপর এই স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। এই স্তম্ভ ক্যাম্পাসে সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের প্রেরণা। বিদ্যার্ঘ্য ভাস্কর্যমহান মুক্তিযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর অন্যতম লক্ষবস্তু ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। জাতিকে মেধাশূন্য করতে আলবদর ও রাজাকারদের সহায়তায় ক্যাম্পাসে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে হানাদার বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় ১৯৭১ সালে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গণিত বিভাগের শিক্ষক শহীদ হবিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ২০১১ সালে তাঁর ত্যাগ ও স্মৃতিকে স্মরণীয় রাখতে শহীদ হবিবুর রহমান হলের সামনে নির্মিত হয় বিদ্যার্ঘ্য স্মৃতিস্তম্ভ। স্থপতি শাওন সগীর সাগর তৈরিকৃত ষড়ভুজ আকৃতির এই ভাস্কর্যে দেখা যায়, প্রায় ৫ ফিট দৈর্ঘ্যরে দুজন মুক্তিযোদ্ধা সগর্বে দাঁড়িয়ে আছেন। একজনের হাতে বন্দুক এবং অন্যজনের হাতে কলম।
শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিফলক : মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে নির্মিত হয়েছে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিফলক। ২৬ ফুট দৈর্ঘ্য এবং সাত ফুট প্রস্থের কালো মার্বেল পাথরের বেদির ওপর সাদা দেয়াল। দেয়ালের পেছনের ’৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ’৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ’৬২-এর ছয়দফা, ’৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, গণ অভ্যুত্থানে শহীদ আসাদের মৃত্যু, দেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী ড. শামসুজ্জোহার মৃত্যু, এগারো দফা ও ’৭০-এর নির্বাচনের বিভিন্ন চিত্র ফুটে তোলা হয়েছে। সামনের দেয়ালের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শহীদ শিক্ষক ড. সুখরঞ্জন সমাদ্দার, শহীদ ড. হবিবুর রহমান ও মীর আবদুল কাইয়ূমের প্রতিকৃতি এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের প্রতিকৃতি রয়েছে।
আবেগ-প্রেম-বিদ্রোহের প্রতীক প্যারিস রোড : ক্যাম্পাসের জুবেরি ভবনের কিনারা থেকে শেরেবাংলা হল পর্যন্ত বিস্তৃত সড়কটি ‘প্যারিস রোড’ হিসেবে পরিচিত। ৫০ বছরেরও বেশি পুরনো এই রাস্তাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোর একটি অংশ। পিচঢালা প্রশস্ত এই সড়কটি সুবিশাল গগনশিরীষ বৃক্ষে আবৃত। ১৯৬৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও মনোরম করে তোলার জন্য তৎকালীন উপাচার্য এম শামসুল হক পাকিস্তানের করাচি থেকে এই গাছ নিয়ে আসেন। তবে এ নিয়ে একটা বিতর্ক আছে। আন্দোলন-সংগ্রাম, প্রেম ও আবেগের এক তীর্থস্থলে পরিণত হয়েছে এই সড়ক। যুগ যুগ ধরেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা জাতীয় স্বার্থ কিংবা অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এই সড়কে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন। এ ছাড়াও প্রেমিক যুগলের খুনশুটি ও শিক্ষার্থীদের আড্ডায় আবেগের প্রতীকে পরিণত হয়েছে প্যারিস রোড।
আধুনিক গবেষণায় দেশে অপার সম্ভাবনার হাতছানি : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের আধুনিক গবেষণা দেশের টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অসামান্য ভূমিকা রাখছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মনজুর হোসেনের নেতৃত্বে একদল গবেষক ১৭০ বছর পূর্বে হারিয়ে যাওয়া বাঙালির ঐতিহ্য ‘ঢাকাই মুসলিন’ বস্ত্র পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়েছেন। দেশ-বিদেশে ঘুরে এই সুতা সংগ্রহ এবং ডিএনএ পরীক্ষা করে দেশে ফুটি কার্পাস সংগ্রহ করেন গবেষক দল। নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে ক্যাম্পাসে সেই ফুটি কার্পাস চাষ করে সফলভাবে মুসলিন কাপড় তৈরি করেন তারা।
ড. হোসেন বলেন, ঢাকাই মসলিন বাংলাদেশের কেবল ঐতিহ্যই নয়, ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাইলফলকও বটে। সঠিকভাবে বিদেশে এই পণ্য বাজারজাত করতে পারলে বিলিয়ন ডলার আয়ের সুযোগ আছে।
বরেন্দ্র অঞ্চলের পানি সংকট নিরসন এবং বিকল্প উৎপাদন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক চৌধুরী সারওয়ার জাহান। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের যৌথ সহযোগিতায় ‘বরেন্দ্র অঞ্চলে পরিচালিত অ্যাকুইফার গবেষণার সম্ভাব্যতা’ বিষয়ক প্রকল্প পরিচালনা করছেন। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বরেন্দ্র অঞ্চলের পানি সংকট নিরসন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলে মনে করেন এই ভূ-তত্ত্ববিদ।
অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ বিভাগের তিন গবেষক বিভিন্ন প্রজাতির মাছ থেকে প্রোটিনসমৃদ্ধ পাঁচ ধরনের খাবার তৈরি করেছেন। এসব খাবারের মধ্যে রয়েছে ফিশবল (তেলাপিয়া ও টুনা), ফিশ সসেজ (পাঙ্গাশ ও ম্যাকরল), ব্যাটারড অ্যান্ড ব্রডেড ফিশ (তেলাপিয়া ও হোয়াইট স্যাপার), ফিশ মেরিনেডস (সারডাইন) এবং ফিস ক্র্যাকার্স (তেলাপিয়া ও টুনা)। গবেষক অধ্যাপক তরিকুল ইসলাম, অধ্যাপক ইয়ামিন হোসেন ও ড. সৈয়দা নুসরাত জাহান প্রথমবারের মতো দেশে মাছ থেকে এসব খাবার তৈরি করেন। এ ব্যাপারে ড. তরিকুল ইসলাম বলেন, মাছের বহুবিধ ব্যবহারে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান যেমন বাড়বে, তেমনি মানুষের স্বাস্থ্যকর প্রোটিনের চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে। এ ছাড়া বঙ্গোপসাগরে বেশ কিছু মাছে ভারী ধাতু এবং মাইক্রোপ্লাস্টিকের বায়ো-অ্যাভেলেবিলিটি ও বিষাক্ত শেলফিশের সন্ধান পেয়েছেন ড. ইয়ামিন হোসেন। এই অধ্যাপক বলেন, প্রতিদিনই উপকূলবর্তী রাখাইন সম্প্রদায় সামুদ্রিক মাছ গ্রহণ করে। এতে তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। কারণ শেল প্রজাতির মাছে ভারী ধাতু বিশেষ করে নিকেল, সিসা, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়ামের ঘনত্ব জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্ধারিত সর্বোচ্চ অনুমোদিত সীমার চেয়ে বেশি।
দেশে সর্বপ্রথম টিসু কালচার পদ্ধতি উচ্চ ফলনশীল কলা উৎপাদনে সফলতা পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন। ২০২০ সাল থেকে গবেষণা করে কলার উন্নত জাত মেহের সাগর, রঙিলা সাগর, জি৯, শবরী, অগ্নীশ্বর বা লাল কলার চারা উৎপাদন করেন তিনি। এই জাতের কলার চারা রোপণের ছয়-সাত মাসের মধ্যে মোচা বের হয়। ফলে সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে কৃষকরা ৩০-৪০ শতাংশ বেশি লাভবান হতে পারে।
এ ছাড়াও পাট ছাড়াই বিকল্প উপায়ে সোনালি আঁশ পাওয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন ফার্মেসি বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলাম। দেশে পাট চাষ উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেলেও এই বিকল্প ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করেন তিনি। ২০১০ সাল থেকে একদল গবেষককে সঙ্গে নিয়ে তুঁতের ক্যান্সার প্রতিরোধী ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের অধ্যাপক এ এইচ এম খুরশীদ আলম। ক্যানসার ছাড়াও হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, কিডনি রোগের প্রতিরোধক হিসেবে তুঁত কার্যকরী ভূমিকা রাখে বলে গবেষণায় পেয়েছেন তিনি।
৭৫০ একরজুড়ে উন্নত ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ : এই ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি সহপাঠ্য কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে উন্নত ক্যারিয়ার গড়ার নানা সুযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ক্যারিয়ার ক্লাব এ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীদের সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা শেখানোর পাশাপাশি সেবামূলক কার্যক্রমে অংশ নিতে উৎসাহ দেয় রোভার স্কাউট গ্রুপ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি)। বিজ্ঞানচর্চা, সামাজিক যোগাযোগ উন্নয়ন ও সমস্যা নিরসনে কাজ করে হায়ার স্টাডি ক্লাব, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), রোটারি ক্লাব ও পাঠক ফোরাম। বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহীদের জন্য রয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স ক্লাব, বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ ও এগ্রিকালচারাল ক্লাব। বিতর্কে আগ্রহীদের জন্য রয়েছে ডিবেটিং ফোরাম, গ্রুপ অব লিবারেল ডিবেটরস, ক্রিডেন্স, রেটোরিক। ক্যাম্পাসে মুক্ত সংস্কৃতিচর্চায় রয়েছে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক জোট এবং জোটভুক্ত সংগঠন বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থা, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, অনুশীলন নাট্যদল, সমকাল নাট্যচক্র, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ড্রামা অ্যাসোসিয়েশন (রুডা), তীর্থক নাটক, বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার রাজশাহী, অ্যাসোসিয়েশন ফর কালচার অ্যান্ড এডুকেশন (এস্), আবৃত্তির সংগঠন স্বনন ও ঐকতান। সাহিত্যচর্চার সংগঠন চিহ্ন, স্নান এবং চলচ্চিত্রবিষয়ক সংগঠন ম্যাজিক লণ্ঠন ও ফিল্ম সোসাইটি।