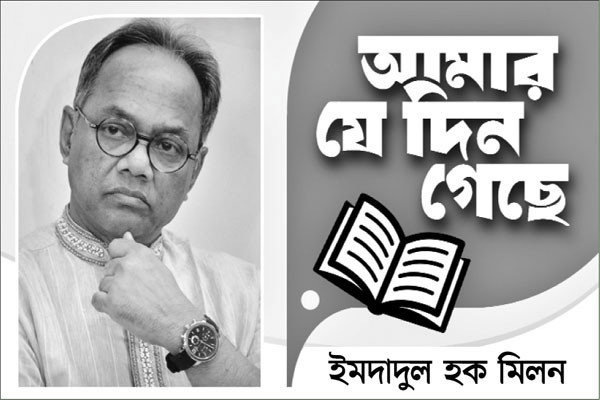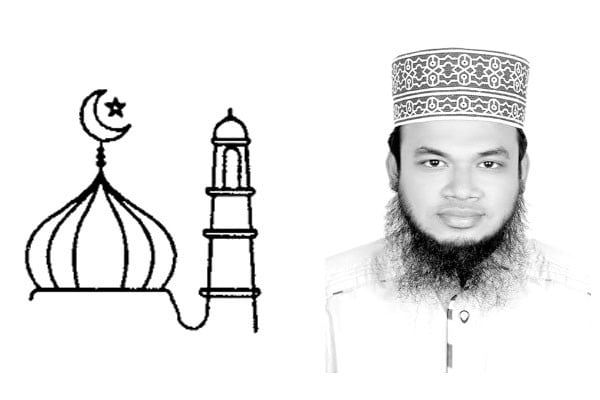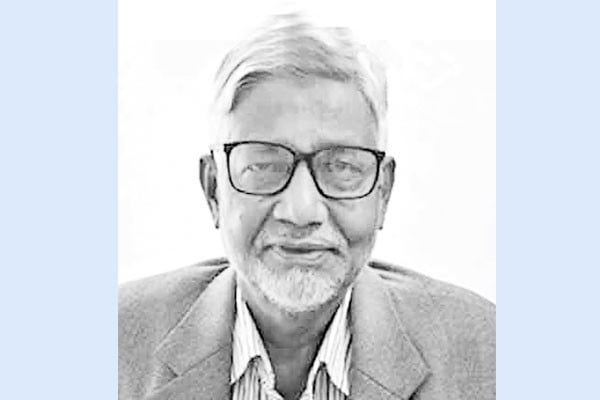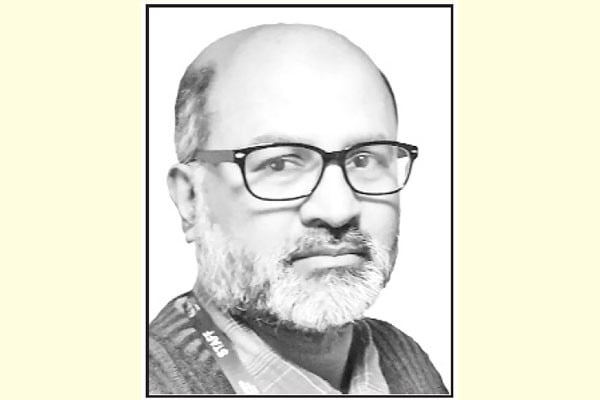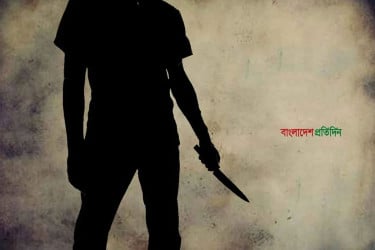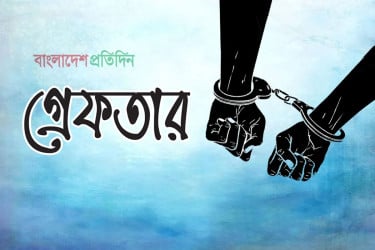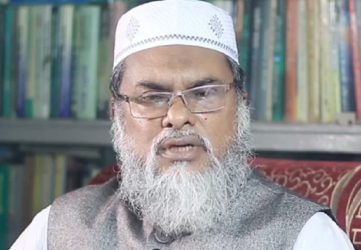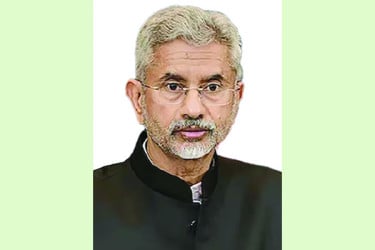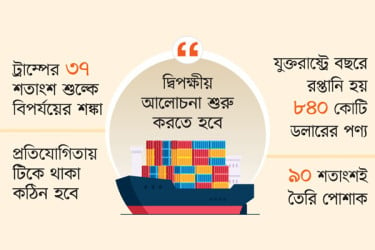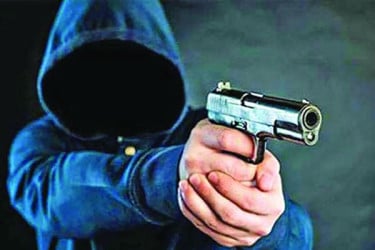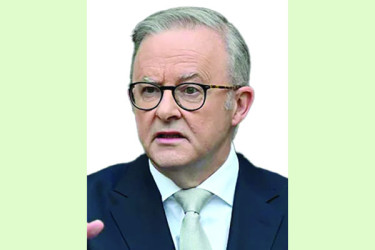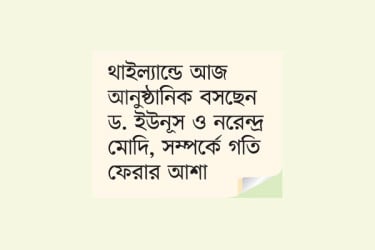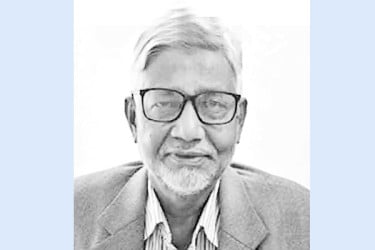ছেলেবেলা থেকেই ঢাকার গেন্ডারিয়া ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। নিজের আপন নানাকে দেখিনি। আমার বড় ভাইয়ের জন্মের আগে তিনি মারা গেছেন। নানির অনেকগুলো সন্তান হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিল দুই মেয়ে। মা আর পুনু খালা। টগর নামে একটি মামা পাঁচ-সাত বছর বয়স পেয়েছিলেন। নানি ছিলেন নানার দ্বিতীয় স্ত্রী। তাঁর নাম আম্বিয়া খাতুন। তিনি ছিলেন এক মহীয়সী নারী। আমার অনেক লেখায় নানির কথা আছে। যেমন ‘কেমন আছ, সবুজপাতা’। ‘নূরজাহান’ উপন্যাসেও চরিত্র হিসেবে আছেন তিনি। ‘একাত্তর ও একজন মা’ উপন্যাসে আছে তাঁর কথা। মানুষ যে মানুষকে কী পরিমাণ ভালোবাসতে পারে নানি ছিলেন তার বড় উদাহরণ। নাতিনাতনিরা ছিলেন তাঁর জান। আমার আত্মজৈবনিক গ্রন্থ ‘যে জীবন আমার ছিল’তে নানিকে বিস্তৃতভাবে পাওয়া যাবে। তাঁর কোনো বোন ছিল না। একটি মাত্র ছোট ভাই। মায়ের সেই মামার নাম আবুল হোসেন খান। ডাকনাম আবেদিন। লম্বা স্বাস্থ্যবান সুদর্শন পুরুষ। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছেন। রুচিশীল মানুষ। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করতেন। গল্প-উপন্যাস পড়ার অভ্যাস ছিল। অর্থাৎ সংস্কৃতিমনা মানুষ। তাঁর নয় সন্তানের প্রত্যেকেই রুচিশীল, সংস্কৃতিমনা ও শিক্ষিত।
মায়ের এই মামাকেই আমরা আপন নানা হিসেবে জানি। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে ঢাকায় চলে এসেছিলেন। সরকারি চাকরি করতেন। গেন্ডারিয়ার দীননাথ সেন রোডে বাড়ি করেছেন। বাড়িতে দোতলা টিনের ঘর। বাড়বাড়ির দিকে আমার টুনুমামা, অনুমামার পড়ার ঘর। সেটাকে বাংলাঘরও বলা হয়। বাড়ির সামনে অনেকগুলো লিচুগাছ। বাঁধানো ঘাটলার বড় একটা পুকুর। পুকুরটা কাদের জানি না। পুকুরের ওপাড়ে রেললাইন। ফুলবাড়িয়া স্টেশন থেকে নারায়ণগঞ্জ যায় রেলগাড়ি। ষাট দশকের একেবারে গোড়ার দিককার কথা। মেদিনীমণ্ডল গ্রাম থেকে আমাদের নিয়ে নানি এসেছেন তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে। ভাই আর তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্য অনেক রকমের পিঠা বানিয়ে এনেছেন। মাটির হাঁড়িতে করে আট-দশটা ইলিশ মাছ জ্বাল দিয়ে এনেছেন। বর্ষাকাল। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। দোতলা ঘরটির নিচতলায় নানি তাঁর ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছেন। মা আর পুনুখালা গল্প করছেন মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে। টিনের চালে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। বাড়িতে গ্রামোফোন আছে। আমরা বলি ‘কলের গান’। টুনু মামা ‘কলের গান’ বাজাচ্ছেন। কোনো বিকেলে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করছেন মিনু খালা। অনু মামা হয়তো বিমল মিত্রের ‘কড়ি দিয়ে কিনলাম’ পড়ছেন। আমার বড় বোন মণির বয়সি বীণা খালা। বড় ভাই আজাদের বয়সি মিন্টু মামা। খোকন মামা এই দুজনের চেয়ে একটু বড়। তারপরও তাদের তিনজনের একটা দল হয়েছে। মণি আছে বীণা খালার সঙ্গে। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু বীণা খালাকে দেখি। তার সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। অপূর্ব সুন্দরী বলতে যা বোঝায় সে তাই। বীণা খালার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হতো, সে বুঝি মানুষ নয়। পরি। পরিস্থান থেকে এই বাড়িতে চলে এসেছে। আমি মণি আর বীণা খালা এক ক্লাসেই পড়তাম। একটা সময়ে গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল খালার সঙ্গে। সে রবীন্দ্রসংগীত গায়। কবিতা লেখে। রবীন্দ্রসংগীতের সিডি বেরিয়েছে, কবিতার বই বেরিয়েছে। কবিতার বইয়ের ইংরেজি অনুবাদও বেরিয়েছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বাংলায় পড়েছে। বিয়ে হওয়ার পর চলে গেল আমেরিকায়। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে আমেরিকায়। আমার বড় বোনও তা-ই। দূরত্বের কারণে বীণা খালার সঙ্গে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়নি। একবার ফ্লোরিডায় গিয়ে ওর বাড়িতে তিন সপ্তাহের মতো ছিলাম।
আমার ছোট ভাই বাদলের বয়সি ছিল সেন্টু মামা। ভালো নাম সাঈদ হোসেন। অল্প বয়সে বাদল ও সেন্টু মামা দুজনেই চলে গেল। সেন্টু মামা ছিল বিটিভির মিউজিক ডিরেক্টর। একেবারে ছোট খালাটির ডাকনাম দীনা। ভালো নাম লায়লা শারমিন। সে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পেইন্টার। কানাডায় থাকে। সবার বড় টুনু মামাও থাকেন কানাডায়। মিন্টু মামা, বীণা খালা আর রিনা আমেরিকায়। মিনু খালা আর অনু মামা মারা গেছেন। দোতলা টিনের ঘরওয়ালা বাড়িটি এখন ছয়তলা আধুনিক বাড়ি। আমার চোখে লেগে থাকা আর স্মৃতিজাগানিয়া সেই বাড়িটি সময়ের সঙ্গে বদলে গেছে। জীবনের অনেকগুলো বছর এই বাড়িটি ছিল আমার সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা। বীণা খালা সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। দিনগুলো ছিল গান আর গল্পকাহিনির সৌরভে ভরা। কাঠের দোতলায় আমরা ছোটরা সার ধরে শুয়ে আছি। হয়তো শীতকাল। ভোর রাতে হুইসেল বাজিয়ে রেলগাড়ি যাচ্ছে। আমার ঘুম ভেঙে গেছে। দোতলার জানালা খুলে রেললাইনের দিকে তাকিয়ে আছি। লিচুগাছগুলো আর পুকুরটার দিকে তাকিয়ে আছি। কুয়াশা এমন করে পড়েছে, যেন বিশাল সাদা একটা মশারি টানিয়ে দেওয়া হয়েছে চারদিককার ভুবনে। আমার বইপড়া আর গান শোনার রুচি তৈরি হয়েছিল এই বাড়ি থেকে। টুনু মামা কলেজে পড়েন। যে কোনো নতুন গানের রেকর্ড বেরোলে সেই রেকর্ড কিনে আনেন। কলের গানে বাজান। ফাগুন দিনের দুপুরবেলার পরের সময়টি স্নিগ্ধ হয়ে থাকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানে। এক বর্ষা দুপুরে রেকর্ডে বেজেছিল ‘আমি বন্ধুবিহীন একা/বাহিরে বাদল ঝরে, ঝর ঝর অবিরল ধারে’। কোনো কোনো বর্ষামুখর দিনে সেই দূর অতীতকাল থেকে হেমন্তের এই গানের কয়েকটি লাইন এখনো কানে ভেসে আসে। আমি আচ্ছন্ন হয়ে যাই। ছেলেবেলার বহু মধুর স্মৃতি ওই বাড়ি ঘিরে।
জিন্দাবাহারের বাসা থেকেও গেন্ডারিয়ায় বেড়াতে আসতাম আমরা। গলির মুখে দুটো রিকশা এসে দাঁড়াত। আমরা ছোট ছোট অনেকগুলো ভাইবোন। এক রিকশায় জায়গা হবে না। মায়ের সঙ্গে এক রিকশায় উঠেছে কেউ কেউ। আব্বার সঙ্গে উঠেছে কেউ কেউ। জিন্দাবাহারের গলি থেকে বেরিয়ে পূর্ব দিকে পাটুয়াটুলী পেরিয়ে সদরঘাটের মোড়। রিকশা ঢুকে গেছে বাংলাবাজারের রাস্তায়। তারপর শ্যামবাজারের ওদিক দিয়ে লোহারপুলের সামনে এসে সবাইকে রিকশা থেকে নামতে হয়েছে। অত উঁচু পুলে এত লোক টেনে তুলতে পারবে না রিকশাওয়ালা। পুলের ওপরে গিয়ে আবার রিকশা চড়া হয়েছে। ওপারের ঢালুতে গিয়ে সাঁ সাঁ করে নেমে গেছে রিকশা। আমার বুকজুড়ে কী গভীর উত্তেজনা। টুনু মামাদের বাড়িতে গিয়ে পাঁচ-সাত দিন থাকা হবে। সেই আনন্দের কোনো তুলনা হয় না।
জিন্দাবাহার থেকে বাসা বদলে আব্বা চলে এলেন গেন্ডারিয়াতে। ধূপখোলা মাঠের পাশেই ডিস্টিলারি রোডের একটি গলিতে বাসা। এই বাড়িটাও জিন্দাবাহারের বাড়ির মতো। অনেকগুলো ঘর। স্কুলঘরের মতো লম্বা ঘরগুলোর মেঝে পাকা। চারদিকে দেয়াল। মাথার ওপর টিনের চালা। ছোট বারান্দাও আছে। তবে জিন্দাবাহারের বাড়ির মতো পুরনো বাড়ি না। সোঁদা গন্ধ নেই। গলির ধারে বাড়ি। নতুন। পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। আব্বা একটি রুম ভাড়া নিয়েছেন। রাস্তার ধারে জানালা। বাড়ির মালিক স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁর নাম জামাল মিয়া। ওই বাড়িটাকে লোকে বলে ‘জামাল মিয়ার বাড়ি’। এই বাড়ির উল্টো পাশেরও আরেকটা বাড়ি তাঁর। একই রকমের বাড়ি। প্রচুর ছোট ছোট ঘর। প্রচুর ভাড়াটে। বাড়ি দুটো ভাড়া দেওয়ার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। আমাদের নিয়ে মা তখন মেদিনীমণ্ডল গ্রামে। আমি পড়ি ক্লাস ফোরে। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ঢাকায় এসেছিলাম। এই বাড়ির কথা লিখেছি ‘মায়ানগর’ উপন্যাসে। মা আমার ছোট ছোট ভাইবোনদের নিয়ে এই বাসায় এসে উঠেছিলেন। আমি, আমার বড় ভাই আর মণি তখন নানির কাছে। ওই ছোট এক রুমের বাসায় সবার জায়গা হবে না। এক বছর পর ’৬৫ সালের বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে পাকাপাকি চলে এলাম ঢাকায়। আব্বা তত দিনে বাসা বদল করেছেন। ডিস্টিলারি রোডেই উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি দরিদ্র এলাকা। চারদিকে অনেক বাড়ি। বেশির ভাগ বাড়িতেই বাঁশের বেড়া দেওয়া টিনের ঘর। দুয়েকটা একতলা দালান আর টিনশেডের পুরনো বাড়িও আছে। জায়গাটার নাম মুরগিটোলা। ওই সব বাড়িঘরের মাঝখানে বড় বড় দুটো কামরার একতলা একটি দালান বাড়ি। সামনে এক টুকরো উঠোন। দুদিকে দুটো গেট আছে ঢোকার। কাঠা তিনেক জমির ওপর বাড়ি। আব্বা মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকরি করেন। সেখানে কন্ট্রাক্টরি করেন মুরগিটোলার স্থায়ী বাসিন্দা আফতাব মিয়া। এই বাড়িটি তাঁর। আব্বাকে ভাড়া দিয়েছেন। পূর্ব দিকে আরেকটা বাড়ি আছে আফতাব মিয়ার। সেই বাড়িতে সপরিবারে থাকেন। আমাদের বাড়িটির ভাড়া ছিল ১০০ টাকা। মুরগিটোলার এই বাড়ির বিশদ বিবরণ লিখেছিলাম ‘মায়ানগর’ উপন্যাসে। ‘একাত্তর ও একজন মা’ উপন্যাসেও এই বাড়ির কথা আছে। আফতাব মিয়ার বাড়িটির উত্তর দিকে বিশাল পুকুর। পুকুরের উত্তর পাড়ে লম্বা জমিতে আখ চাষ হয়। এলাকার লোকে আখকে বলে ‘গেন্ডারি’। সেই জমির উত্তর পাশেই ধোলাইখাল। দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা থেকে এসে সূত্রাপুরের লোহারপুল, ভাটিখানার কাঠেরপুলের তলা দিয়ে মুরগিটোলার দিকে এসে বেঁকে একটা মাথা চলে গেছে উত্তর-পশ্চিমে নারিন্দার দিকে। অন্য মাথাটি পুবদিকে বেঁকে রেলপুলের তলা দিয়ে চলে গেছে ধোলাইরপাড় যাত্রাবাড়ীর দিকে। গ্রীষ্মকালে খালে তেমন পানি থাকে না। বর্ষাকালে টইটম্বুর। ছোট বড় অনেক নৌকা চলাচল করে। পানিটা খুবই স্বচ্ছ। বাড়ির পেছনের পুকুরের পানিও পরিষ্কার ছিল। আশপাশের বাড়িগুলোর মহিলারা ধোয়া পাকলার কাজ করত। গোসল করত সবাই। এই পুকুরে ডুবে আমার পাগল নানি মারা গিয়েছিলেন। আমাদের বাড়ির উত্তর পাশের বাড়িটি অনেক বড়। টিনের চালা আর বাঁশের বেড়ার ঘর। পনেরো বিশঘর ভাড়াটে। বছরে এক-দুবার রেডিওতে গান গায় শাহাবুদ্দিন বয়াতি। ও রকম একটা ঘরে তিনি থাকেন। তাঁর তুলনায় স্ত্রীর বয়স অনেক কম। যুবক হয়ে ওঠা ছেলেটির নাম মোহাম্মদ আলী। ক্লাস এইট-নাইনে পড়ে। দেখতে সুন্দর। নিয়মিত ব্যায়াম করা স্বাস্থ্য। সুন্দর পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়। ফ্যাশনসচেতন। পাড়ার কাউকে তেমন পাত্তা দেয় না। বেশ উগ্র। পশ্চিম পাশের বাড়িটাও ঠিক ও রকমই। সেই বাড়িতেও পনেরো-বিশটি ঘর। নানা রকমের ভাড়াটে। প্রধান ভাড়াটের নাম করিম সর্দার। আমাদের বাড়ির লাগোয়া দুটো ঘর নিয়ে তাঁর অংশটুকু প্রায় আলাদা। তাঁর বড় ছেলেটি আমার বয়সি। তারও নাম মোহাম্মদ আলী। সবাই ‘আলী’ বলে ডাকে। এই ‘আলী’ হচ্ছে ঢাকায় আমার প্রথম বন্ধু।
’৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত-পাকিস্তান একটা যুদ্ধ লেগে গেল। তখনকার দিনে ‘ভারত’ শব্দটা সেভাবে কেউ বলত না, বলত ‘ইন্ডিয়া’। ইন্ডিয়া-পাকিস্তান যুদ্ধের তারিখটা আমার পরিষ্কার মনে আছে। ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫। আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। স্কুল ছুটি ছিল। বিক্রমপুর থেকে ঢাকায় এসেছি। চারদিকে যুদ্ধের উত্তেজনা। অফিস থেকে বাড়িতে এসে প্রতিদিনই যুদ্ধের নানা রকম ঘটনা বলেন আব্বা, শুনে আমরা উত্তেজিত হই। চীন দাঁড়িয়ে গেছে পাকিস্তানের পক্ষে। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। সবাই মনে করে এই যুদ্ধে পাকিস্তানের জয় অবধারিত। নানা রকমের গুজব চারদিকে। যুদ্ধের সময় বারুদের গন্ধের মতো হাওয়ায় ভাসে গুজব। সেই সময়ও গুজবের অন্ত ছিল না। যে কোনো অচেনা লোক দেখলেই মানুষ তাদের ‘ইন্ডিয়ান স্পাই’ হিসেবে ধরে। আমাদের বাড়ির দক্ষিণে শখানেক পা গেলেই পাকা মসজিদ। সেই মসজিদের সামনে এক সন্ধ্যায় বিরাট হৈচৈ। কী হয়েছে? কে একজন ছুটে এসে বলল, ‘ইন্ডয়ার স্পাই ধরা পড়ছে’। পাড়ার শিশু-কিশোরদের সঙ্গে আমিও ছুটে গেছি। গিয়ে দেখি ভিড়ের মধ্যে অতি দীন-দরিদ্র ধরনের লুঙ্গি গেঞ্জি আর ছেঁড়া চাদর পরা অসহায় চেহারার একজন মধ্যবয়সি মানুষ। সে কাঁদতে কাঁদতে জোড় হাতে অনুনয়-বিনয় করছে। ‘ভাই আপনেরা আমারে বিশ্বাস করেন। আল্লাহর কসম, আমি গরিব মানুষ। ফরিদপুর থিকা ঢাকায় আইছি জোগালুর কাম করতে। আমি ইন্ডিয়া-পাকিস্তান বুঝি না। আইছি পেটের ধান্ধায়। দুই দিন ধইরা কামও পাই না, খাইতেও পাই না।’ তার কথা কেউ বিশ্বাসই করল না। কয়েকজন ঢাকাইয়া উগ্র যুবক কিলঘুসি চড় চাপড় মারতে লাগল তাকে। সঙ্গে কুৎসিত ভাষার গালাগাল। লোকটা তখন মাটিতে পড়ে গেছে। নাকমুখ দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ছে। তখন সে দুহাত মোনাজাতের ভঙ্গিতে তুলল। উচ্চৈঃস্বরে ‘আয়াতুল কুরসি’ পড়তে লাগল। শুনে লোকজন হতভম্ব। মসজিদের ইমাম সাহেব অল্প বয়সি। নুরানি চেহারা। ধীর শান্ত নম্র মানুষ। তিনি ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। দুহাত তুলে সবাইকে থামালেন। বললেন, “মানুষটার গায়ে দয়া করে আপনারা আর হাত দেবেন না। সে ‘স্পাই’ না। এ রকম মানুষের গায়ে হাত তুললে আল্লাহপাক নারাজ হবেন।” মানুষটিকে বাঁচিয়ে দিলেন ইমাম সাহেব। সবাই ধরাধরি করে তাকে মসজিদের ভিতর নিয়ে গেল। মানুষটি তখনো সমানে কাঁদছে আর একটার পর একটা সুরা পাঠ করছে। ’৬৫ সালের যুদ্ধের কথা মনে পড়লেই সেই মানুষটির মুখ আমি চোখের সামনে দেখতে পাই। জীবনের অনেকগুলো দিন তার কথা ভেবে কেটেছে। ক্ষুধার্ত অসহায় একজন মানুষ বাঁচার আশায় এসেছিল ঢাকায়। কী দুর্ভাগ্য তার! খাবারের পরিবর্তে কপালে জুটল ব্যাপক প্রহার। যুদ্ধের ডামাডোল এক অসহায় মানুষকে প্রহারের সঙ্গে করল চূড়ান্ত অপমান। মসজিদের তরুণ ইমাম মানুষটি যেন ফেরেশতা হয়ে সেই ভিড়ের মধ্যে এসেছিলেন। অসহায় মানুষটিকে বাঁচিয়েছিলেন। সেই সন্ধ্যাটির কথা আজও আমি ভুলতে পারিনি।
লেখক : কথাসাহিত্যিক