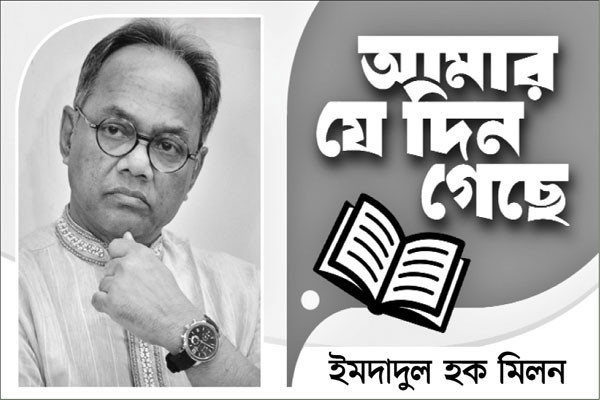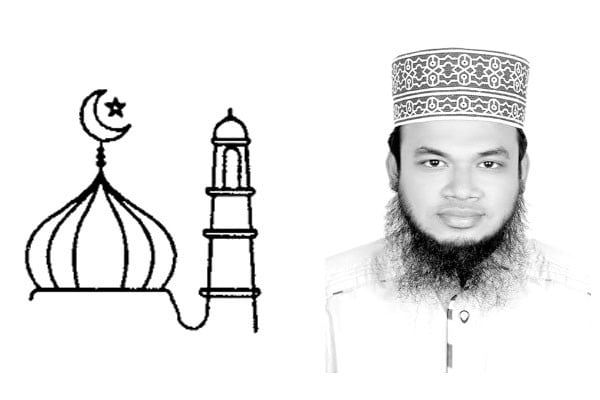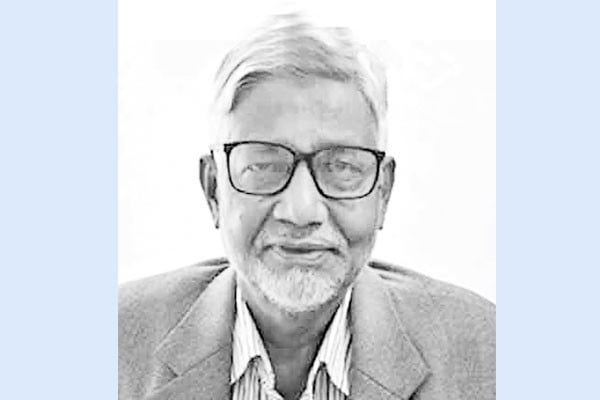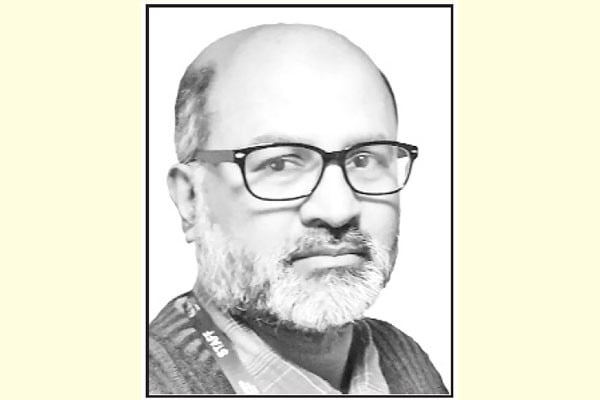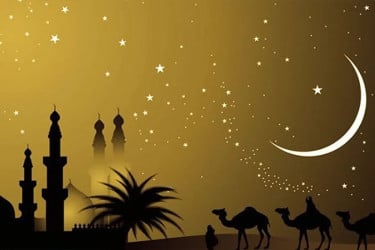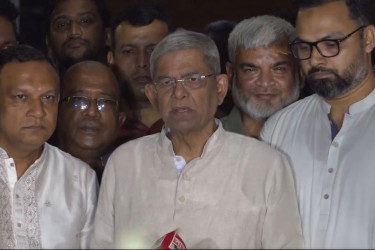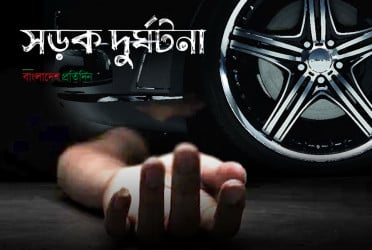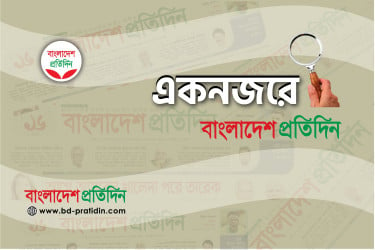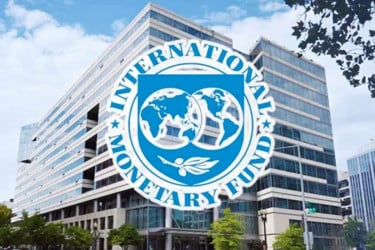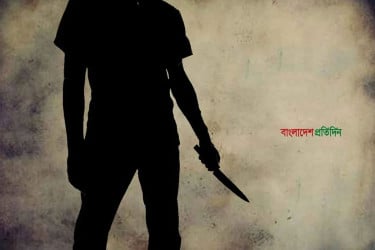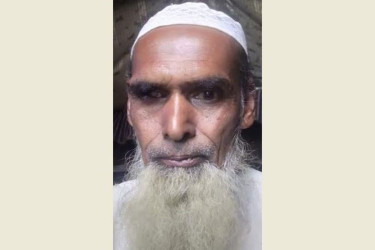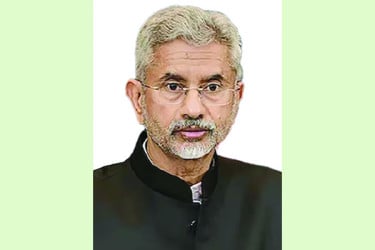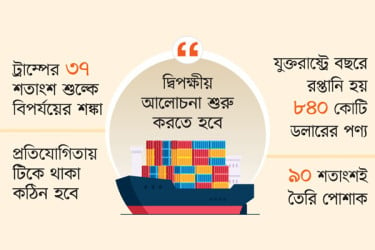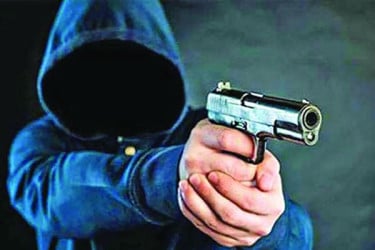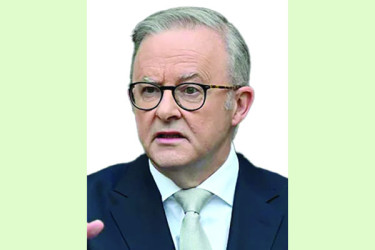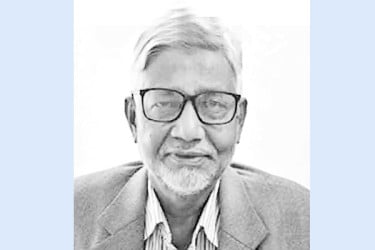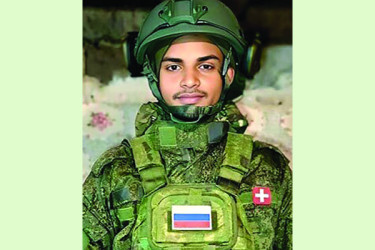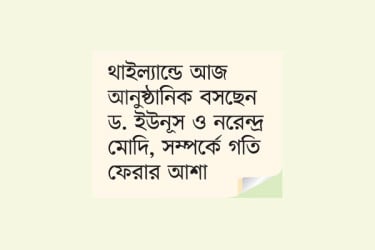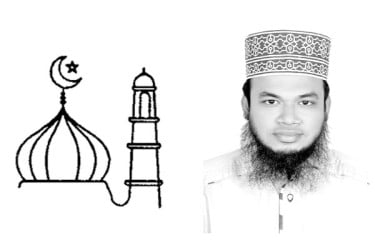সূত্রাপুর বাজারের পশ্চিম পাশের সরু একটা গলি। শেষ বিকালে সেই গলির অতি পুরনো একতলা একটা বাড়িতে আব্বা আমাকে নিয়ে গেছেন। এ বাড়ির ক্লাস টুতে পড়া মেয়েটিকে পড়াতে হবে। ’৬৯ সালের কথা। আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। যে ভদ্রলোকের মেয়েকে পড়াতে হবে তিনি ছোট একজন ব্যবসায়ী। সূত্রাপুরের স্থায়ী বাসিন্দা। বাড়ির লোকজন ঢাকাইয়া ভাষায় কথা বলে। ভদ্রলোক আব্বার পরিচিত। আমাকে বেতন দেওয়া হবে ১০ টাকা। গভীর আগ্রহ নিয়ে জীবনের প্রথম টিউশনি শুরু করলাম। শিক্ষক ক্লাস নাইনের ছাত্র। ছাত্রী ক্লাস টু। বিকালবেলা পড়াতে যাই। সন্ধ্যায় ফিরে আসি। নিজের পড়াশোনা আছে। গেন্ডারিয়া হাইস্কুলের সায়েন্সের ছাত্র। পড়াশোনায় মোটামুটি ভালো। স্যাররা বিশেষ নজরে দেখেন। ভালোবাসেন। স্কুলে ফুল ফ্রি। বেতন দিতে হয় না। আব্বার চাকরি নেই। কষ্টের দিন। টিউশনি করে ১০ টাকা রোজগার করতে পারলে নিজের পয়সায় খাতাপত্র কিনতে পারব। আব্বার ওপর চাপ পড়বে না। আমার বড় ভাই এসএসসি পাস করেছে। নাইট শিফটে জগন্নাথে পড়ে। সে-ও টিউশনি করে। স্কুল থেকে ফিরে চলে যেতাম টিউশনিতে। আমার খুব খিদে পেত। ছাত্রীর বাড়িতে কখনো কখনো এক কাপ চা আর একটা টোস্ট বিস্কুট দিত। কখনো কখনো এক টুকরো আমের মোরব্বা। খুবই আগ্রহ নিয়ে খেতাম। দেখতে দেখতে মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু বেতনের ১০টা টাকা আর দেয় না। রোজ টিউশনিতে যাই। রোজই ভাবি আজ টাকাটা পাব। টাকা আর পাই না। আব্বাকে বললাম। তিনি বললেন, ‘চাইতে হবে তো।’ পরদিন চাইলাম। ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন। টাকা দিতে হবে? ব্যাপারটার আগামাথা আমি কিছুই বুঝলাম না। আব্বা তো বলেছেন ১০ টাকা করে পাওয়া যাবে। তাহলে? ভদ্রলোক ভেবেছেন, পরিচিত লোকের ছেলে, মাগনাই তাঁর মেয়েকে পড়াবে? এ নিয়ে কি আব্বার সঙ্গে তাঁর কোনো কথা হয়নি? না হয়ে থাকলে ১০ টাকার কথা আব্বা আমাকে বলবেন কেন? ভদ্রলোক কি ইচ্ছা করেই এমন করছেন? দু-তিন দিন পর ১০টা টাকা তিনি আমাকে দিলেন। জীবনে সেই আমার প্রথম রোজগার। কী যে আনন্দিত হয়েছিলাম! বছরখানেক সেই মেয়েটিকে আমি পড়িয়েছি। গেন্ডারিয়ার রজনী চৌধুরী রোডে থাকি। স্কুল থেকে ফিরেই টিউশনিতে চলে যাই। ঘণ্টাখানেক মেয়েটিকে পড়াই। তত দিনে আরেকটা টিউশনি পেয়েছি। এ ভদ্রলোকও আব্বার পরিচিত। লোহারপুলের পশ্চিম দিককার ঢালের গলির ভিতর বাড়ি। নাম শামসুদ্দিন। ওই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা। অত্যন্ত সজ্জন মানুষ। মিউনিসিপ্যালিটিতে কন্ট্রাক্টরি করেন। অবস্থা ভালো। তাঁর মেয়েটি পড়ে ক্লাস থ্রিতে। পড়াতে হবে সকালবেলায়। বেতন ১৫ টাকা। আমাদের বাসার বেশ কাছে। আমি উঠি ভোর ৫টার দিকে। নিজের পড়া শেষ করে নাশতা করে চলে যাই ছাত্রী পড়াতে। ফিরে এসে যাই স্কুলে। বিকালে বন্ধুরা ধূপখোলা মাঠে খেলতে যায়। আমি যাই টিউশনিতে। ’৭০ সাল এলো। পড়ার চাপ অনেক। সামনে এসএসসি পরীক্ষা। সব সামলে টিউশনি দুটো চালিয়ে যাচ্ছি। ওদিকে আমাদের সায়েন্স গ্রুপের প্রত্যেকেই প্রাইভেট পড়তে শুরু করেছে। বিশেষ প্রিপারেশন নিচ্ছে পরীক্ষার। আমি ইলেকটিভ ম্যাথমেটিকস তেমন বুঝি না। বিষয়টির তুখোড় শিক্ষক ফখরুল স্যার। তিনি থাকেন স্কুলের কাছেই। ছুটির পর তাঁর বাড়িতে গিয়ে ব্যাচে পড়ে বন্ধুরা। আমি পড়ব কেমন করে? মাসে ২০ টাকা করে দিতে হবে। স্যার একদিন বললেন, ‘তুই আসিস না কেন?’ সমস্যাটা বললাম। শুনে স্যার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘টাকা দিতে হবে না। আজ থেকেই বাসায় আসবি।’ আহা রে, গেন্ডারিয়া হাইস্কুলের স্যাররা আমাকে কী ভালো যে বাসতেন! বি. রহমান স্যার ব্যাচে বাংলা পড়াতেন। তিনিও টাকা নিতেন না। আশু স্যার কখনো কখনো আমাদের বাসায় এসে আমাকে পড়িয়ে যেতেন। টাকা দেওয়া তো দূরের কথা, স্যারকে এক কাপ চা-ও খাওয়াতে পারতাম না। আমার ইংরেজি টিচার রউফ স্যার নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে আমার এসএসসির ফরম ফিলাপ করে দিয়েছিলেন। জেনারেল ম্যাথ অনেক দিন স্কুল শেষে আমাদের কয়েকজনকে অতিযত্নে পড়াতেন এ রহমান স্যার। সবাই টাকা দিত। আমি দিতে পারতাম না। স্যার চাইতেনও না। গেন্ডারিয়া হাইস্কুলের সেসব মহান শিক্ষকের ঋণ এক জীবনে শোধ করা যাবে না।
’৭০ সালের শেষদিকে মিউনিসিপ্যালিটির চাকরি ফিরে পেলেন আব্বা। প্রায় চার বছর চাকরি ছিল না। সেই চার বছরের পুরো বেতনটা পেয়ে গেলেন। কারণ তাঁকে অবৈধভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল। আমাদের কষ্টের দিন শেষ হয়ে এলো। তবে ওই চারটি বছর অতিকষ্টে দিন কেটেছে। নিয়মিত ভাড়া দেওয়া যাচ্ছিল না বলে একের পর এক বাসা বদলাতে হচ্ছিল। মুরগিটোলার বাড়ি থেকে যেতে হয়েছিল রজনী চৌধুরী রোডের বাড়িতে। সেখান থেকে গেন্ডারিয়া স্টেশনের কাছে ডিআইটি প্লটে। ওদিকটায় তখনো তেমন বাড়িঘর হয়নি। পুরো এলাকাটা যেন বিশাল একখানা মাঠ। সেই মাঠের এদিক-ওদিক ছড়ানো ছিটানো দু-চারটা বাড়ি। নতুন নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে অনেক। স্টেক দেওয়া ইট, রড, বালু পড়ে আছে একেকটা প্লটের সামনে। দিঘির মতো বিশাল একখানা পুকুর আছে। স্টেশনের রাস্তায় কিছু দোকানপাট। ওদিককার এক বাড়িতে থাকা হলো কয়েক মাস। বর্ষাকালটা কেটেছিল সেই বাড়িতে। বড় একটা কামরায় আমরা সবাই থাকতাম। সে বছর বন্যা হলো। ডিআইটি প্লট ডুবে গেল। কোমরপানি ভেঙে চলাচল করতে হয়। আমাদের স্কুলে বন্যার্তদের জন্য আশ্রয়শিবির খোলা হয়েছে। এলাকার লোকজন আর ছাত্ররা মিলে তাদের দেখভাল করছে। রেডক্রসের লোকজন এসে বস্তা বস্তা পাউডার দুধ দিয়ে যেত। বন্ধুদের সঙ্গে আমিও আছি বন্যার্তদের কাজে। মুঠো মুঠো পাউডার দুধ খেতাম। খুবই টেস্টি ছিল জিনিসটা। তখনকার দিনে ওই পাউডার দুধ আমাদের কাছে অতি মহার্ঘ খাবার।
ডিআইটি প্লট থেকে বাসা বদলে যেতে হয়েছিল ঘুণ্টিঘরের ওদিককার মসজিদের উল্টোদিককার গলির ভিতর অতি পুরনো, প্রায় ভেঙে পড়া বিশাল একটা নর্দমার পাশের কাঠাখানেক জমির ওপর একটা বাড়িতে। ছোট ছোট দুটো রুম। ভাপসা গন্ধে ভরা। ওই বাড়িটায় বোধ হয় কয়েক মাস থাকা হয়েছিল। সেখান থেকে যেতে হয়েছিল রেললাইনের ওপারে গ্রামের দরিদ্র বাড়ির মতো একটি বাড়িতে। এক ঘরে থাকার জায়গা হতো না বলে আমি চলে যেতাম মুরগিটোলার পুকুরটির ওপারে আলীদের বাড়িতে। আলীর বাবা একতলা ভারি সুন্দর একটা বাড়ি করেছেন ধোলাইখালের ধারে। আমি রাতে গিয়ে আলীদের বাড়িতে থাকতাম। তার কিছুদিন পরই চাকরি ফিরে পেলেন আব্বা। প্রায় রাতারাতি আমরা ঋণমুক্ত হলাম। সুখের হাওয়া বইতে লাগল সংসারে। রেললাইনের ওপারকার সেই বাড়ি থেকে চলে এলাম সাবেক শরাফতগঞ্জ লেনের একটা বাড়িতে। ’৭১ সাল এলো। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। আমাদের সুখের সময় বেশি দিন স্থায়ী হলো না। অক্টোবরের ৬ তারিখ সন্ধ্যায় আব্বা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ‘নার্ভাস ব্রেক ডাউন’ হয়েছিল। কারণ এক কাবুলিওয়ালা মিলিশিয়া নিয়ে এসেছিল আমাদের গেটে। কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে সুদে টাকা নিয়েছিলেন আব্বা। সেই টাকা সুদসহ পুরোটা শোধ করেছেন। তারপরও লোকটা অতিরিক্ত সুযোগ নেওয়ার লোভে আব্বাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার থ্রেট দিয়ে গেল। আব্বা তখন বাসায় ছিলেন না। ফিরে এসে সব শুনে অসুস্থ হয়ে গেলেন। সেই অবস্থায় বাড়িওয়ালার বড় ছেলে কাশেম ভাইয়ের সহযোগিতায় আমি আর আমার বড় ভাই মিলে একটা বেবিট্যাক্সিতে করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গিয়েছিলাম আব্বাকে। রাত ১টায় তিনি মারা গেলেন। আব্বার মৃত্যুর অনুপুঙ্খ বিবরণ ও তাঁর মৃত্যুর পর ১০টি নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার মায়ের যে লড়াই সেই লড়াইয়ের কথা লিখেছি ‘একাত্তর ও একজন মা’ উপন্যাসে।
আব্বা মারা যাওয়ার পর সাবেক শরাফতগঞ্জ লেনের ওই বাড়িটাতেই আমরা রয়ে গিয়েছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। তবে গেন্ডারিয়ার ওদিকটা নিরাপদ ছিল। পাকিস্তানিদের আনাগোনা সেভাবে ছিল না। আমাদের বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের বড় মেয়ের নাম খালেদা বারি। তিনি ডাক্তার। তাঁর স্বামী অত্যন্ত বিনয়ী ভদ্রলোক। খুবই স্নেহপরায়ণ ও দয়ালু। ওই বাড়িতেই থাকতেন। আমাদের পরিবারটির প্রতি বাড়িওয়ালার পরিবারের প্রত্যেকেরই বিশেষ সহানুভূতির দৃষ্টি ছিল। আব্বার মৃত্যু আমাকে খুবই কাতর করে তুলেছিল। চার দিন বাকরুদ্ধ ছিলাম। একটি কথাও বলিনি কারও সঙ্গে। আমার বন্ধু হামিদুল সেই চারটা দিন সারাক্ষণ আমার সঙ্গে। আমাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে প্রতিটি মুহূর্ত। তারপরও পিতা হারানোর শোক আমি কিছুতেই কাটাতে পারছিলাম না। খালেদা আপার স্বামীর নাম হানিফ সাহেব। তিনি আমাকে লক্ষ করতেন। চুপচাপ কোথাও বসে থাকি তো বসেই থাকি। যখন-তখন জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদি। একদিন দুপুরের পর তিনি আমাকে ডাকলেন। আমার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে গভীর মায়াবী গলায় বললেন, ‘চল আমার সঙ্গে। তোমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাব।’ তিনি আমাকে নিয়ে এলেন আমাদের সেই পুরনো বাড়ির এলাকা মুরগিটোলায়। মসজিদের উল্টোদিকে হাই সাহেবের তিনতলা বিশাল বাড়ি। হাই সাহেব মুরগিটোলার নামকরা বড়লোক। আরামবাগে তাদের ‘হাই আয়রন ইন্ডাস্ট্রি’ নামে ইন্ডাস্ট্রি আছে। মুরগিটোলায় থাকার সময় হাই সাহেবের দুই মেয়ের সঙ্গে আমার বোনদের বন্ধুত্ব ছিল। বড় মেয়ের নাম কোকিলা। মেজজনের নাম আঙ্গুরি। হানিফ সাহেব আমাকে সেই বাড়িতে নিয়ে এলেন। তখনো আমি কিছু বুঝতেই পারছি না। আমরা তাঁকে দুলাভাই ডাকি। দুলাভাই আমাকে কেন এ বাড়িতে নিয়ে এসেছেন? সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে তিনি জানালেন, এ বাড়ির তিনতলার ফ্ল্যাটে তাঁর প্রথম স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকেন। বড় দুই ছেলের বিয়ে হয়েছে। মেয়েদের কারও এখনো বিয়ে হয়নি। বড় মেয়ে ডাক্তারি পড়ছে। কিন্তু এ বাড়িতে আমাকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য কী?
তিনতলায় উঠেই সিঁড়িকোঠা। তারপর অনেকখানি খোলা ছাদ। ছাদ দক্ষিণমুখী। উত্তরদিকটা পূর্বদিকে বাঁক নিয়েছে। সেখানটায় চার কামরার একটা ফ্ল্যাট। আমাকে বসার ঘরে নিয়ে বসানো হলো। অত্যন্ত ছিমছাম পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। পড়ার টেবিল চেয়ার আছে। টেবিলে ক্লাস নাইনের বই। আমাকে চা-বিস্কুট দেওয়া হলো। দুলাভাই ভিতরে চলে গেছেন। আমি বসে আছি একা। বিস্কুট খেয়ে চায়ে চুমুক দিয়েছি। মনের ভিতর নানা প্রশ্নের আনাগোনা। দুলাভাই আমাকে কেন তাঁর এ পরিবারের কাছে নিয়ে এসেছেন? খানিক পরেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। ভিতরের ঘর থেকে দুলাভাই এসে ঢুকলেন। সঙ্গে তাঁর দুই মেয়ে। সেই মেয়েদের দেখে আমি চোখ ফেরাতে পারি না। অপূর্ব সুন্দর মেয়ে। যেন চাঁদের আলো দিয়ে গড়া হয়েছে তাদের। দুলাভাইও খুব সুন্দর মানুষ। দুই মেয়ের সঙ্গে তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর চতুর্থ ও পঞ্চম মেয়ে। চতুর্থজনের নাম নাসিমা হানফি, পরেরজন ফাতেমা হানফি। মণিজা রহমান গার্লস হাইস্কুলে দুজনই ক্লাস নাইনে পড়ে। তাদের আমার পড়াতে হবে। শুনে আমি হতভম্ব। আমি এসএসসি দেব। প্রকৃত অর্থে ক্লাস টেনের শেষদিককার ছাত্র। এ অবস্থায় একজন ছাত্র পড়াবে ক্লাস নাইনের ছাত্রীদের? বাকরুদ্ধ হয়ে আছি। দুলাভাই বললেন, ‘আমি জানি তুমি লেখাপড়ায় ভালো। অবশ্যই পড়াতে পারবে। আজ থেকেই শুরু কর।’ আমি যেন অনেকটা বাধ্য হয়েই শুরু করলাম। পড়াতে গিয়ে দেখি ভালোই পারছি সবকিছু। কারণ ক্লাস নাইন আর টেনের তো একই বই। ওরা দুজনই আর্টসের ছাত্রী। বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, সাধারণ বিজ্ঞান- এগুলো তো আমি পড়েই চলেছি। শুরু হলো আমার নতুন এক টিউশনির জীবন। নাসিমা একটু চুপচাপ, কম কথা বলা মেয়ে। হাসি আনন্দ উচ্ছ্বাসের তেমন প্রকাশ নেই। চাপা স্বভাব। পড়তে গিয়ে কোনোটা না বুঝতে পারলে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। ফাতেমা বেশ চঞ্চল। চটপটে ভঙ্গিতে কথা বলে। কোনো কিছু না বুঝতে পারলে অবিরাম প্রশ্ন করে। দুজনের কেউই আমাকে স্যার বলে না। আসলে কোনো সম্বোধনই করে না। ধীরে ধীরে এ পরিবারের প্রতিটি মানুষ আমাকে বিশেষ নজরে দেখতে শুরু করলেন। নাসিমা ও ফাতেমার দুই ভাই বিজনেস করেন। ওষুধের দোকান আছে তাঁদের। বড় ভাই পরহেজগার ধরনের মানুষ। কথা বলেন কম। তার পরের ভাই খুবই সুপুরুষ। ভাবিটিও সুন্দরী। তখন ভাইদের সংসারে কোনো বাচ্চাকাচ্চা এসেছে কি না, আমার মনে নেই। একে একে বাড়ির প্রত্যেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে। সদ্য পিতৃহারা আমাকে একটু যেন বিশেষ স্নেহের চোখেই দেখতে শুরু করল পরিবারটি। কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা হয়ে গেল নাসিমা ও ফাতেমার মায়ের সঙ্গে। এত স্নিগ্ধ সুন্দর পবিত্রতায় ভরা মুখখানি তাঁর! ও রকম মায়ের সামনে দাঁড়ালে আপনা আপনি মাথা নত হয়ে আসে। আমি তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করেছিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে মৃদুকণ্ঠে যে কথাটি বলেছিলেন তা আজও পরিষ্কার মনে আছে। ‘বড় হও বাবা। মানুষের মতো মানুষ হও।’ কতটা বড় আমি হতে পেরেছি, জানি না। মানুষের মতো মানুষ কতটা হতে পেরেছি, জানি না। তবে সেই মায়ের মায়াবী হাতের স্পর্শখানি আজও আমার মাথায় লেগে আছে।
লেখক : কথাসাহিত্যিক