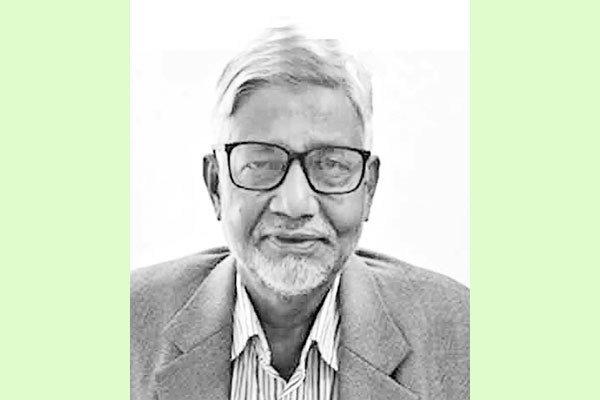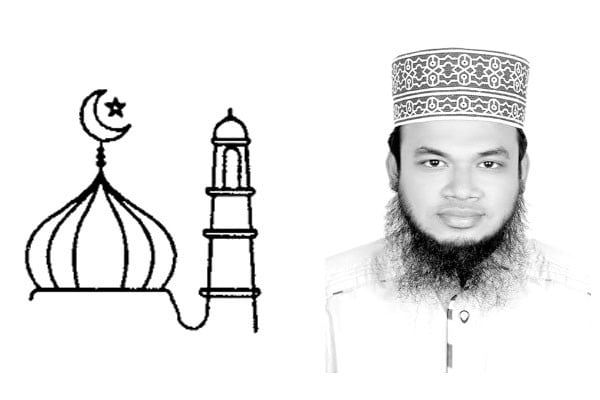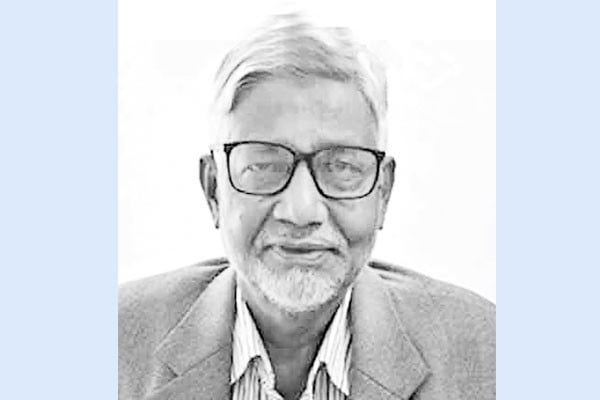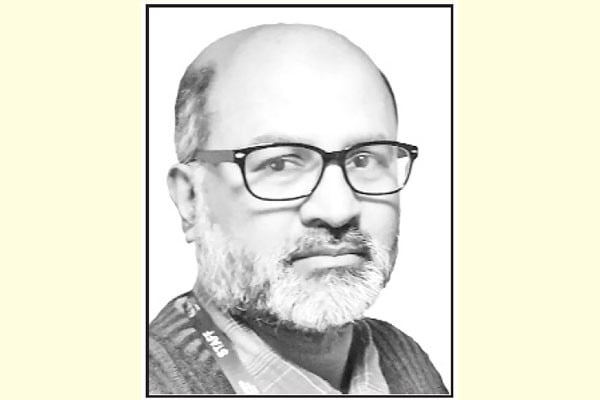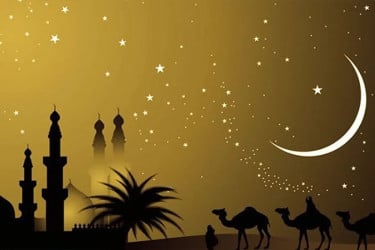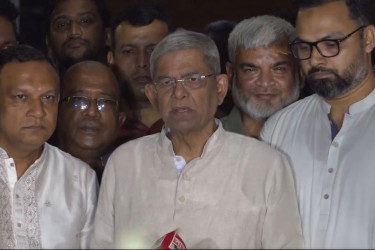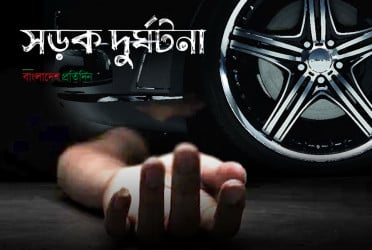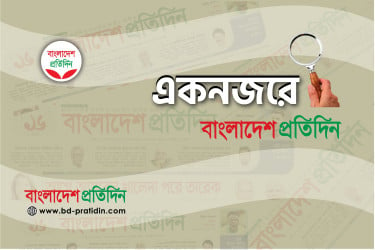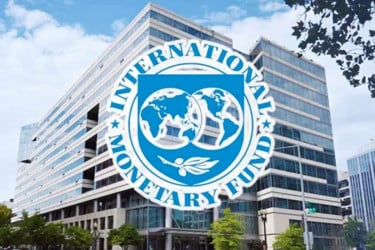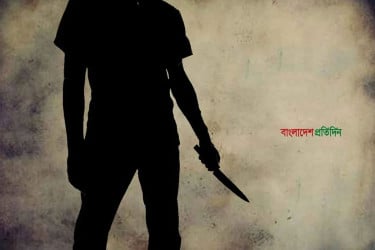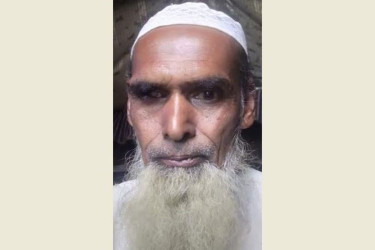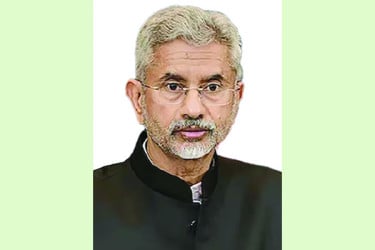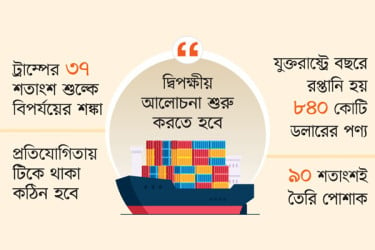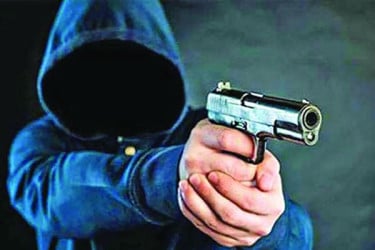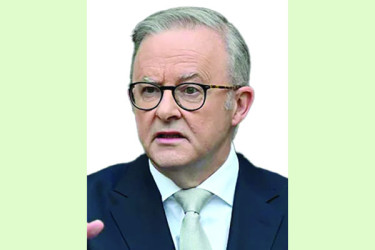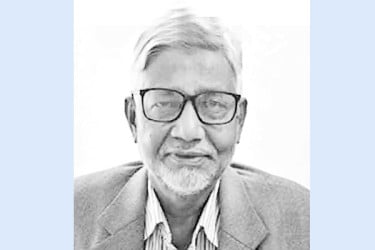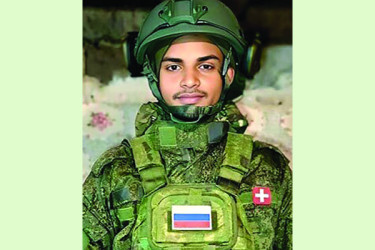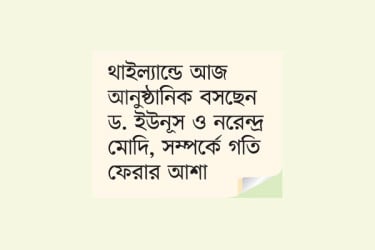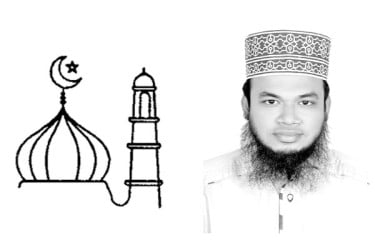কম সংস্কার চাইলে জাতীয় সংসদের নির্বাচন আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে হতে পারে। আর বেশি সংস্কার চাইলে আগামী বছরের মাঝামাঝি। ইলেকশন ঠিক কোন সময়টায় হবে, তা নির্ভর করছে জনগণ কতটা সংস্কার চান, তার ওপর। ব্রিটিশ পার্লামেন্টারিয়ান রূপা হকের সঙ্গে এ রকমটাই বলেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। প্রশ্ন উঠতে পারে, জনগণ আসলে কী চায়, সেটা নির্ধারণ করা হবে কীভাবে? জনমত যাচাইয়ের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য পন্থা হচ্ছে ভোট। ভোটের আগে জনগণ কতটা সংস্কার চায়, তা নির্ণয় করা কঠিন। এই বাস্তবতায় ড. ইউনূসের বক্তব্যকে কেউ কেউ দ্ব্যর্থক মনে করতে পারেন।
ইলেকশনের ডেডলাইন প্রশ্নে রাজনৈতিক দল ও ছাত্রনেতাদের মতের যে মিল নেই, এক্ষণে মোটেও তা অস্পষ্ট নয়। অন্যদিকে ইলেকশনের প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে সামনে আনা হচ্ছে নতুন নতুন ইস্যু এবং সেসব ইস্যুতে মতান্তরও দুর্লক্ষ্য নয়। জুলাই অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, শুধু ভোটের জন্য এত মানুষ রক্ত দেয়নি। তারা বলছেন, সিস্টেম বদলাতে হবে। সবকিছু মেরামত করে, তার পরে নির্বাচন। এই সরকার নিরেট একটা অন্তর্বর্তী সরকার নয়। বিপ্লবী সরকার ঘোষণা করতে হবে। রাষ্ট্রপতিকে সরিয়ে দেওয়া বা পদত্যাগে বাধ্য করা, সংবিধান বাতিল করে শহীদ মিনার থেকে নাগরিক কমিটির ঘোষণাপত্র প্রোক্লেমেশনের আয়োজন, সতেরো বছর বয়সিদের ভোটার বানানোর প্রস্তাব, স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগে না জাতীয় নির্বাচন, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আগে জাতীয় নির্বাচন নয়- এ রকম নানান ইস্যু নিয়ে রাজনীতির মাঠে আলোচনা-সমালোচনা চলছে। স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন জাতীয় নির্বাচনের আগেই স্থানীয় নির্বাচনের পক্ষে। কিন্তু বিএনপি বলছে, না। নতুন নতুন এসব ইস্যু বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি করছে, তা কতখানি গণতন্ত্রের পক্ষে যাচ্ছে, সেটা ভাবনার বিষয়ই বটে।
এদিকে ব্রিটিশ এমপি রূপা হক বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন করে একটা পুরনো ও পরিত্যক্ত স্লোগান থ্রো করেছেন। গত মঙ্গলবার ইউকে-বাংলাদেশ ক্যাটালিস্টস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্টিজের এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বাংলাদেশে রাজনীতি দুই পরিবারের হাতে থাকবে, এটা হতে পারে না। একজন নেতার কন্যা, আরেকজন নেতার বেগম ও তাঁদের ছেলেরা সবকিছুতে আধিপত্য দেখাবে- এ প্রবণতার পরিবর্তন প্রয়োজন। ৫৪ বছরের এই বাস্তবতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একটা পরিচ্ছন্নতা অভিযান দরকার।
 রূপা হক যতই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত হয়ে থাকুন না কেন, তিনি ঢাকায় এসেছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে। বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে এ ধরনের আহ্বান তিনি জানাতে পারেন কি না, সে প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া যায় না। রাজনৈতিক দলীয় নেতৃত্বের পারিবারিক উত্তরাধিকার সঠিক কী বেঠিক, তা নিয়ে যতই তর্ক থাকুক না কেন; বাংলাদেশের মানুষ এটা কিন্তু মেনেই নিয়েছে। আর জনগণের ইচ্ছাই যে গণতন্ত্রের মূল কথা; তা-ও রূপা হকের না জানবার কথা নয়। উপরন্তু এই ইস্যুটি বাংলাদেশে পরিত্যক্ত। ওয়ান-ইলেভেনের সেনা-সমর্থিত মইন ইউ আহমেদ ও ফখরুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তথাকথিত মাইনাস টু ফর্মুলার এটাই ছিল বাহ্যিক কথা। ভিতরে ছিল বিশেষ কোনো একটি দেশের আধিপত্য নিশ্চিত করার কৌশল। পনেরো বছরের কর্তৃত্ববাদী শাসন তারই প্রমাণ বহন করে। প্রতিবেশী ভারতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব নেহরু পরিবারের হাতে ছিল এবং আছে। কিন্তু রাজীব গান্ধীর পরে নেহরু পরিবার আর সরকারে নেই। কারণ জনগণ চায়নি। জনগণ যেটা চাইবে, সেটাই গণতন্ত্র। আর এ-ও মানতে হবে, দল জনগণের ইচ্ছায় পরিচালিত হয় না। দল চলে দলের সদস্যদের ইচ্ছায়। দলের ভিতরে যদি গণতন্ত্র না থাকে, তাহলে প্রতিবাদ হতে হবে দলীয় ফোরামে। সেখানে বাইরের লোকের মতামতের বিশেষ কোনো মূল্য নেই। তবে জনগণ সেই দলকে জাতীয় নির্বাচনে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, আবার সমর্থনও দিতে পারে। এটাই গণতন্ত্রের সাচ্চা কথা। মোট কথা; বাংলাদেশে চলমান পরিস্থিতিতে এ ধরনের উটকো কথা বাঞ্ছনীয় নয়। সব মিলিয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে যে মতানৈক্য দেখা যাচ্ছে, তা প্রীতিকর পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেয় না।
রূপা হক যতই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত হয়ে থাকুন না কেন, তিনি ঢাকায় এসেছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে। বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে এ ধরনের আহ্বান তিনি জানাতে পারেন কি না, সে প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া যায় না। রাজনৈতিক দলীয় নেতৃত্বের পারিবারিক উত্তরাধিকার সঠিক কী বেঠিক, তা নিয়ে যতই তর্ক থাকুক না কেন; বাংলাদেশের মানুষ এটা কিন্তু মেনেই নিয়েছে। আর জনগণের ইচ্ছাই যে গণতন্ত্রের মূল কথা; তা-ও রূপা হকের না জানবার কথা নয়। উপরন্তু এই ইস্যুটি বাংলাদেশে পরিত্যক্ত। ওয়ান-ইলেভেনের সেনা-সমর্থিত মইন ইউ আহমেদ ও ফখরুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তথাকথিত মাইনাস টু ফর্মুলার এটাই ছিল বাহ্যিক কথা। ভিতরে ছিল বিশেষ কোনো একটি দেশের আধিপত্য নিশ্চিত করার কৌশল। পনেরো বছরের কর্তৃত্ববাদী শাসন তারই প্রমাণ বহন করে। প্রতিবেশী ভারতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব নেহরু পরিবারের হাতে ছিল এবং আছে। কিন্তু রাজীব গান্ধীর পরে নেহরু পরিবার আর সরকারে নেই। কারণ জনগণ চায়নি। জনগণ যেটা চাইবে, সেটাই গণতন্ত্র। আর এ-ও মানতে হবে, দল জনগণের ইচ্ছায় পরিচালিত হয় না। দল চলে দলের সদস্যদের ইচ্ছায়। দলের ভিতরে যদি গণতন্ত্র না থাকে, তাহলে প্রতিবাদ হতে হবে দলীয় ফোরামে। সেখানে বাইরের লোকের মতামতের বিশেষ কোনো মূল্য নেই। তবে জনগণ সেই দলকে জাতীয় নির্বাচনে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, আবার সমর্থনও দিতে পারে। এটাই গণতন্ত্রের সাচ্চা কথা। মোট কথা; বাংলাদেশে চলমান পরিস্থিতিতে এ ধরনের উটকো কথা বাঞ্ছনীয় নয়। সব মিলিয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে যে মতানৈক্য দেখা যাচ্ছে, তা প্রীতিকর পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেয় না।
তবে একটা বিষয় স্পষ্ট, জাতীয় নির্বাচনের ডেডলাইন নিয়ে রাজনৈতিক শক্তিসংঘগুলো দুভাগে বিভক্ত। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই বিভক্তি? এর পেছনে কারণ কী আদর্শিক না কৌশলগত? বলা বাহুল্য, রাজনীতিতে আদর্শের চেয়ে কৌশল অনেক বেশি দামি। এই জায়গাটায় দেশ-কাল ও পাত্রের খুব একটা ব্যবধান নেই। মনের কথা মনে থাকে, পাওয়ার পলিটিক্সে কৌশলটাই আসল। জাতীয় নির্বাচন বিলম্বিত হলে কার লাভ, কার ক্ষতি! লাভক্ষতির অঙ্কটা মেলাতে পারলেই বুঝতে পারা যাবে যে কোনো দল, কেন, কী চাইছে! জামায়াতে ইসলামী একটি সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল। এই দলের সমর্থক ও কর্মীদের আদর্শিক কমিটমেন্টের জায়গাটি সবল হলেও জনভিত্তি এখনো ততটা শক্ত হয়ে ওঠেনি। তদুপরি ক্ষমতাচ্যুত সরকারের সাড়ে পনেরো বছরের শাসনামলে দলটি প্রকাশ্যে সাংগঠনিক কোনো কাজ করতে পারেনি। রীতিমতো ঝড় বয়ে গেছে দলটির ওপর দিয়ে। আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা জামায়াত-শিবিরকে খারাপ গালির সমার্থক মনে করত। এখন মুক্ত পরিবেশে জনমত গঠনের জন্য জামায়াতে ইসলামীর যথেষ্ট সময় প্রয়োজন। বিএনপির মিত্রদলগুলোরও কোনো কোনোটি খুব শিগগিরই ইলেকশন চায় না। বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের রাজনৈতিক দল এখনো পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ না করলেও রাজনৈতিক দলের মতোই বলছে ও কাজ করছে। নাগরিক কমিটির মই বেয়ে তারা যে রাজনৈতিক দল করতে যাচ্ছে, সে দল গোছাতেও সময় দরকার। নির্বাচনে ভালো ফলাফল করার জন্য তাদেরও লম্বা সময় নিয়ে অনেক শ্রমঘাম ঝরাতে হবে। দ্রুত নির্বাচন হয়ে গেলে তাদের ট্রেন মিস করার সমূহ আশঙ্কা। কাজেই তারা সংস্কারের আড়ালে কালক্ষেপণের পক্ষপাতী। একে খারাপভাবে দেখার কিছু নেই। এটা তাদের রণকৌশল। এ ক্ষেত্রে তাদের ম্যাচিউরিটির প্রশংসা করা উচিত। পক্ষান্তরে নির্বাচন যত বিলম্বিত হবে, বিএনপির তত ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা। ক্ষতি হতে পারে দুই দিক থেকে। এক. তৃণমূল পর্যায়ের একশ্রেণির নেতা-কর্মীর কার্যকলাপে সাইলেন্ট মেজরিটির মধ্যে অসন্তোষ বাড়বে। তাদের অনেকেই ঝুঁকে পড়বেন জামায়াত বা নতুন রাজনৈতিক সংঘের দিকে। দুই. এই পরিস্থিতির মধ্যে যদি স্থানীয় সরকারের নির্বাচন হয়ে যায়, তাহলেও বিএনপির ক্ষতির আশঙ্কা। স্থানীয় সংস্থাসমূহের নির্বাচিত নির্দলীয় চেয়ারম্যান-মেম্বারদের প্রো-গভর্নমেন্ট একটা প্রবণতা সব সময় দেখতে পাওয়া যায়। তারা সাধারণত ক্ষমতাসীনদের পক্ষে কাজ করে। বিরোধী দলের দিকে ঝুঁকতে চায় না। সরকারি দল সমর্থন করলে স্থানীয় সরকারের বেশি বরাদ্দ পাওয়া যায়। অনিয়মও বেশি করা যায়। দৃশ্যত অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো দল নেই। কিন্তু ছাত্ররা যে দল করতে যাচ্ছে, পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন, সেটি হবে কিংস পার্টি। সোজা কথায় সরকারি দল। মাঠপর্যায়েও এই বার্তাই রয়েছে। এমতাবস্থায় বিএনপি জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকারের ভোট চাইবে না, দলটি বিলম্বিত জেনারেল ইলেকশনের ঝুঁকিও নেবে না, এই স্বাভাবিক।
সাধারণ নির্বাচন বিলম্বিত হলে জাতীয় জীবনেও বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নির্বাচন যত বিলম্বিত হবে রাজনৈতিক মতান্তর ততই বেশি সাংঘর্ষিক রূপ নিতে পারে। এখনই তার কিছু আলামত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। রাজপথে নামার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনে সিদ্ধান্তহীনতার সংকট দেখা দিতে পারে। পুলিশ ও প্রশাসনের লোকদের কর্মক্ষেত্রে কোথাও কোথাও শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থায় পড়তে হতে পারে। কারণ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাদের মধ্যে যাদের সংঘশক্তি রয়েছে, তাদের দাপট অফিসারদের পক্ষে উপেক্ষা করা কঠিন। অন্যদিকে ছাত্রদের রাজনৈতিক দল যদি সত্যি সত্যি কিংস পার্টির মতো আচরণ করতে শুরু করে, তাহলে অন্তর্বর্তী সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে কথা উঠতে পারে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে এ-ও বড় কাঁটা হয়ে দেখা দেবে। কাজেই ঠান্ডামাথায় সবদিক ভেবে অগ্রসর হওয়া উচিত। সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে কীভাবে বাধাহীন নির্বাচনের মাধ্যমে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করা যায়, সেটাই হওয়া উচিত এ সময়ের প্রথম বিবেচনা। সেই বিবেচনা মাথায় রেখে জরুরি সংস্কারগুলো করা দরকার যত দূর সম্ভব কম সময়ের মধ্যে। যে এগারোটি সংস্কার কমিশন হয়েছে, তাদের সুপারিশ এবং রাজনৈতিক দলসমূহের প্রস্তাবের আলোকে অন্তর্বর্তী সরকার একটি সর্বসম্মত ঘোষণাপত্র প্রোক্লেইম করতে পারে। নির্বাচিত সরকার সেই প্রোক্লেমেশনকে মান্যতা দিতে বাধ্য থাকবে মর্মে সামাজিক চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে। সেটা যদি হয়, তাহলে প্রত্যাশিত সংস্কার প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার কোনো কারণ নেই।
লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক