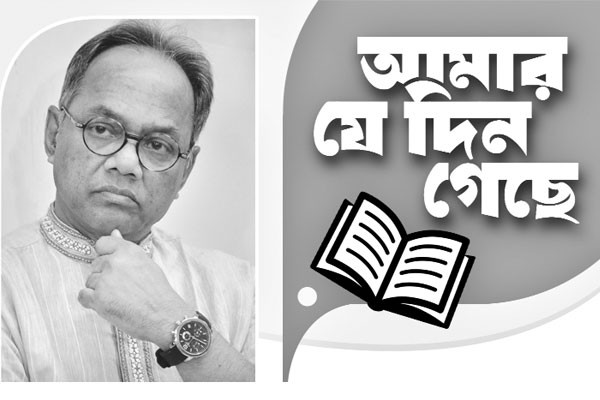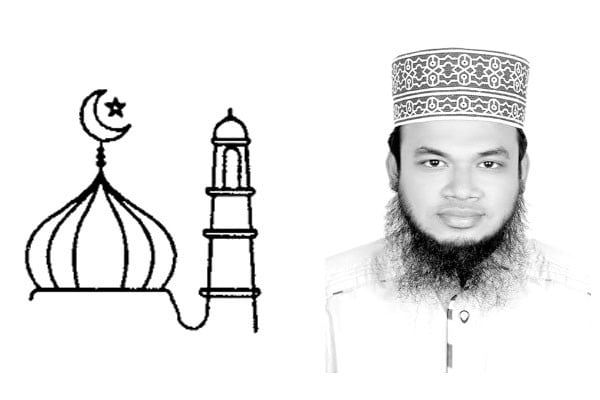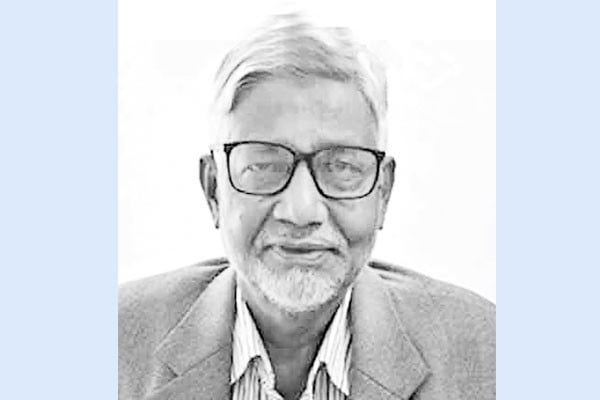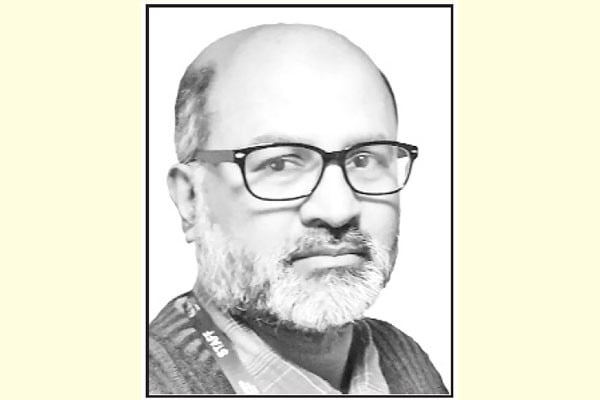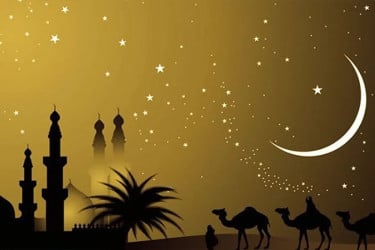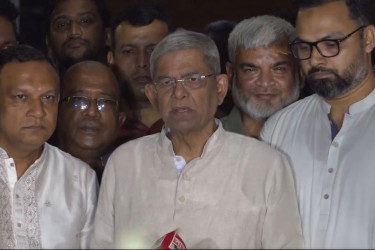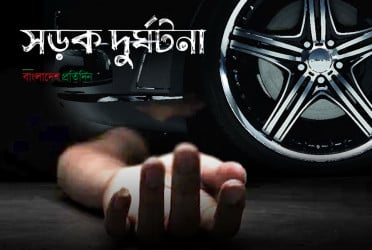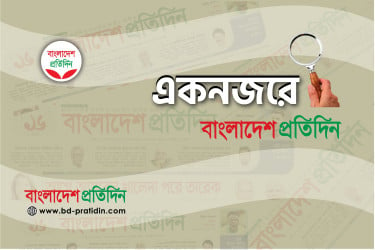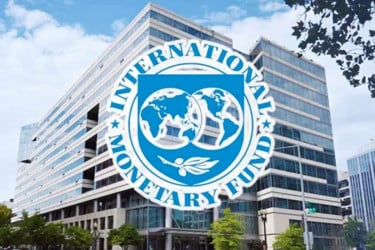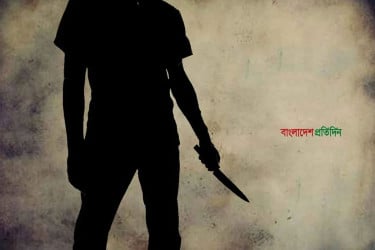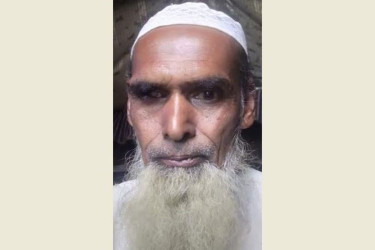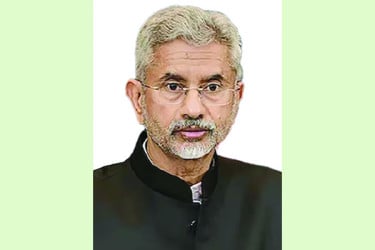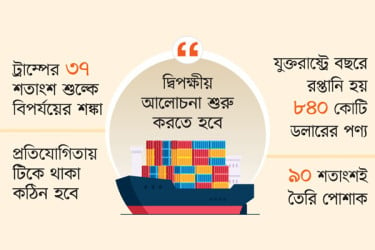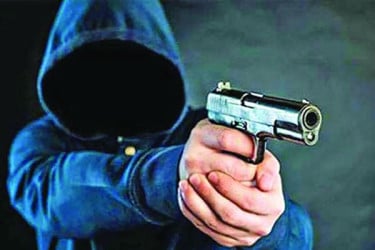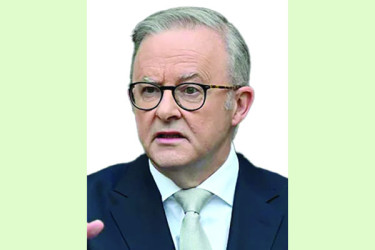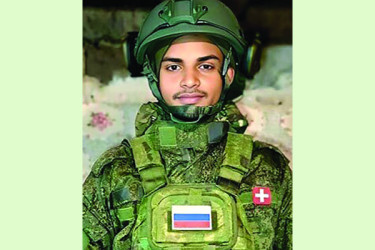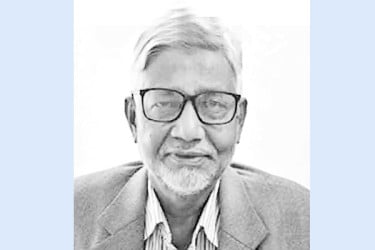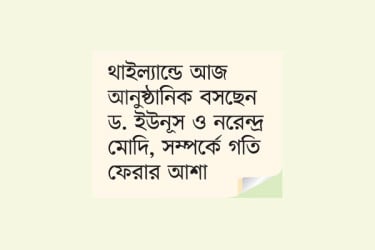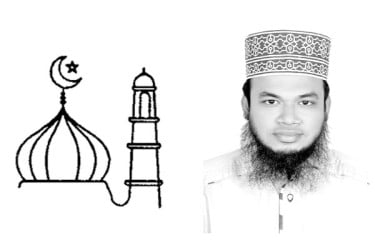তখন নাসিমা ও ফাতেমাকে পড়াতে যাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। অনেক সময় সকাল ৯টা-১০টার দিকে যেতাম। অনেক সময় দুপুরের পর যেতাম। বিকাল-সন্ধ্যায়ও গিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধ শেষ পর্যায়ে। ঢাকা প্রায় অবরুদ্ধ। সারা রাতই ঢাকার আশপাশে বা ঢাকা শহরের ভিতরেই গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যায়। আমার টুনুমামাদের পুরো পরিবার বিক্রমপুরে। টুনুমামাও চলে গিয়েছিলেন। একা একা ফিরে এসেছেন। দীননাথ সেন রোডের বাড়িটা শূন্য পড়ে আছে। ভাড়াটিয়ারাও চলে গেছে। টুনুমামা একা দোতলার একটা রুমে থাকেন। আমি গিয়ে রাতে তাঁর সঙ্গে থাকি। এক রাতে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে টুনুমামা আমাকে ডেকে তুললেন। বাড়ির পুবদিককার পুকুরের ওপারেই রেললাইন। দক্ষিণে কিছুদূর এগোলেই গেন্ডারিয়া স্টেশন। সেদিকটায় তুমুল গোলাগুলির শব্দ। ঘুম ভাঙার পর আমিও আতঙ্কিত। মামা-ভাগ্নে ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে রইলাম। নিশ্চয় পাকিস্তানিদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের মুখোমুখি যুদ্ধ হচ্ছে। পরদিনই বাড়ি ফেলে টুনুমামা আবার বিক্রমপুরে চলে গেলেন। আমাদের পরিবারটি যাওয়ার উপায় নেই। বাড়িঘর সবই আছে বিক্রমপুরে। কিন্তু টাকাপয়সা তো নেই। খাব কী? ওই অবস্থাতেই বড় ভাই একটা চাকরি করে টঙ্গীতে। গেন্ডারিয়া থেকে সাইকেল চালিয়ে টঙ্গী যায়। অফিসে থাকার ব্যবস্থা আছে। একদিন দুদিন পরপর ফিরে আসে। মা আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে থাকেন ছেলের জন্য। ছেলে ফিরে আসতে পারবে কি পারবে না। পাকিস্তানিরা তাকে ধরে নিয়ে যায় কি না! মেরে ফেলে কি না! ওই অফিসের চাকরির ফাঁকে ফাঁকে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে ভাইয়ের। সে তাদের হয়ে ইনফরমারের কাজ করে। এসব কথা বিস্তারিত লিখেছি আমার ‘একাত্তর ও একজন মা’ উপন্যাসে।
এ রকম পরিস্থিতিতেই পরিচয় হয়েছিল কামালদের পরিবারের সঙ্গে। আমার ছাত্রীরা থাকে বাড়িটির তিনতলায়। কামালদের পরিবারটি থাকে দোতলায়। ছাত্রী পড়াতে যাওয়ার সময় ওদের ফ্ল্যাটের পাশ দিয়েই সিঁড়ি ভাঙতে হয়। ফুটফুটে সুন্দর একটি ছেলেকে দেখি সারাক্ষণই অতি চঞ্চল ভঙ্গিতে ছোটাছুটি করছে। খেলাধুলা দুষ্টুমি করছে। সঙ্গে ছোট একটি ভাই আর পুতুলের মতো দেখতে একটি বোন। মাকে ‘আম্মা’ ডাকে কামাল। আম্মাকে দেখি মাস ছয়েকের বাচ্চা ছেলে কোলে নিয়ে ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন। অতি চঞ্চল তিন ছেলেমেয়েকে স্নেহের গলায় শাসন করছেন। তিনি বেশ লম্বা। টকটকে সুন্দর গায়ের রং। মাথাভর্তি চুল। ব্যক্তিত্বময়ী চেহারা। কণ্ঠে সব সময় প্রায় আদেশ-নির্দেশের স্বর। পরে দেখেছিলাম কী অসামান্য মায়াবতী মানুষ তিনি। স্নেহ-মমতা আর ভালোবাসায় তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ।
তখন নভেম্বর মাসের শুরু। এক সকালে গিয়েছি নাসিমা-ফাতেমাকে পড়াতে। নেমে আসার সময় দেখি কামালের আম্মা দাঁড়িয়ে আছেন দরজার সামনে। আমাকে ডাকলেন। সরাসরি বললেন, ‘তোমার সম্পর্কে আমি সবই জানি। কাল থেকে আমার তিন ছেলেমেয়েকেও পড়াও।’ নাসিমা-ফাতেমাকে পড়িয়ে ২৫ টাকা পেতাম। আম্মাও সেই টাকাটা দেবেন। ওই অবস্থায় মাসে ৫০ টাকা রোজগার খুবই বড় ব্যাপার। একই বাড়িতে দুটো টিউশনি। সুবিধাও অনেক। একই সময়ে পড়াতে গেলেই হবে। একটি শেষ করে আরেকটি টিউশনি। এ দুই পরিবারের মধ্যে আরেকটা মিলও আছে। তারা মানিকগঞ্জের লোক। পরদিন থেকে দ্বিতীয় টিউশনি শুরু হলো আমার। কামালদের পরিবারটি অত্যন্ত ছিমছাম। গোছানো। স্নিগ্ধ সুন্দর পরিবেশ ফ্ল্যাটের ভিতর। কামাল ক্লাস সিক্সে পড়ে বাংলাবাজারের জুবিলী হাইস্কুলে। মেজো ছেলেটির নাম শোয়েব। মেয়েটির নাম বামনি। ওরা পড়ে ক্লাস টুতে। আমরা পড়তাম গেন্ডারিয়া হাইস্কুলে। গেন্ডারিয়া হাইস্কুলে একটা মর্নিং শিফট চালু করা হয়েছে। শোয়েব আর বামনি সেখানে পড়ে। বাড়ির কর্তা আজিজুল হক সাহেব ফুড ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন। ফুড ইন্সপেক্টর। অত্যন্ত নম্র বিনয়ী সজ্জন মানুষ। ব্যক্তিত্ববান। কথা বলেন কম। ধীরে ধীরে জানলাম আম্মার ডাকনাম ‘ননী’। ভালোনাম ‘মাকসুদা হক’। কামালদের মতো আমিও তাঁকে ‘আম্মা’ ডাকতে শুরু করেছি। কিন্তু আব্বাকে ডাকি ‘খালুজান’। কামাল অতি চঞ্চল স্বভাবের। ছটফটে। শোয়েব একটু ধীর। বামনি বেশ চুপচাপ শিশু। পড়াতে গিয়ে দেখি ওরা তিন ভাইবোনই আমাকে বেশ মান্য করছে। বয়সে কামালের চেয়ে আমি বছর পাঁচেকের বড়। আমার শরীর স্বাস্থ্যও তেমন ভালো নয়। এ রকম একটা ছেলেকে শিক্ষক হিসেবে মেনে নেওয়া কঠিন। কিন্তু কামালরা মেনে নিয়েছে। পড়াতে গেলে আম্মা যত্ন করে চা-বিস্কুট খাওয়ান। দুপুর হয়ে গেলে ভাত না খেয়ে বেরোতে দেন না। নাসিমা-ফাতেমাদের বাসায়ও একই অবস্থা। ওরাও খাওয়ায়। অর্থাৎ দুটো পরিবারের কাছেই অনেক বাড়তি স্নেহ-মমতা আমি পেতে শুরু করেছি। এ বয়সে এসে যখন সেই জীবনটার দিকে ফিরে তাকাই, তখন অনেক ছোট ছোট ঘটনা মনে পড়ে। গেন্ডারিয়ার অনেক বাড়িতে পালাক্রমে ভাড়া থেকেছি আমরা। মুরগিটোলা থেকে গিয়েছিলাম রজনী চৌধুরী রোডের বাড়িটায়। সেই বাড়ির কর্ত্রী একটু রাগী ধরনের। সামান্য কিছু এদিক-ওদিক হলে খুব ধমকাধমকি করতেন। আমরা তাঁকে খুব ভয় পেতাম। পরবর্তীকালে তিনি আমার বড় বোনের শাশুড়ি। তার ছোট ছেলের সঙ্গে আমার বড় বোনের বিয়ে হয়। আমার দুলাভাইয়ের ডাকনাম ‘নবনূর’। ভদ্রমহিলাকে সবাই বলতেন ‘নবনূরের মা’। আমরা ডাকতাম খালাম্মা। ’৬৯ সালে সেই বাড়িতে প্রথমবার কয়েক মাস থেকেছি। ’৭০ সালের শেষ কিংবা ’৭১-এর শুরুর দিকে অনেক বাড়ি ঘুরে চলে এসেছিলাম সাবেক শরাফতগঞ্জ লেনের বাড়িতে। আব্বা মারা গেলেন সেই বাড়িতে। যে খালাম্মাকে আমরা এত ভয় পেতাম, সেই রাগী খেপাটে মানুষটির তখন অদ্ভুত এক চেহারা দেখলাম আমরা। আমাদের কথা তাঁর মনে রাখারই কথা নয়। কিছুদিন তাঁর ভাড়াটে ছিলাম। শরাফতগঞ্জ লেনের ওই বাড়ি থেকে চার-পাঁচটা বাড়ির দক্ষিণে তাঁদের বাড়ি। আব্বার মৃত্যুশোকে ধসে পড়া পরিবার আমাদের। মাকে ঘিরে সব ভাইবোন সকালবেলায় বসে আছি বড় রুমটায়। এ সময় সেই খালাম্মা এসে হাজির। সঙ্গে সবচেয়ে বড় সাইজের তিনটা পাউরুটি আর বড় কেটলি ভরা চা। নিজেই আমাদের রুম থেকে চায়ের কাপ বের করলেন। পাউরুটি ভাগ করে দিলেন আমাদের। সামনে বসিয়ে জোর করে অনাথ ছেলেমেয়েগুলোকে খাওয়ালেন। প্রায় দিন দশেক, প্রতিদিন এ কাজটা তিনি করেছেন। গেন্ডারিয়ার মানুষ আমাদের খুব ভালোবেসেছে। যে বাড়িতে ভাড়া থেকেছি, তাঁদের সঙ্গেই এক ধরনের ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে গেছি। ফেরদৌস ওয়াহিদদের বাড়ি কিনেছিলেন পরে বড় ব্যবসায়ী শাজাহান সাহেব। সেই পরিবারের মানুষ আজও আমাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁরা আসেন। ধারাভাষ্যকার হামিদ ভাইদের পরিবারটিও স্নেহ-মমতায় ভরিয়ে রেখেছিলেন আমাদের। যদিও তাঁদের বাড়িতে আমরা কোনো দিন ভাড়া থাকিনি। যে বাড়িতে থাকতাম সেই বাড়ির উল্টো দিকে ছিল তাঁদের বাড়ি। রজনী চৌধুরী রোডে। এখন সেসব দিনের কথা ভাবলে মনে হয় তখনকার মানুষ খুবই মানবিক ছিল। যত দিন গেছে, ধীরে ধীরে আমরা অমানবিক হয়ে গেছি। আমাদের ভালোবাসা কমে গেছে, স্নেহ-মমতা কমে গেছে। আমরা নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর হয়ে গেছি।
নাসিমা-ফাতেমাদের পড়াতে পেরেছিলাম মাস দুয়েকের কম সময়। কামালদের বোধ হয় এক মাস কয়েক দিন হবে। ডিসেম্বর মাস এলো। আমাদের মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনী যুক্ত হয়ে যৌথ বাহিনী তৈরি হয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল পাকিস্তান। ঢাকায় বিমান হামলা শুরু হলো। ওই বাড়ির ছাদে দুপুরের দিকে নাসিমা-ফাতেমাদের পরিবার আর কামালদের পরিবারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দুদেশের ফাইটার বিমানের ককফাইট দেখলাম একদিন। তারপরই ঢাকা ছেড়ে মানিকগঞ্জে চলে গেল ওই দুটো পরিবার। কয়েক দিন পর আমিও চলে গেলাম বিক্রমপুরে। সেই যাত্রা ও ফিরে আসার বর্ণনা বিস্তারিত লিখেছিলাম ‘একাত্তর ও একজন মা’ উপন্যাসে। স্বাধীন বাংলাদেশ। চারদিকে উৎসব আনন্দ। কিন্তু আমাদের পরিবারে কোনো আনন্দ উৎসব নেই। মায়ের চোখে হতাশা। দশ ছেলেমেয়ে নিয়ে কেমন করে বেঁচে থাকবেন সেই দুশ্চিন্তা। বড় ভাইয়ের টঙ্গীর চাকরিটা আছে। কিন্তু অফিস বন্ধ। বেতন অনিশ্চিত। যে বাড়িতে টিউশনি করি সেই দুই বাড়ির কেউ তখনো ঢাকায় ফেরেননি। আমি এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াই। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিই। হিন্দু বন্ধুদের পরিবারগুলো ধীরে ধীরে ঢাকায় ফিরছে। তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আড্ডা হয়। হামিদুল নিয়মিত আছে আমার সঙ্গে। বেলালের বড় ভাই মহিউদ্দিন ভাই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। স্বাধীনতার আনন্দে বেলালদের বাড়িতে সারাক্ষণই উৎসব। মাঝেমাঝে বেলালদের বাড়িতেও যাই। কলুটোলায় মিনুখালার বাড়ি। তাঁরাও বিক্রমপুর থেকে ফিরেছেন। টুনুমামাদের বাড়ির সবাই ফিরে এসেছেন। ঘুরে ঘুরে সবার খবর নিই। অনুমামা পাকিস্তান এয়ারফোর্সে চাকরি করতেন। থাকতেন করাচিতে। তিনি সেখানে আটকা পড়েছেন। এজন্য টুনুমামাদের বাড়িতে কোনো আনন্দ নেই। নানা-নানি, মামা-খালারা উদ্বিগ্ন। অনুমামার বড় বোন মিনুখালা। ভাইয়ের জন্য তিনি প্রতিদিন রোজা রাখছেন। খালু অবস্থাপন্ন। বড় ছেলেটির নাম দিপু। ছয়-সাত বছর বয়স। তাকে পড়ানোর দায়িত্ব পড়ল। দিপু অসম্ভব দুষ্টু। একটা মিনিট স্থির হয়ে বসে না। কারও কথা শোনে না। আমার খালু গমগমে গলার প্রচণ্ড রাগী মানুষ। যৌথ পরিবার। এক সন্ধ্যায় দিপুকে পড়াতে গেছি। দিপু কিছুতেই পড়তে বসবে না। আমার কথা শুনছেই না। খালা এসে দুয়েকবার চেষ্টা করে গেলেন। কাজ হলো না। শেষ পর্যন্ত খালু এসে ওই অতটুক ছেলেটাকে নির্দয়ভাবে পেটাতে শুরু করলেন। তাঁর তখন এমন ভয়ংকর এবং মারমুখো চেহারা, যে তাঁকে আটকাতে যাবে তার ওপরই চড়াও হবেন। আমি ভয়ে পালিয়ে এলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় শুনি বাপের হাতে বেধড়ক মার খাচ্ছে আর ত্রাহিস্বরে ‘বাবাগো মাগো’ বলে ডাক ছাড়ছে দিপু। সেদিনই ওই টিউশনি আমার শেষ। আমি আর কখনো দিপুকে পড়াতে যাইনি।
কামালরা ফিরে এলো কয়েক দিনের মধ্যেই। খবর পেয়ে গেছি দেখা করতে। আম্মা বললেন, ‘কাল থেকেই পড়াও।’ পরদিন থেকে শুরু করলাম। ওপরতলার ছাত্রী দুজন ফিরল আরও দিন দশেক পর। তাদেরও পড়াতে যাই। শোনা যাচ্ছে এপ্রিলের দিকে আমাদের এসএসসি পরীক্ষা হবে। তার প্রিপারেশনও শুরু করেছি। অন্যদিকে প্রায় প্রতিদিনই যাচ্ছি লক্ষ্মীবাজারের মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে। আব্বার প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়েটি ইত্যাদির টাকা কীভাবে তোলা যায় সেসব জানা-বোঝার চেষ্টা করছি। বড় ভাই টঙ্গীর চাকরিটা চালিয়ে যাচ্ছে। মিউনিসিপ্যালিটিতে আব্বার যাঁরা কলিগ তাঁরা নানা রকমভাবে আমাদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করছেন। তবে কোর্ট থেকে সাকসেশন সার্টিফিকেট বের করতে হবে। ওই সার্টিফিকেট হাতে না এলে আব্বার প্রাপ্য টাকাটা তোলা যাবে না। আমার সেই খালু একজন উকিল নিয়োগ করে দিলেন। তখনো জানি না যে সাকসেশন সার্টিফিকেট জিনিসটা এত জটিল। এবং সেটা পেতে এক দেড় বছর লেগে যাবে। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশ। সবকিছু এলোমেলো। মাকে নিয়ে প্রায়ই কোর্টে গিয়ে বসে থাকি। কখনো কখনো আমি যেতে পারি না। আমার ছোট ভাই খোকনকে নিয়ে মা যান। খোকনের তখন সাত বছর বয়স। কোর্ট থেকে একদিন সে হারিয়ে গেল। আহা রে আমার মায়ের যে তখন কী দিশাহারা ভাব! কী উদ্বিগ্নতা আর কান্না! মিনিট পনেরো-কুড়ি পর খোকনকে পাওয়া গেল। জজ কোর্টের আঙিনায় নিজেকে হারিয়ে আমার সেই শিশু ভাইটিও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। চারপাশে ভিড় করেছিল মানুষ। মিউনিসিপ্যালিটিতে আব্বার প্রাপ্য ছয় হাজার টাকা আমরা পেয়েছিলাম। সেই পুরো টাকাটাই খেয়ে ফেলল মায়ের এক টাউট চাচাতো ভাই। আমার সেই মামাটি ব্যবসার নাম করে টাকাটা নিল। প্রতি মাসে লভ্যাংশের অর্ধেক দেবে আমাদের। দেড়-দুই শ টাকা যা-ই পাওয়া যাবে মাসে তাতে আমাদের সংসারের অনেকটা সাশ্রয় হবে। মাস তিনেক বোধ হয় টাকাটা সে দিয়েছিল। তারপর উধাও হয়ে গেল। না ঢাকায় তাকে খুঁজে পাওয়া যায়, না গ্রামের বাড়িতে। এ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি উপলব্ধি করেছি, বিপদের দিনে এমন একেকটা সময় আসে, খড়কুটো আঁকড়ে ধরলেও সেটা হাতের ফাঁক দিয়ে গলে যায়। আবার সুসময়ে খড়কুটো হাত দিয়ে ছুঁলেও তা সোনা হয়ে যায়।
এসএসসি পরীক্ষা এসে গেল। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম এসএসসি পরীক্ষা। সব সাবজেক্টে পরীক্ষা হবে না। হবে পাঁচ সাবজেক্টে। আমি সায়েন্সের ছাত্র। বাংলা ইংরেজি অঙ্ক ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি পরীক্ষা হবে। তা-ও একশ নম্বরে নয়, পঞ্চাশ নম্বরে। ‘পগোজ স্কুল’-এ সিট পড়ল। রেজাল্ট বেরোবার পর দেখা গেল অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এই তিনটাতে লেটার মার্কস পেয়েছি। অঙ্কে পঞ্চাশে পঞ্চাশ। কেমিস্ট্রিতে উনপঞ্চাশ। ফিজিক্সে আটচল্লিশ। বাংলা-ইংরেজিতেও ও রকমই নাম্বার। অর্থাৎ স্টার মার্কস পেয়েছি। আমার বড় বোন মণিও পরীক্ষা দিয়েছিল। সে-ও ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে। তারপরও আমাদের পরিবারে আনন্দ নেই। মা চিন্তা করছেন ছেলেমেয়ে দুটিকে কলেজে ভর্তি করাবেন কেমন করে? টাকা পাবেন কোথায়? অন্যদিকে আমার দুই ছাত্রী নাসিমা ও ফাতেমা খুব খুশি। তাদের টিচার ভালো রেজাল্ট করেছে। কামালদের পরিবারেরও একই অবস্থা। আম্মা খুবই খুশি। তত দিনে আমি লক্ষ করেছি, কামালের বেশ গানবাজনার দিকে ঝোঁক। যে ঝোঁক আমারও ছেলেবেলা থেকে। আমার মায়ের হারমোনিয়াম, কলের গানটা টুনুমামাদের বাসায় রয়ে গিয়েছিল। মা আর কোনো দিন তা ফিরিয়ে আনেননি। সেই বাড়িতে গেলেই দেখতাম, আমার খালারা কেউ কেউ সেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করে। মামারা কলের গানের রেকর্ড চাপিয়ে দুপুরের পর গান শোনে। সেই অতীতকাল থেকে কলের গানে শোনা কোনো কোনো গানের লাইন এখনো উদাস নির্জন কোনো দুপুরে আমাকে বিষন্ন করে তোলে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের একটা গানের রেকর্ড বাজাতেন টুনুমামা। সেই গানের দুটো লাইন মনে পড়ে। ‘আমিও পথের মতো হারিয়ে যাব, আমিও নদীর মতো আসব না ফিরে আর, আসব না ফিরে কোনো দিন।’
♦ লেখক : কথাসাহিত্যিক