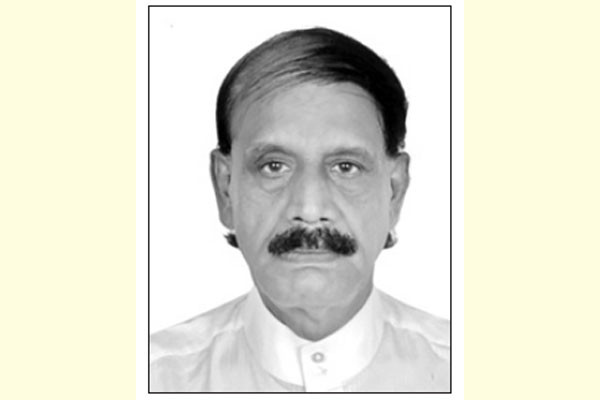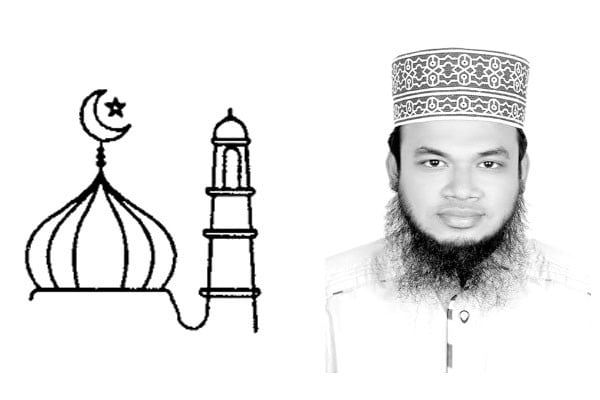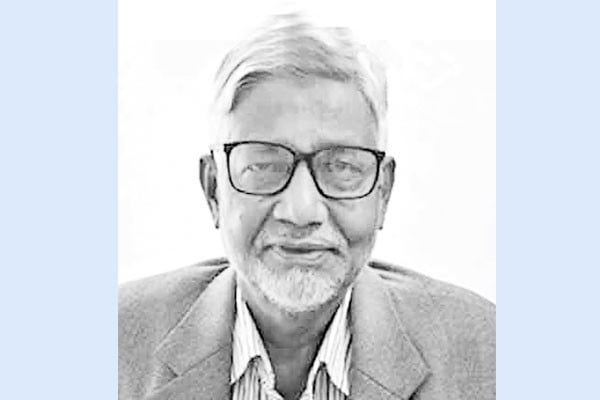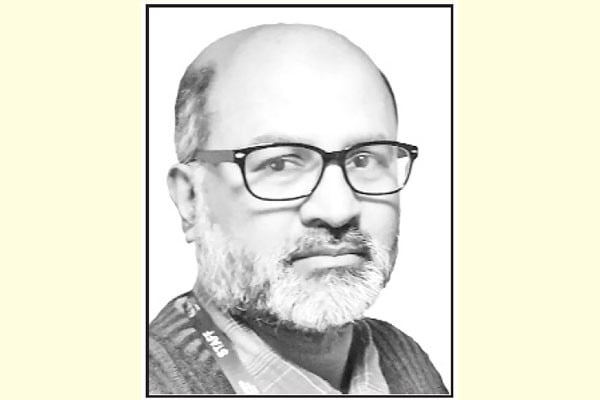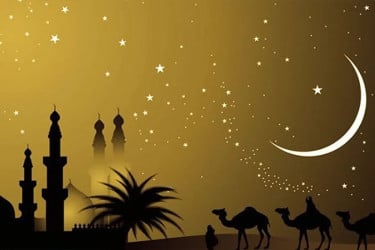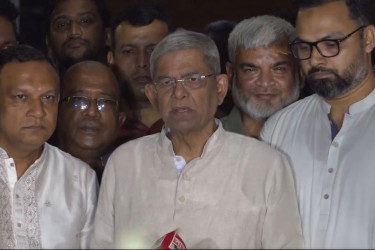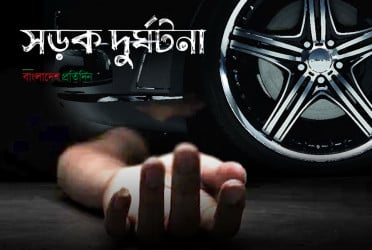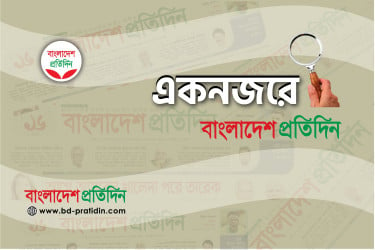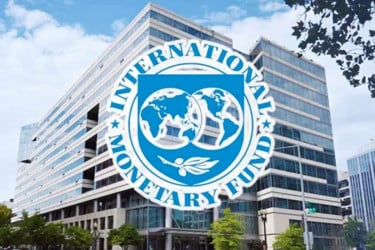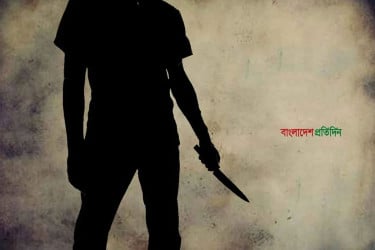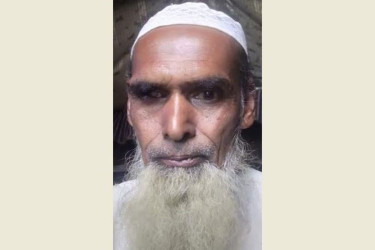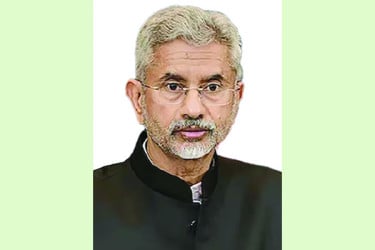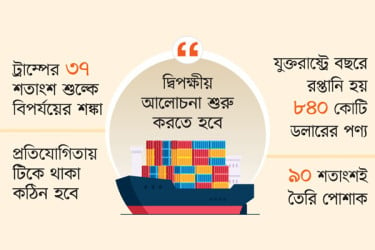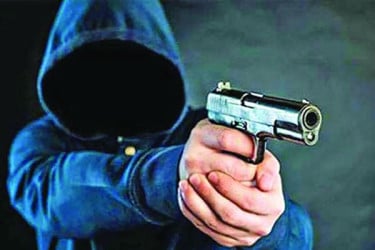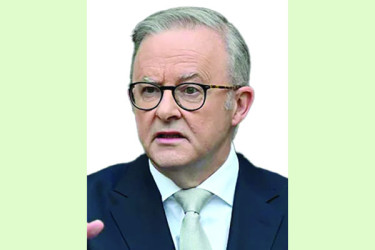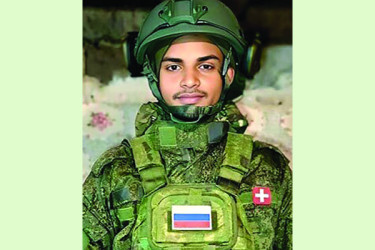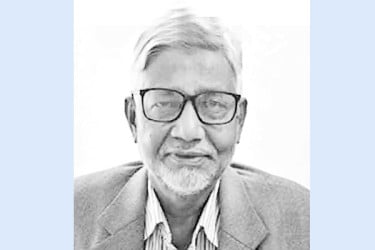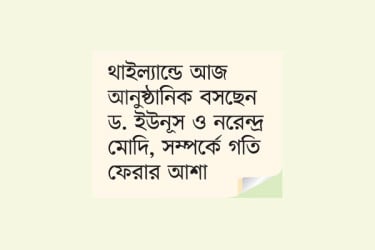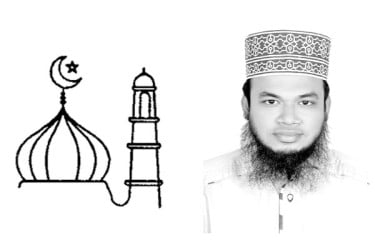প্রবাদ-প্রবচন ভাষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত। এটি ভাষার অমূল্য সম্পদ। বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতি তথা সামগ্রিক জীবনাচরণে প্রবাদ-প্রবচন একটি সমৃদ্ধ বিশেষ ধারা হিসেবে বিবেচিত। প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে বাঙালির জীবন, ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার, বিশ্বাস ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাদ ও প্রবচন প্রায় একই অর্থে এবং পাশাপাশি ব্যবহৃত হলেও এর মধ্যে পার্থক্য আছে। উল্লেখ্য মানবসমাজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ জীবন সত্যের স্মারক কোনো জনপ্রিয় বিদ্রƒপাত্মক সংক্ষিপ্ত উক্তিকে প্রবাদ বলে। কিন্তু প্রবচন হলো প্রজ্ঞাবান, মননশীল বা সৃজনশীল ব্যক্তির অভিজ্ঞতাপ্রসূত ব্যক্তিগত সৃষ্টি। এগুলো সাধারণত প্রণেতার নামেই প্রচলিত হয়। যেমন খনার বচন। তা ছাড়া কবি, সাহিত্যিক বা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা এর উদ্ভাবক বা রচয়িতা। প্রবাদ ও প্রবচনের সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য হলো প্রবাদ লোকসমাজ বা কালের সৃজন। কিন্তু প্রবচন কবি, সাহিত্যিক বা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সৃষ্টি। প্রবাদের কোনো লিখিত ভিত্তি নেই। কিন্তু প্রবচনের আছে। প্রবাদকে বলা যায়, লোকসমাজের অভিজ্ঞতার নির্যাস, একক কোনো ব্যক্তি এর রচয়িতা হিসেবে দাবি করতে পারে না। অন্যদিকে প্রবচন ব্যক্তিগত প্রতিভার দ্বারা সৃষ্ট বাক্য বা বাক্যাংশ। তবে প্রবচন একসঙ্গে লোকসমাজের অধিকারে চলে আসে। আবার প্রবাদ রূপক ও ব্যঞ্জনার্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে প্রবচনের রূপক ধর্ম থাকে না, সরাসরি প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সাধারণত প্রবাদের চেয়ে প্রবচন আকারে বড় হয়। যেভাবেই বলি না কেন, প্রবাদ-প্রবচন মানবজীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল এবং বিস্তৃততম জীবন অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সাহিত্যিক প্রয়াস। এর মূলে থাকে কোনো ঘটনা বা কাহিনি। মজার ব্যাপার হলো, এতে নিহিত থাকে মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় উপদেশ, যা জীবন চলার পথে অনেকাংশে সারথী হিসেবে পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখে।
প্রবাদ-প্রবচনের সংক্ষিপ্ত বাক্যে একটি জাতির নানা বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে থাকে। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অর্থব্যঞ্জনা, অভিজ্ঞতার নির্যাস এবং সরল প্রকাশভঙ্গি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থব্যঞ্জনার ব্যাপারে উল্লেখ্য যে প্রবাদের অর্থ গভীর ও তাৎপর্যময়। এর তীক্ষ্ণ অর্থভেদী মন্তব্য শ্রোতা ও পাঠককে সহজে সচকিত করে। এর শব্দার্থ নয়, রূপক অর্থই গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে অভিজ্ঞতার নির্যাসের ক্ষেত্রে যে কথা উঠে আসে তা হলো, প্রবাদের শক্তিই হলো অভিজ্ঞতা। লোকসমাজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার মূল সার থাকে প্রবাদে। আসলে যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যোগ হয়। আর সরল প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে প্রবাদ সহজসরল হওয়ার কারণে তা সহজেই শ্রোতার মনে সাড়া জাগায়। তা ছাড়া প্রবাদের আলংকারিক গুণ রয়েছে বলে মানুষ তা সহজে ভুলে যায় না। সাধারণত ছন্দ ও অন্ত্যমিলের জন্য এবং একই সঙ্গে উপযুক্ত অনুষঙ্গের জন্য প্রবাদ দীর্ঘদিন মানুষের মনে থাকে। যেমন : অর্থ অনর্থের মূল। কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালে পাজি; ইত্যাদি। এদিকে বিচিত্র অর্থের দিক বিবেচনা করে প্রবাদকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন : সাধারণ অভিজ্ঞতামূলক : কান টানলে মাথা আসে, অল্পবিদ্যা ভয়ংকরি। নীতিমূলক : চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনি, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। সমালোচনামূলক : উচিত কথায় মামা বেজার। সামাজিক রীতিবিষয়ক : মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট ইত্যাদি। ব্যঙ্গাত্মক : চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, ঠেলার নাম বাবাজি ইত্যাদি। এ ছাড়া প্রবাদ-প্রবচনের বাক্য গঠনের দিক দিয়ে তিন ধরনের হয়ে থাকে; যেমন পূর্ণবাক্য অপূর্ণ বা খণ্ডবাক্য এবং একাধিক বাক্য। প্রবাদের সঙ্গে বাগধারার মিল আছে বটে।
তবে চরিত্রগত ও গঠনগত পার্থক্যে উপক্ষণীয় নয়। প্রবাদ ও বাগধারা উভয়ই লোকসমাজের অভিজ্ঞতার প্রকাশ। প্রবাদে উপদেশ বিধৃত। কিন্তু বাগধারায় সে রকম প্রবণতা দেখা যায় না। প্রবাদ প্রায়ই সম্পূর্ণ বাক্যে প্রকাশিত; অন্যদিকে বাগধারা সম্পূর্ণ বাক্য নয়, বাক্যাংশ। আশ্চর্যের বিষয় হলো, একটি ভাষার প্রবাদ-প্রবচন সে ভাষার একান্ত নিজস্ব সম্পদ। এই সম্পদ হস্তান্তর করা যায় না। অর্থাৎ এগুলোকে অনুবাদ করে অন্য ভাষায় নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তবু কিছু কিছু অনুবাদ হয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য যে কোনো বাঙালি যখন বলে ‘আদার ব্যাপারি হয়ে জাহাজের খবরে কাজ কী?’ তখন তার অন্তর্নিহিত অর্থ কেবল বাঙালির পক্ষেই বুঝে ওঠা সম্ভব। ভিন্ন ভাষাভাষীর নয়।
লেখক : প্রাবন্ধিক