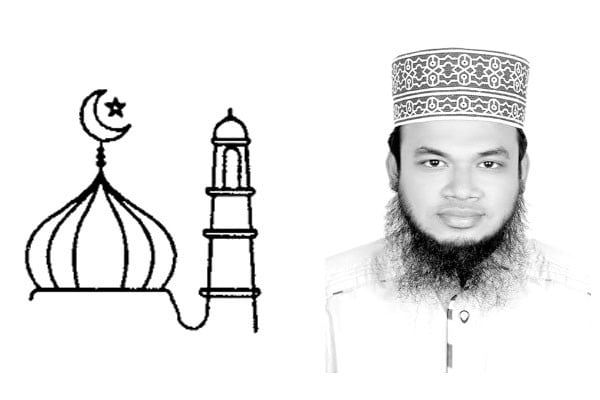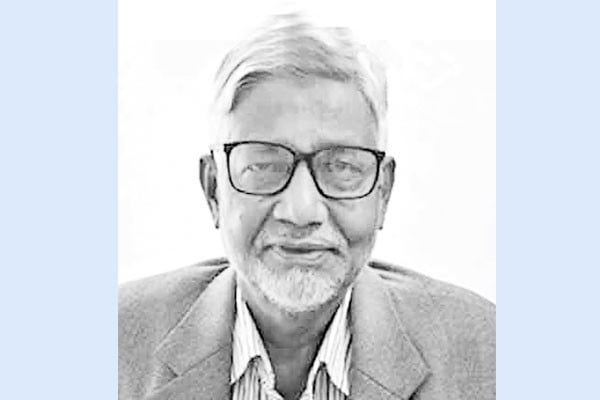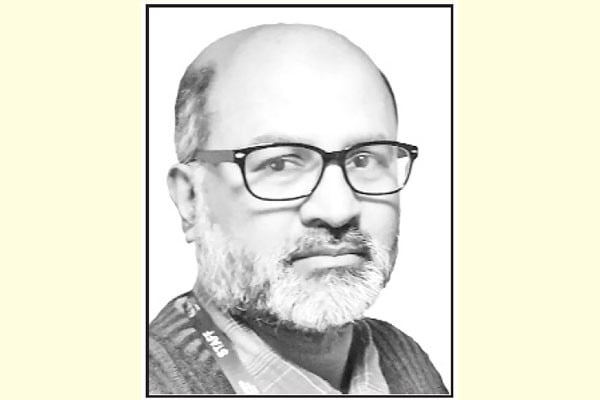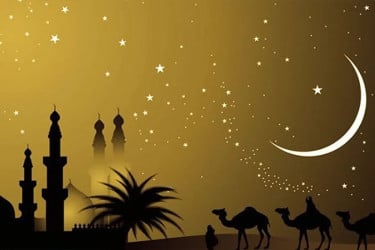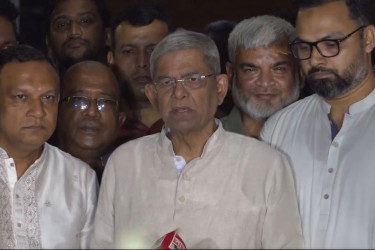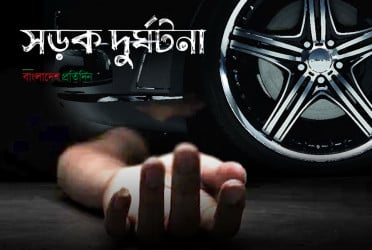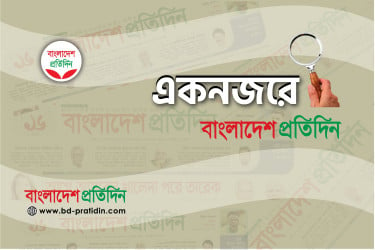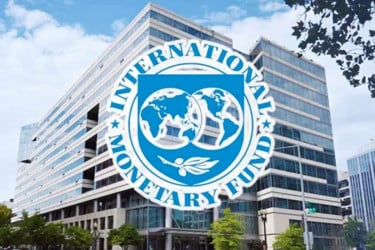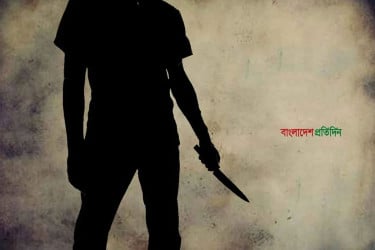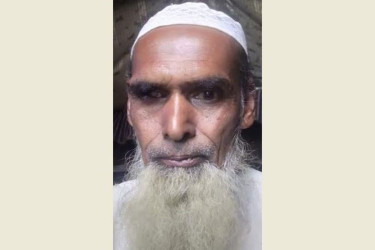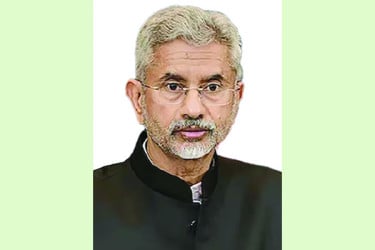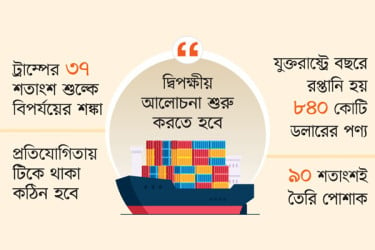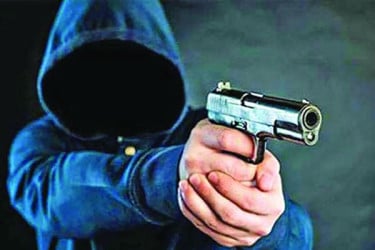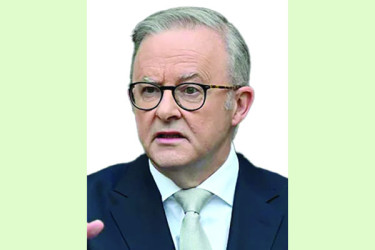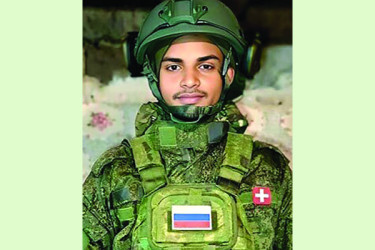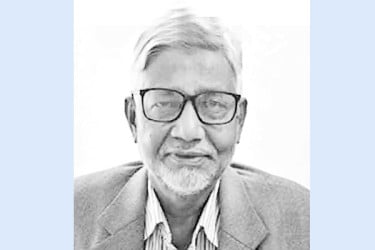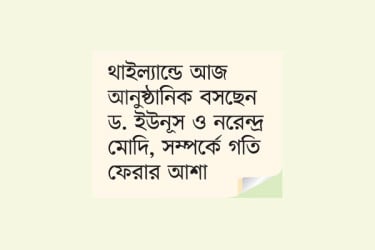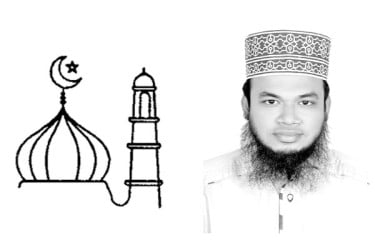গত বছর অক্টোবর মাসে চুনতি অভয়ারণ্যে ট্রেনের ধাক্কায় একটি হাতিশাবক আহত হয়ে মারা যায়। পরে পত্রপত্রিকার প্রকাশিত খবর থেকে জানলাম পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে হাতিসংক্রান্ত একটি সভা হয়েছে এবং উপদেষ্টা হাতি সংরক্ষণে বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা যাঁরা বন্যপ্রাণী নিয়ে গবেষণা ও সংরক্ষণের কাজ করি, তাঁদের জন্য এটি সুখবর, কারণ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে এ ধরনের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এক দশক ধরে সাঙ্গু নদের দক্ষিণাংশে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার বনাঞ্চলে নির্বিচারে হাতি হত্যা নিয়ে অনেক খবর প্রচার হলেও কোনো বিশেষ কারণে এ বিষয়টি নিয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কখনো যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি অথবা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ২০১৫ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত কক্সবাজার বনাঞ্চলে ২০টি হাতি বৈদ্যুতিক তারে পেঁচিয়ে এবং গুলিতে মারা পড়ে। উখিয়ায় শেষ হাতিটি মারা পড়ে গত বছরের ১৫ আগস্ট। দেশে হাতি-মানুষের দ্বন্দ্ব নিরসনে এবং সার্বিকভাবে হাতি সংরক্ষণে অগ্রাধিকার পাওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে কি না, বিশেষভাবে ভেবে দেখা দরকার। কারণ দেশে হাতি নিয়ে সমস্যা এলাকাভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন। দেশের উত্তরাঞ্চলের জামালপুর-শেরপুর-ময়মনসিংহ-নেত্রকোনার হাতিগুলোর সমস্যা এক ধরনের। কর্ণফুলী নদীর উত্তর পাড়ের চট্টগ্রাম আর পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলের হাতির সমস্যা আরেক ধরনের। অন্যদিকে সাঙ্গু নদের দক্ষিণাংশে চট্টগ্রামের বনাঞ্চল ও কক্সবাজার অঞ্চলের হাতির সমস্যা অন্য ধরনের। আর শেরপুর-জামালপুরের হাতিগুলোর সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ লেখায় সাঙ্গু নদীর দক্ষিণাংশে চট্টগ্রামের বনাঞ্চল এবং কক্সবাজার বনাঞ্চলে হাতির সার্বিক অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করব। বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা যায়, একটি পূর্ণ বয়স্ক হাতি দিনে প্রায় ১৫০ কেজি ঘাসজাতীয় ও গাছগাছালি খেয়ে থাকে। আর ১০০ থেকে ২০০ লিটার পর্যন্ত পানি পান করে। এই বিপুল পরিমাণ খাবারের জন্য হাতিকে পানির জলাশয়সহ বন পরিবেষ্টিত বিশাল এলাকাজুড়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। হাতিরা বংশপরম্পরায় বছরের পর বছর একই পথ দিয়ে চলাচল করে। বছরব্যাপী এরা বিশাল এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় চড়ে বেড়ানোর সময় যেমন এরা ওই নির্দিষ্ট পথে চলাচল করে ঠিক তেমনি দুটি এলাকার মধ্যে একটি থেকে অন্যটিতে যাওয়ার সময় এরা খুবই নির্দিষ্ট পথে গিয়ে থাকে। হাতির করিডরগুলো হাতির চলাচলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চলাচলের পথ বা করিডরের ওপরে যদি কখনো কোনো স্থাপনা তৈরি করা হয়, তাহলে হাতিরা তা ভেঙে ফেলবেই। আমাদের হাতির চলাচলের পথ ও করিডরের অবস্থান নিয়ে প্রায় এক দশকের গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে ২০১৬ সালে প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা IUCN-বাংলাদেশ অত্যন্ত বিশদ আকারে একটি এটলাস প্রকাশ করেছে। হাতির আবাসস্থল পরিবর্তন করে মানুষের জনবসতি তৈরিসহ জমির বহুমুখী ব্যবহারই এ এলাকায় হাতি-মানুষের দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ। লক্ষ করলেই দেখা যাবে, হাতি এ এলাকার যত জায়গায় মানুষের ঘরবাড়ি ভেঙেছে, সেসব স্থায়ী বা অস্থায়ী স্থাপনাগুলো হাতির দৈনন্দিন চলাচলের পথ বা করিডরের ওপরেই করা হয়েছিল। এই এলাকার কক্সবাজার অঞ্চলের রামু-উখিয়াকেন্দ্রিক হাতির সমস্যা এক ধরনের আর চুনতি-মেধাকচ্ছপিয়াকেন্দ্রিক হাতির সমস্যা অন্য ধরনের।
২০০৭ সালে IUCN-এর হাতি গবেষণার অংশ হিসেবে উখিয়া-টেকনাফ এলাকায় দেখা যায়, মিয়ানমার থেকে হাতির দল ঘুমধুম হয়ে উখিয়ায় প্রবেশ করে। হাতির এ চলাচলের পথে বালুখালী টিলায় একটি টিভি উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয় সম্ভবত ২০০৫ সালে। টাওয়ারসহ বিশাল এ স্থাপনাটি দেয়াল দিয়ে ঘেরা। তাই হাতিরা ঘুমধুমের পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে টেকনাফ-উখিয়ার রাস্তার যে জায়গায় টিভি উপকেন্দ্র টাওয়ারটি করা হয়েছে, সেখানে এসে দক্ষিণ বা উত্তর পাশ দিয়ে বালুখালী টিলা থেকে নেমে আবার আগের পথে চলাচল করে। ২০০৪-২০০৬ সালে এই টিভি উপকেন্দ্রের পাশের পাহাড়ে কিছু রোহিঙ্গা শরণার্থীকে পুনর্বাসিত করা হয়। সেই থেকেই এ এলাকায় হাতি-মানুষের দ্বন্দ্ব আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ২০১০-১১ সালে আরণ্যক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আমরা টেকনাফ অভয়ারণ্যের জীববৈচিত্র্যের ওপর গবেষণা করি। এ কাজের অংশ হিসেবে টেকনাফ অভয়ারণ্যসহ এ অঞ্চলে হাতির চলাচলের ওপর GPS নির্ভর একটি বিশদ জরিপ করা হয়। এতে দেখা যায়, হাতির ছোট একটি দল সারা বছর টেকনাফ অভয়ারণ্যে থাকে। হাতির অন্য একটি দল ইনানি অভয়ারণ্য থেকে মনখালী, শাপলাপুর হয়ে শিলখালী দিয়ে টেকনাফ অভয়ারণ্যে আসে, কিছুদিন থেকে আবার চলে যায়। অন্য একটি দল মিয়ানমার সীমান্ত অতিক্রম করে ঘুমধুম দিয়ে উখিয়ার টিভি উপকেন্দ্রের পাশ দিয়ে হোয়াইক্যং হয়ে টেকনাফ অভয়ারণ্যে প্রবেশ করে। এটি বেশ বড় দল এবং বছরে দুইবার ধান পাকার সময় অভয়ারণ্যসহ সম্পূর্ণ দক্ষিণ কক্সবাজার বনাঞ্চলে ঘুরে যায়। অন্যদিকে হিমছড়িতে যে হাতির দল দেখা যায় সেগুলো রাজারকুল, রামু, নাইক্ষ্যংছড়ি, বাইশারি, ভোমারিঘোনা হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বা মিয়ানমারের দিকে আসা-যাওয়া করে।
২০১৭ সালে মিয়ানমার থেকে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা টেকনাফে প্রবেশ করে। এদের সবাইকে উখিয়া টিভি উপকেন্দ্রের আশপাশের আগের রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের সঙ্গে রাখা হয়। এতে উখিয়া থেকে মধ্যহ্নীলা পর্যন্ত পুরো হাতির চলাচলের জায়গাটি পরিণত হয় রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে। ২০১৮ সালে মিয়ানমার ঘুমধুম এলাকায় তারকাঁটার বেড়া দিয়ে সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে হাতির দীর্ঘদিনের চলাচলের পথ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। মিয়ানমার থেকে আসা হাতি শরণার্থী শিবিরের দক্ষিণাংশে হোয়াইক্যং, হ্নীলা, মধ্যহ্নীলা আর টেকনাফ অভয়ারণ্যের বনাঞ্চলে আটকে যায়। অন্যদিকে ২০১০ সাল থেকে রাজাপালং এবং জালিয়াপালংয়ে জনবসতি বাড়তে থাকে, যা ২০১৭ সালের রোহিঙ্গা পুনর্বাসনের পর ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করে। এতে ইনানি অভয়ারণ্য থেকে হাতিগুলো যে পথে রেজু খাল পর্যন্ত যাতায়াত করত, তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। তাই ২০১৭-এর পর ইনানি-টেকনাফকেন্দ্রিক বনাঞ্চলে হাতির দল আটকা পড়ে। তখন থেকেই শুরু হয় এ অঞ্চলে হাতি হত্যার মহোৎসব। এ এলাকায় যত হাতি মারা পড়েছে তার বেশির ভাগই বৈদ্যুতিক তারে পেঁচিয়ে। পরিকল্পিতভাবে হাতির চলাচলের পথে আর পাহাড়ের কিনারায় বৈদ্যুতিক তার দিয়ে বেড়া তৈরি করে হাতি হত্যা করা হয়েছে। কয়েকটি হত্যা করা হয়েছে গুলি করে। যদিও IUCN-বাংলাদেশ Elephant Response Team গঠনের মাধ্যমে হাতি-মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসনে কিছুটা সফল হয়েছে কিন্তু তাতেও এ এলাকায় হাতি হত্যা বন্ধ হয়নি।

অন্যদিকে হিমছড়ি, রামু আর নাইক্ষ্যংছড়ি হয়ে আসা-যাওয়া করা হাতির সমস্যা ভিন্ন। এ হাতিগুলোর জন্য রাজারকুল রিজার্ভ ফরেস্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজারকুল হয়েই এরা মিয়ানমার বা পার্বত্য চট্টগ্রামে আসা-যাওয়া করে। ২০২২ সালে IUCN বাংলাদেশ এ এলাকার হাতির চলাচলের বিশদ তথ্য সংগ্রহের জন্য অত্যন্ত অত্যাধুনিক এক গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়। ওই গবেষণার অংশ হিসেবে এ এলাকার একটি হাতিকে রেডিওকলার পরানো হয়। বন্যহাতির গলায় রেডিওকলার পরিয়ে এবং রেডিও ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে হাতির অবস্থান নিরূপণের পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য শ্রীলঙ্কা থেকে Dr Prithiviraj Fernando-এর নেতৃত্বে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি গবেষক দল বাংলাদেশে আসে। তারা শ্রীলঙ্কাসহ এশিয়াব্যাপী বিভিন্ন দেশে ১০০টিরও বেশি হাতিকে রেডিওকলার পরিয়েছেন। এ ব্যাপারে বন বিভাগের কর্মকর্তা এবং সাফারি পার্কের ভেটেরিনারি বিশেষজ্ঞসহ একটি ট্রেনিং কর্মসূচির আয়োজন করা হয় এবং সবার সমন্বয়ে বন্যহাতির গলায় রেডিওকলার পরানোর উদ্যোগটি নেওয়া হয়। ২০২২ সালের ১৬ ডিসেম্বরের কুয়াশা মোড়া ভোরে রাজারকুল বিটের বনে প্রথম হাতিটিতে ডার্ট করার জন্য গিয়ে মারক্সম্যান (যিনি নির্ভুলভাবে বিশেষভাবে তৈরি বন্দুক দিয়ে ডার্ট নিক্ষেপে দক্ষ) Mr. Chinthaka Pathirana ফিরে আসেন হাতিটিকে অজ্ঞান না করেই। কারণ তিনি দেখতে পান ওই হাতিটির সামনের ডান পায়ে গুলির আঘাত থাকায় হাতিটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানান যে এই হাতিটিতে যে ধরনের সংক্রমণ দেখেছেন তাতে তিন মাসের মধ্যে হাতিটি মারা যাওয়ার আশঙ্কাই বেশি। তাই তিনি হাতিটিকে ট্রাঙ্কুলাইজ না করেই ফিরে আসেন। এটি একটি ভালো সিদ্ধান্ত ছিল, কারণ অসুস্থ হাতিকে ডার্ট করা হলে অনেক সময় বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি হয়। প্রথম হাতি পাওয়ার তিন ঘণ্টা পরে আরেকটি হাতি পাওয়া যায়। হাতির আকৃতি, শারীরিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করেই বিশদ আলোচনার পর হাতিটিকে রেডিওকলার পরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাই সবাই উদ্বিগ্ন, অনেক দিনের প্রস্তুতি, হাতির দলকে মাসের পর মাস পর্যবেক্ষণ আর গতিবিধি অনুসরণ করে দেখে রাখা। আর এর সবকিছুই করেছে IUCN-এর একদল তরুণ গবেষক। সুলতান আহমেদ IUCN-এর পক্ষ থেকে গত এক যুগ ধরে এ অঞ্চলের হাতি সংরক্ষণে কাজ করে আসছেন। তার তত্ত্বাবধানেই পুরো দলটি হাতিকে রেডিওকলার পরানোর কাজটি করছে। পুরো প্রক্রিয়াটিতে হাতির সার্বিক নিরাপত্তাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। অনেক আলোচনার পর Mr. Chinthaka Pathirana হাতিটিকে ডার্ট করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ডার্ট করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতিটি অবশ হয়ে পড়লে প্রথমেই তার একটি পা গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হয় নিরাপত্তার খাতিরে। তারপর একটি কালো কাপড় দিয়ে চোখ ঢেকে দিয়ে হাতির শারীরিক অবস্থা নিরূপণ করতে গিয়ে দেখা যায় যে হাতির পায়ের পাতায় আঘাতজনিত ব্যাপক ক্ষত আছে। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতযুক্ত প্রাণীকে রেডিওকলারিং করা যায় না বলে এনটি ডট দিয়ে হাতিটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং পরক্ষণেই হাতিটি সুস্থ অবস্থায় বনে ফিরে যায়। এটির পায়ের পাতার সংক্রমণ ছিল গুলির কারণে। তৃতীয় একটি হাতিতে রেডিওকলারিং পরানো হয় এবং সফলভাবে এ গবেষণা চলছে। রেডিওকলারিংসংক্রান্ত এত দীর্ঘ কাহিনিটি উল্লেখ করলাম এ এলাকায় হাতির অবস্থা বোঝানোর জন্য। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ এলাকায় যত হাতি মারা গেছে তার সবই চোরা শিকারিদের গুলিতে। যে অল্প কয়েকটি হাতি এখনো এ এলাকায় আছে সেগুলোও চোরা শিকারিদের গুলিতে আহত হয়ে আস্তে আস্তে মারা যাচ্ছে। কিন্তু এ প্রশ্নের কোনো উত্তর পাইনি যে এত চোরা শিকারি কোথা থেকে আসছে? ২০১০-এর আগে তো এ এলাকায় গুলি করে হাতি মারার কোনো খবর পাওয়া যেত না। অন্যদিকে চুনতি-মেধাকচ্ছপিয়ার হাতির সমস্যা প্রধানত রেললাইনকেন্দ্রিক। চুনতি অভয়ারণ্যটি এ এলাকার হাতির জন্য একটি সংযোগ স্থান হিসেবে কাজ করে। দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ির কয়েকটি হাতির দল সাঙ্গু নদী অতিক্রম করে বান্দরবানের চিম্বুক পাহাড়ের পশ্চিম দিয়ে টঙ্কাবতী হয়ে সাতগড় পর্যন্ত আসে। অন্যদিকে লামা-আলিকদম থেকে আজিজ নগরের পূর্বের পাহাড়ি পথে কিছু হাতি সাতগড় আসে। সাতগড় থেকে এরা একটি নির্দিষ্ট পথে চুনতি অভয়ারণ্যে প্রবেশ করে। বেশ কিছুদিন চুনতি-হারবাঙ্গ-পুইছড়ি-বাঁশখালী-আনোয়ারার পাহাড়ে থেকে আবার ফিরে যায়। চুনতি অভয়ারণ্যের ভিতরে এবং আশপাশে প্রচুর ধান চাষ হয়। এই ধানই হাতির প্রধান আকর্ষণ। চুনতির আশপাশে যেমন জনবসতি বেড়েছে তেমনি হাতির চলাচলের রাস্তায় সর্বত্রই বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠেছে জনবসতি।
সাঙ্গু নদের দক্ষিণ পাড় থেকে শুরু করে টেকনাফ পর্যন্ত হাতির আবাসস্থল ও দৈনন্দিন চলাচলের পথে যে কয়টি বড় স্থাপনা হয়েছে তার সব কটিতেই হাতিসংক্রান্ত জটিলতা চলছে। এই পুরো এলাকাজুড়ে দোহাজারী থেকে যে রেললাইনটি ঘুমধুম পর্যন্ত গিয়েছে, সেই রেললাইনটি বহু জায়গাতেই হাতির চলাচলের পথ ও করিডরের ওপর দিয়ে গেছে। অথচ এ এলাকার হাতির চলাচলের ওপর প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এসব স্থাপনা তৈরি করার সময় সামান্য এদিক-ওদিক করে করলেই হাতির সঙ্গে সংঘাত অনেকাংশে এড়ানো যেত। যেমন দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইনটি লোহাগড়া উপজেলায় আসার পরে পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে চুনতি অভয়ারণ্যের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এটি যদি চট্টগ্রাম-কক্সবাজার পাকা রাস্তার পুব দিক দিয়ে সাতগড় দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো তাহলে হাতির অন্তত চারটি চলার পথ ও দুইটি করিডরকে পাশ কাটানো যেত। একইভাবে রেললাইনটি মেধাকচ্ছপিয়া অভয়ারণ্যের ঠিক মাঝ বরাবর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অথচ মাত্র ৮০০ গজ পশ্চিমে চেপে গেলেই একটি গাছও কাটা পড়ত না বা হাতির চলাচলের পথ পাশ কাটানো যেত। অথচ IUCNএর Asian Elephant Specialist Group এবং IUCN Connectivity Conservation Specialist Group-এর বেশ কয়েকজন সদস্য এ দেশে থাকার পরও কাউকে এ-সংক্রান্ত বিষয়ে কখনই যুক্ত করা হয়েছে বা তাদের মতামত নেওয়া হয়েছে বলে জানা নেই। এ ছাড়াও ২০১৬ সালে IUCN-বাংলাদেশ ও বন বিভাগ হাতির চলাচলের পথের যে বিশদ এটলাস তৈরি করেছে অথবা ২০১৮ সালে হাতির জন্য যে ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান তৈরি করেছে সেগুলোর কোনো প্রতিফলনই দেখা যায় না এই রেললাইন তৈরিতে। একইভাবে রামুতে যে ক্যান্টনমেন্ট করা হয়েছে সেটি যদি বর্তমান অবস্থান থেকে কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণে করা হতো, তাহলে এখন যে সমস্যাটি হচ্ছে সেটি হয়তো হতো না। রাষ্ট্রীয় নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি বড় স্থাপনা তৈরির সিদ্ধান্তের আগে ওই স্থাপনার কারণে পরিবেশের ওপর প্রভাবের সম্ভাব্যতা (EIA) যাচাই করা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এসব স্থাপনা তৈরির আগে কি এই সম্ভবতা যাচাই করা হয়েছিল? যদি করা হয়ে থাকে তাহলে দায়িত্বে কারা ছিলেন? কী ছিল ওই রিপোর্টগুলোতে? হাতির চলাচলের বিষয় কি সেখানে ছিল? যদি থেকে থাকে সেগুলো মানা হয়েছিল কিনা? এগুলো দেখার দায়িত্ব কি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো এড়াতে পারে? যেসব কোম্পানির মাধ্যমে এসব স্থাপনার ফলে পরিবেশের ওপর প্রভাবের সম্ভবতা (EIA) যাচাই করা হয়েছে, তাদের যদি কোনো গাফিলতি থাকে তবে পুনর্বিবেচনা করে আইনের আওতায় আনা হোক।
আশির দশকে ড. রেজা খান, ড. ফরিদ আহসান, ড. আনিসুজ্জামান খান এবং ড. এএসএম রশীদের হাতিসংক্রান্ত গবেষণাগুলোয় প্রাপ্ত তথ্য থেকে কক্সবাজার বনাঞ্চলের হাতি সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায়। ২০০৪ সাল থেকে পরবর্তী দুই যুগে IUCN-এর হাতি গবেষণা থেকে এ এলাকায় হাতির সার্বিক পরিস্থিতি জানা যায়। আমার বন্যপ্রাণী ল্যাব থেকে বেশ কয়েকজন ছাত্র/শিক্ষার্থী হাতি নিয়ে এমএসসি পর্যায়ে বিশদ গবেষণা করেন। ১৯৯২ সালে আবদুল্লাহ আল যাবেদ, ১৯৯৬ সালে তাপস রঞ্জন চক্রবর্তী, ২০০৩ সালে আবদুল আজিজ এবং তারিকুল ইসলাম, ২০০৯ সালে সৈয়দ মাহমুদুর রাহমান এবং ২০২৩ সালে ড. মতালেবের হাতিসংক্রান্ত গবেষণাগুলোয় বাংলাদেশের হাতি বিশেষ করে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার হাতি সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে সব ধরনের তথ্যই পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ২০০৬ সালে ইতালির সিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাদের দেশের হাতি নিয়ে পিএইচডি করেন ড. মো. মহসিনুজ্জামান চৌধুরী এবং ২০১২ সালে নরওয়ের University of Science and Technology থেকে ড. রায়হান সরকার তাঁর পিএইচডি গবেষণায় এ অঞ্চলের হাতি-মানুষের দ্বন্দ্ব নিয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন। বন বিভাগের SRCWP প্রকল্পে হাতি নিয়ে গবেষণায় অনেক তথ্য উঠে আসে। ২০১৮ সালে বন অধিদপ্তর এবং IUCN-বাংলাদেশ যৌথভাবে বাংলাদেশের হাতির ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান তৈরি করে। এ ছাড়াও দেশের বেশ কিছু পরিবেশবাদী সংগঠনে হাতিসংক্রান্ত অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের হাতিসংক্রান্ত গবেষণালব্ধ বিশদ তথ্য থাকার পরও রাষ্ট্রীয়ভাবে কখনোই এ তথ্য ব্যবহার করে এ এলাকার হাতি-মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসনে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না, আমার জানা নেই।
প্রকৃতপক্ষে বন্যপ্রাণীসংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বা এ-সংক্রান্ত যে কোনো উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পর্যালোচনা ও দিকনির্দেশনা প্রদানের আইনগত কর্তৃপক্ষ হচ্ছে বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ড এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কমিটি। আমাদের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ধারা-৩ এবং ধারা-৪ এ এই বোর্ড ও কমিটি তৈরি এবং এর কার্যপরিধি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, মন্ত্রণালয়ের সুবিধার্থে ২০১৭ সালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় যেভাবে এই দুটি কমিটি তৈরি করে তা আমাদের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ২০১৭ পরবর্তী সময়ে বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা বোর্ডের সভা বছরে একবারের বেশি হয়েছে বলে আমার জানা নেই অথবা বন্যপ্রাণীসংক্রান্ত কোনো উ™ূ¢ত পরিস্থিতিতে এ বোর্ডের কোনো সভা হয়েছে বলেও জানা নেই। অথচ বন্যপ্রাণীসংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তের আগে এ সভায় আলোচনার বিষয়ে আইনে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে।
গত তিন দশকে হাতির এই এলাকার আবাসস্থলগুলো যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটি পুনরুদ্ধার প্রায় অসম্ভব। এই এলাকার বনের বিপুল অংশই অবৈধভাবে দখল হয়ে যাওয়ায় হাতির চলাচলের পথ সংকুচিত হয়েছে। বনের ভিতরে খাবারের স্বল্পতার চেয়েও বন লাগোয়া নিচু জমিতে ধান চাষের ফলে হাতি সহজপ্রাপ্য খাবারের জন্য ধান খেতে নেমে আসছে, যা হাতি-মানুষ দ্বন্দ্বের আরও একটি কারণ। দেশে হাতির সব আবাসস্থলের আশপাশের ধানখেতে হাতিরা ধান খেতে আসবেই এবং এ সময়ে অনেক হাতিই মারা পড়বে স্থানীয়দের হাতে। গত কয়েক বছর থেকে এমনটাই হয়ে আসছে। এটি কীভাবে সমাধান হবে জানি না, তবে বনের দখল করা জায়গা উদ্ধার করা গেলে এবং বনের লাগোয়া নিচু জমিতে চাষাবাদ বন্ধ করা গেলে এ সংঘাত কমবে।
রাজাপালং আর জালিয়াপালংয়ের হাতির চলাচলের রাস্তা এখন আর পুনরুদ্ধারের সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। তবে উখিয়ার ঘুমধুমের হাতির চলাচলের পথটি যদি খুলে দেওয়া যায়, মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে হাতির আন্তদেশীয় চলাচল শুরু করা যায় এবং সে সঙ্গে হাতি হত্যা থামানো যায়, তাহলে হয়তো টেকনাফের বনাঞ্চলে টিকে থাকা হাতি বেঁচে যাবে। একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মনে রাখা উচিত যে আমরা হাতির আবাসস্থলে গিয়ে সব ধরনের স্থাপনা করেছি, হাতিরা আমাদের আবাসস্থলে আসেনি, যার কারণে হাতিরা আজ ভয়ানকভাবে বিপর্যস্ত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বিক বিষয়টি দেখতে হবে। না হলে এ দশকের শেষে টেকনাফ অভয়ারণ্যে আর কোনো হাতি থাকবে বলে মনে হয় না।
লেখক : অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়