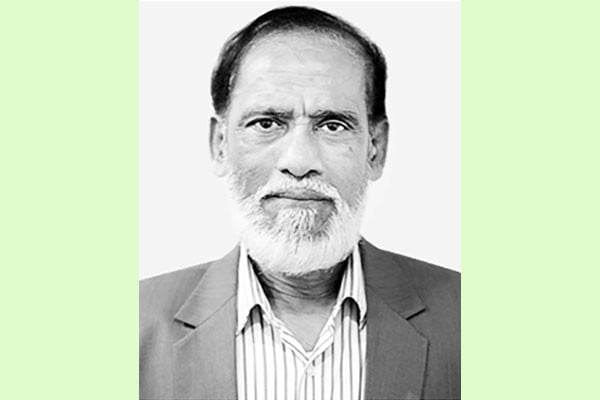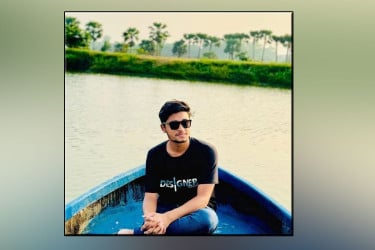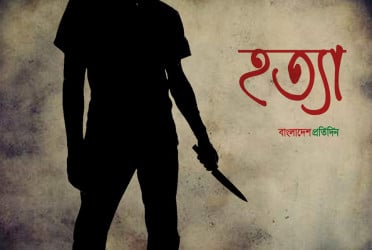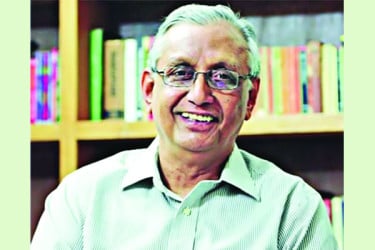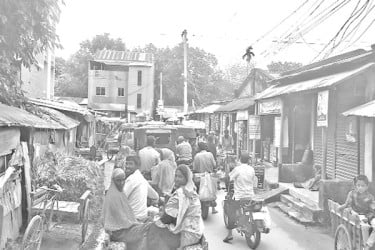জাতীয় ঐক্য একটি দেশের স্থিতিশীলতা, সামাজিক শান্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি। ইতিহাস দেখায়, জাতি যত ঐক্যবদ্ধ হয়, দেশের সম্ভাবনা তত বৃদ্ধি পায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ তার উজ্জ্বল প্রমাণ। তখন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিকভাবে ঐক্যবদ্ধ জাতি স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতার লড়াই, স্বার্থপরতা ও অবিশ্বাস দেশের স্থিতিশীলতা ও সংহতিকে বিপন্ন করে। ১৯৭৫ সালের পর থেকে দলগুলো সংবিধান ও প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। ১৯৯০ সালের গণ আন্দোলনের পরও তারা জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি, যা দীর্ঘমেয়াদি বিপদের সূচনা করে।
গত ১৫ বছরে ফ্যাসিবাদী শাসন সংবিধান, আইন ও প্রশাসনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনেছে। বিচারব্যবস্থা, সংবাদমাধ্যম ও নির্বাচন কমিশনে পক্ষপাত বেড়েছে; র্যাব, ডিজিএফআই ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বিরোধী মত দমনে ব্যবহার করা হয়েছে- গুম, খুন ও নির্যাতন সাধারণ ঘটনা হয়েছে। এতে প্রাতিষ্ঠানিক স্বতন্ত্রতা, সামাজিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক চাপের মুখে দায়িত্ব ও স্বচ্ছতা হারিয়েছে।
দীর্ঘ ফ্যাসিবাদী শাসন দেশের শিক্ষা, অর্থনীতি ও সমাজকে বিপর্যস্ত করেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে পাঠ্যক্রম ও নিয়োগে স্বচ্ছতা নষ্ট হয়েছে। অর্থনীতি অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বেড়েছে, সামাজিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব প্রভাব দেশের নিরাপত্তা, সামাজিক শান্তি ও সার্বভৌমত্বকে গভীর ঝুঁকিতে ফেলেছে। এ দুরবস্থা মোকাবিলায় সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন সংস্কার কমিটি ও ঐকমত্য কমিশন গঠন করেছে। কমিটিগুলো সংবিধান, আইন এবং প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠনের জন্য কাজ করেছে। তারা স্বেচ্ছাচারী আইন ও সংবিধান পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ করেছে, বিভিন্ন সুপারিশ করেছে এবং রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তি স্থাপন করার চেষ্টা করেছে। এ প্রচেষ্টার অন্যতম শীর্ষ দিক হলো জুলাই সনদ, যা রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। জুলাই সনদে সংবিধান, আইন এবং প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠনের জন্য সুস্পষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে বিএনপি কিছু ধারায় নোট অব ডিসেন্ট প্রকাশ করেছে, যা প্রমাণ করে রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্য অর্জন এখনো চ্যালেঞ্জিং। জুলাই সনদের বাস্তবায়ন ও দেশের পুনর্গঠনের জন্য গণভোট প্রস্তাবিত হয়েছে। গণভোট কার্যকর না হলে দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে যাবে। রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ না হলে সনদের ধারাগুলো কার্যকর হবে না, সংবিধান ও আইন সংস্কারের প্রক্রিয়া ব্যর্থ হবে এবং দেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দুর্বল থাকবে।
জুলাই বিপ্লব প্রমাণ করেছে যে, রাজনৈতিক দল ও জনগণ যখন ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন দেশের জন্য বড় ধরনের পরিবর্তন সম্ভব। দেশের ভবিষ্যৎ শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য, সংবিধান ও আইনকে কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর নির্ভর করছে। ঐক্যহীনতা দেশের জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। জাতিকে সতর্ক হতে হবে, নিজেদের পার্থক্য ভুলে দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু এভাবে বাংলাদেশ একটি স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে এগোতে পারবে, যা আগামী প্রজন্মের জন্য সমৃদ্ধি, শান্তি এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে।
জাতীয় ঐক্যহীনতার প্রভাব দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গভীর। রাজনৈতিক দলগুলো যখন নিজেদের স্বার্থের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয় না, প্রশাসন কার্যকরভাবে পরিচালিত হয় না, বিচারব্যবস্থা নিরপেক্ষ থাকে না এবং আইন প্রয়োগে স্বচ্ছতা হারায়-এর ফলশ্রুতিতে দেশের প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়, রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ও পক্ষপাতমূলক হয়ে যায়। এই পরিস্থিতি জনগণের আস্থা হ্রাস করে, সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি করে এবং দেশে বিভাজন সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক অস্থিরতা বিদেশি ও দেশীয় বিনিয়োগকারীদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প স্থগিত বা বাতিল হয়। বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও সামাজিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়।
জাতীয় ঐক্য ও রাজনৈতিক সমঝোতা না থাকলে দেশ সম্ভাব্য বিপর্যয়ের দিকে এগোচ্ছে। দেশের স্থিতিশীলতা, সংবিধানিক কাঠামো ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার একমাত্র পথ হলো রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়া। দেশের জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের স্বার্থ ভুলে দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে। ঐক্যহীনতার সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো দেশের সার্বভৌমত্বের হুমকি। দেশের স্থিতিশীলতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য আন্তর্জাতিক প্রভাবও উদ্বেগজনক। যখন রাজনৈতিক দলগুলো বিভক্ত এবং প্রশাসন পক্ষপাতমূলক হয়, তখন প্রতিবেশী শক্তিগুলো, বিশেষ করে ভারত, দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগ নিয়ে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে।
জাতীয় ঐক্য ও রাজনৈতিক সমঝোতা না থাকলে দেশ সম্ভাব্য বিপর্যয়ের দিকে এগোবে। রাজনৈতিক দলগুলো যদি নিজেদের স্বার্থকে জাতির স্বার্থের ওপরে প্রাধান্য দেয়, তবে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ধ্বংস হয়ে যাবে। রাজনৈতিক অস্থিরতা সামাজিক বিভাজন, গৃহযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতা সৃষ্টি করতে পারে। দেশের স্থিতিশীলতা, সংবিধানিক কাঠামো ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার একমাত্র পথ হলো রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়া। দেশের জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের পার্থক্য ভুলে দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে। সংবিধান ও আইনকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগণকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। শুধু এভাবে বাংলাদেশ একটি স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে এগোতে পারবে, যা আগামী প্রজন্মের জন্য শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে।
যদি জুলাই বিপ্লব আইনগত স্বীকৃতি না পায়, তাহলে বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সরকার ও তার নেতাদের অবস্থান অত্যন্ত অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। আইনগত ভিত্তি ছাড়া কোনো সরকার দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। কারণ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও অর্থনৈতিক লেনদেনের সব কিছুই আইনি বৈধতার ওপর নির্ভর করে। এ ক্ষেত্রে জুলাই বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডকে ‘অবৈধ দখল’ বা ‘অসাংবিধানিক ক্ষমতা গ্রহণ’ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হতে পারে, যা ভবিষ্যতে তাদের বিরুদ্ধে আইনি বা আন্তর্জাতিক বিচার দাবি তুলতে পারে। রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিতরে আমলাতান্ত্রিক অচলাবস্থা দেখা দিতে পারে, কারণ অনেক সরকারি কর্মকর্তা, সংস্থা বা বিদেশি মিশন এমন সরকারের সঙ্গে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে, যাদের আইনগত অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ।
অন্যদিকে, অন্তর্বর্তী সরকার যদি আইনগত বৈধতা না পায়, তাহলে রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, প্রশাসনিক স্থবিরতা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। বিদেশি বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক সাহায্য, এমনকি বাণিজ্যিক সম্পর্কও ঝুঁকির মুখে পড়বে, কারণ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সাধারণত শুধু বৈধ ও স্বীকৃত সরকারের সঙ্গেই কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখে। এতে দেশের অভ্যন্তরে অস্থিরতা, সামাজিক বিভাজন ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বাড়তে পারে, যা নতুন করে সংঘাতের জন্ম দেবে। তাই জুলাই বিপ্লবকে টেকসই ও ফলপ্রসূ করতে হলে তার একটি দৃঢ় আইনগত ভিত্তি নিশ্চিত করা জরুরি, নইলে বিপ্লবের অর্জনগুলো দীর্ঘমেয়াদে অর্থহীন হয়ে পড়বে।
সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো-বিএনপি ও তাদের সমমনা দল চাচ্ছে বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিতে নির্বাচন এবং জাতীয় নির্বাচনের দিনেই গণভোট আয়োজন। বিএনপি যদি তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে তাহলে রাজনৈতিক অচলাবস্থা আরও গভীর হতে পারে। নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাবে ভোট পরিচালনায় জটিলতা দেখা দিতে পারে, যা নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। এ অবস্থায় নির্বাচন যদি অনুষ্ঠিতও হয়, তাহলে ফলাফল নিয়ে তীব্র বিতর্ক ও সংঘাত দেখা দিতে পারে, যা নতুন করে রাজনৈতিক সহিংসতা ও অস্থিতিশীলতার জন্ম দেবে। এমন একটি পরিস্থিতিতে গণভোটের মূল উদ্দেশ্য-জনমতের প্রতিফলন, বরং হারিয়ে যাবে, কারণ এটি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অংশে পরিণত হবে।
অন্যদিকে, জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামপন্থি দল আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক (পিআর) পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচন এবং জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দেওয়ার জন্য গণভোট জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে করার বিষয়ে তাদের অবস্থানে যদি অটল থাকে এবং জাতীয় দাবি অব্যাহত রাখে, তাহলে সেটিও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করবে। এতে জাতীয় নির্বাচনের সময়সূচি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হবে, প্রশাসনিক প্রস্তুতি ব্যাহত হবে এবং জনগণের আস্থা ক্ষুণ্ন হবে। দুই জোট যদি নিজেদের অবস্থান থেকে কোনো রকম সরে না আসে, তাহলে দেশ কার্যত দ্বিধাবিভক্ত রাজনৈতিক সংকটে পড়বে। এ অবস্থায় রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়তে পারে, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হতে পারে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারে।
জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে, যখন রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের অবস্থানে অটল থেকে জাতীয় স্বার্থের চেয়ে দলীয় অবস্থানকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, তখন দেশের পরিস্থিতি অচলাবস্থায় রূপ নিতে পারে। যেখানে প্রশাসন স্থবির, অর্থনীতি বিপর্যস্ত ও জনগণ হতাশ হয়ে পড়বে। অর্থনৈতিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়ে খাদ্য ও জ্বালানি সরবরাহে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এতে সামাজিক অসন্তোষ সৃষ্টি হতে পারে; হিংসা ও লুটপাট বৃদ্ধি পেতে পারে। একপর্যায়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হতে পারে। ঐক্যহীনতার সুযোগ নিয়ে আবার ফ্যাসিবাদ ফিরে আসতে পারে। সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো দেশের সার্বভৌমত্বের হুমকি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জরুরি হলো একটি জাতীয় সংলাপের উদ্যোগ নেওয়া, যেখানে সব রাজনৈতিক শক্তি, নাগরিক সমাজ, নির্বাচন কমিশন ও প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা অংশ নেবেন। সংলাপের মাধ্যমে গণভোট ও নির্বাচনের সময়সূচি, পদ্ধতি ও তদারকি ব্যবস্থায় একটি সমঝোতা গড়ে তোলা যেতে পারে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত হবে সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও জাতীয় ঐক্যের মানসিকতা গড়ে তোলা, কারণ রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা দলীয় জয়ের চেয়ে অনেক বড় লক্ষ্য। প্রয়োজনে একটি জাতীয় ঐক্য সরকার গঠনের বিষয়ও বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও অর্থনৈতিক আস্থা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়।
লেখক : অর্থনীতিবিদ ও গবেষক