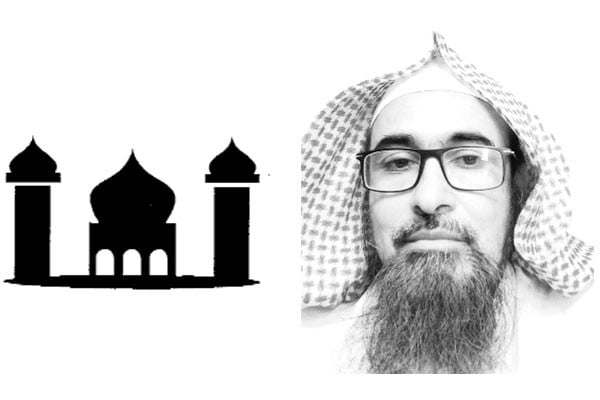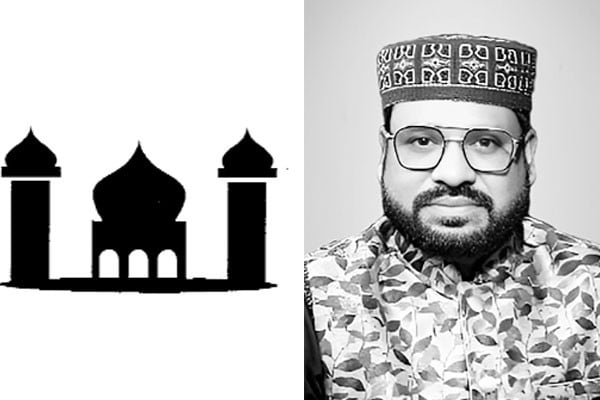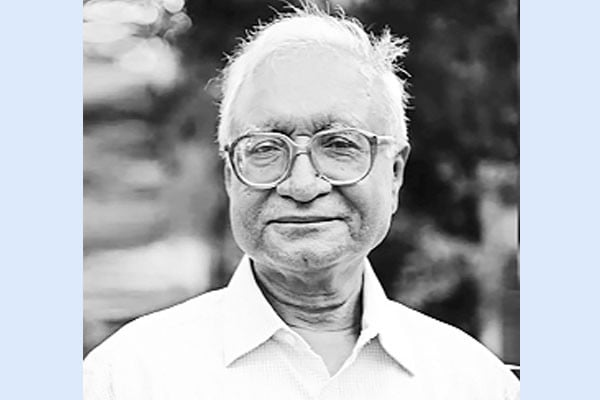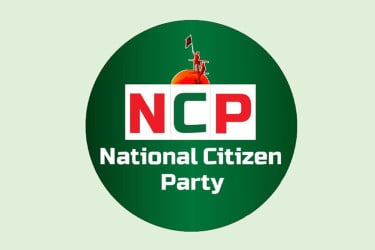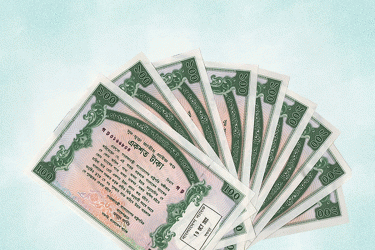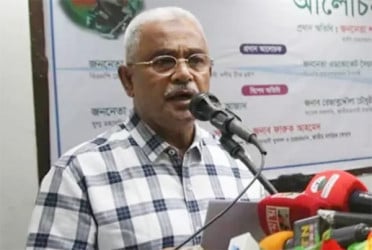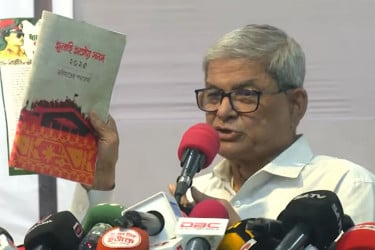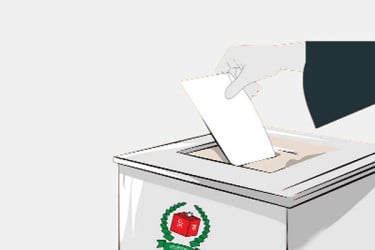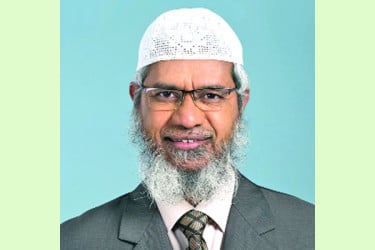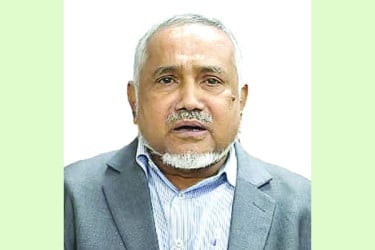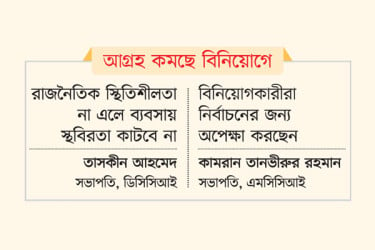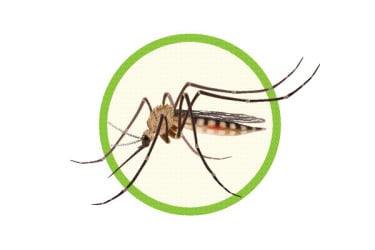আমেরিকার রাজনীতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প এক অদ্ভুত চরিত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক মানুষ তাঁকে দেবতা ভাবেন, বাকিরা মনে করেন তিনি গণতন্ত্রের জন্য এক চলমান ঝড়, আবার কেউ কেউ তাকে বদ্ধপাগলও বলেন। তিনি যতবার নীরব থাকেন, তার চেয়ে বেশি আলোড়ন তোলেন যখন মুখ খোলেন। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। সর্বশেষ ঘটনায় তিনি নিজেই নিজের সরকারের বিরুদ্ধে ২৩ কোটি ডলারের ক্ষতিপূরণ দাবি করে আবারও প্রমাণ করলেন-ডোনাল্ড ট্রাম্প কেবল রাজনীতিক নন, একেবারে জীবন্ত রাজনৈতিক থিয়েটার।
ট্রাম্পের অভিযোগ, ২০১৬ সালের নির্বাচনের সময় রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে যে তদন্ত হয়েছিল এবং ২০২২ সালে ফ্লোরিডার মার-এ-লাগোতে এফবিআই যে অভিযান চালায়, দুটিই ছিল রাজনৈতিক প্রতিশোধের বহিঃপ্রকাশ। এই তদন্তের কারণে তাঁর মানসিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষতি হয়েছে এবং সেই ক্ষতির দায় সরকারকেই নিতে হবে। কিন্তু যে সরকারের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ তুলেছেন, সেই সরকারেরই প্রধান তিনি নিজেই। তাঁর এই বৈপরীত্যই ট্রাম্পীয় রাজনীতির সারকথা।
যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল টর্ট ক্লেইমস অ্যাক্ট অনুযায়ী, সাধারণ নাগরিক সরকারি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ চাইতে পারেন। কিন্তু কোনো প্রেসিডেন্টের নিজের প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি একেবারে অভূতপূর্ব ঘটনা। আইনি বিশেষজ্ঞরা এটিকে বলেছেন-‘অধিকারের বিকৃত প্রয়োগ’ এবং ‘নৈতিক কল্পবিজ্ঞান’। কারণ, একদিকে ট্রাম্প সরকারই তাঁর দাবির বিচার করবে, অন্যদিকে ট্রাম্পই সেই সরকারের নির্বাহী প্রধান। এ ঘটনাকে অনেকেই তুলনা করছেন মধ্যযুগীয় রাজাদের সঙ্গে, যারা নিজেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে নিজেরাই রায় দিতেন। ইংল্যান্ডের রাজা হেনরি অষ্টম যেমন নিজের আদালতে নিজের বিয়ের বৈধতা বিচার করতেন, তেমনই ট্রাম্প আজ হোয়াইট হাউসের ছায়ায় বসে নিজের প্রতি রাষ্ট্রের আচরণের বৈধতা নির্ধারণ করছেন। রোমান সম্রাট নিরোর মতোই তিনি যেন নিজেই আইনের আগুন জ্বালিয়ে তার তাপে নিজের প্রতিচ্ছবি গড়ছেন।
তবে এই দাবি কেবল আইনি কৌতুক নয়; এটি এক গভীর রাজনৈতিক কৌশলও বটে। তাঁর বিরুদ্ধে নিউইয়র্কের বেসামরিক প্রতারণা মামলায় যখন ৪৫৪ মিলিয়ন ডলারের জরিমানা বহাল থাকে, ঠিক তখনই ট্রাম্প ক্ষতিপূরণের এই দাবির মাধ্যমে যেন বলেন, ‘তোমরা আমার থেকে অর্থ আদায় করেছ, এখন আমিও রাষ্ট্রের কাছ থেকে আদায় করব আমার প্রাপ্য।’
ট্রাম্পের ক্ষতিপূরণ দাবি আসলে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ধারাবাহিকতা। ২০২০ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর ‘ক্যাপিটল হিল দাঙ্গা’- ঘটনায় তিনি বারবার বলেছেন, ‘রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।’ একসময়ে যেসব সংস্থা তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করত, আজ তাদের বিরুদ্ধেই তিনি দাঁড়িয়েছেন। তিনি যেন শেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ, যিনি ক্ষমতার মায়ায় নিজের চারপাশে এমন এক অদৃশ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছেন, যার বাইরে সত্যের আলো না পৌঁছায়। আইনবিদরা সতর্ক করছেন, এ ধরনের ক্ষতিপূরণ দাবি যদি আদালতে যায় এবং কোনোভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়, তাহলে তা হবে এক ভয়ংকর দৃষ্টান্ত। যেখানে ভবিষ্যতের নেতারাও নিজেদের সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে রাষ্ট্রীয় অর্থ থেকে ‘নৈতিক প্রতিশোধ’ নিতে পারবেন। মার্কিন গণতন্ত্র, যা একসময় নেলসন ম্যান্ডেলার মতো নেতাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল, আজ সেই গণতন্ত্রই আত্মসমালোচনার মুখে। এ ঘটনার নৈতিক দিকটিও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। যে প্রেসিডেন্টের হাতে রয়েছে বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ, সেই প্রেসিডেন্টই যখন বলেন-‘আমি ক্ষতিপূরণ চাই,’ তখন তা কেবল আইনি ভাষায় নয়, নৈতিকতার দৃষ্টিতেও এক তীব্র প্রশ্ন তোলে। রাষ্ট্র যদি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগের আসামি হয়, তাহলে ন্যায়বিচারের সীমানা কোথায়? এই প্রশ্ন এখন কেবল যুক্তরাষ্ট্রের নয়, সমগ্র গণতান্ত্রিক বিশ্বেরও। অনেকে বলছেন, ট্রাম্পের ক্ষতিপূরণ দাবি মূলত রাজনৈতিক রণকৌশল। ২০২৮ সালের নির্বাচনের মঞ্চে নিজেকে ‘নিপীড়িত নায়ক’ হিসেবে পুনর্¯’াপন করার প্রয়াস। ইতিহাস সাক্ষী, পপুলিস্ট নেতারা সব যুগেই নিজেদের রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের শিকার হিসেবে উপস্থাপন করে জনগণের সহানুভূতি আদায় করেছেন।
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট থেকে শুরু করে তুরস্কের এরদোগান পর্যন্ত, সবাই কোনো না কোনোভাবে ‘আমার বিরুদ্ধে বিশ্ব’ এই ভাষাটি ব্যবহার করেছেন। ট্রাম্প সেই ঐতিহ্যেরই এক মার্কিন সংস্করণ। তবে ইতিহাস আমাদের এটাও শিখিয়েছে, যে নেতা নিজের ক্ষমতার শীর্ষে দাঁড়িয়ে আইনের প্রহসন শুরু করেন, তাঁর পতনও সাধারণত নাটকীয়ভাবে অতি দ্রুতই হয়ে যায়। রাজা নিরো যেমন নিজের প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে সংগীত বাজিয়েছিলেন, ট্রাম্পও আজ রাজনৈতিক অগ্নিনির্বাপক হাতে নিয়ে নিজেই রাজনীতির অগ্নিস্রোত প্রজ্বলিত করছেন। হয়তো তিনি মনে করেন, এই আগুনই তাঁকে অমর করবে।
লেখক : ওয়ার্ল্ড পিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস সোসাইটির চেয়ারম্যান